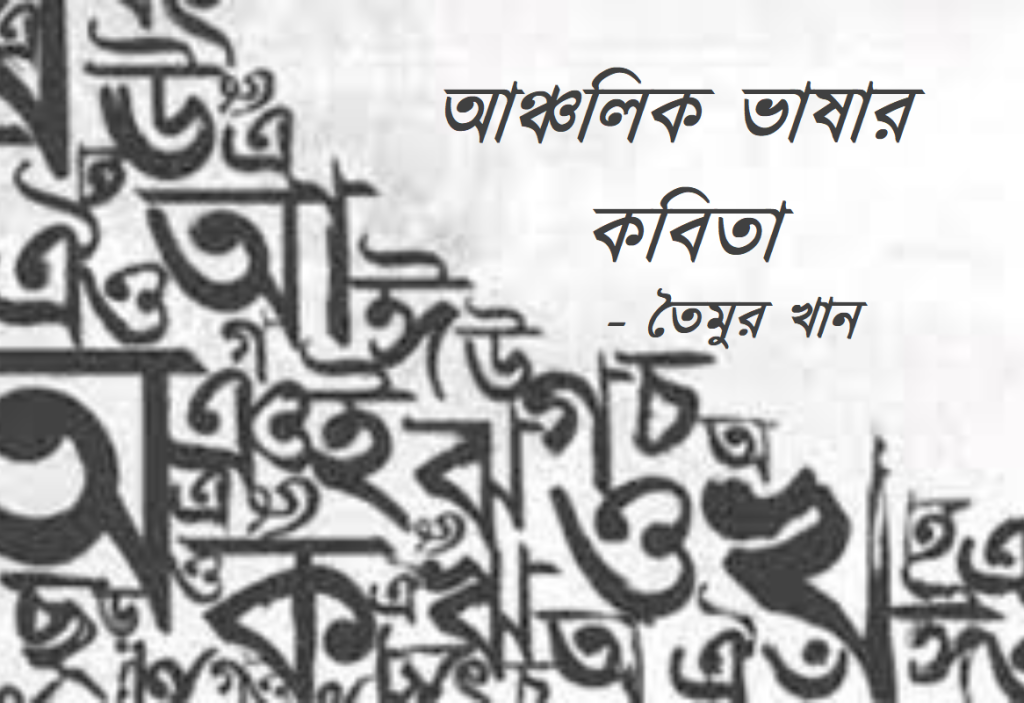একবার এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে মেট্রো সিটিতে বাস করা এক কবিকে আঞ্চলিক ভাষার কবিতা পাঠ করতে শুনেছিলাম। বাংলা ভাষার বহু উপভাষা আছে, তেমনি বহু আঞ্চলিক ভাষাও। বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষা, বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ভাষা, পুরুলিয়ার আঞ্চলিক ভাষা, উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা এবং মালদহ-মুর্শিদাবাদেরও আঞ্চলিক ভাষা।
যে কবি কবিতা পড়ছিলেন তিনি কোনো আঞ্চলিক ভাষাতেই কখনো কথা বলেননি। এমনকী তাঁর পরিবারের সঙ্গেও বলেন না। তিনি যে আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা পাঠ করেছিলেন সেই ভাষা ছিল আমাদের সমাজে আদিবাসীদের অর্থাৎ বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ব্যবহার করা বাংলা ভাষা। তাদের মুখে কেমন বাংলা ভাষা উচ্চারিত হয় আশা করি তা সকলেরই জানা। সেই ভাষাতেই তিনি কবিতা লিখে পাঠ করছিলেন। সেই কবিতা শুনে মোটেও আমার ভালো লাগেনি। কেন ভাল লাগেনি সেই কথাটি বলতে চাইছি।
কবিতা একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিষয় বলেই আমি মনে করি। নিজস্ব উপলব্ধি নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলে আমার মনে হয় সত্যিকারের কবিতা লেখা সম্ভব নয়। এ কথা বিশ্বাস করি, কবিতায় বাঁক কাছে, রহস্য আছে, না বলা আছে, শূন্যতা আছে, উল্লম্ফন আছে, বিষয়হীনতা আছে, আবার পরম সত্য এবং চরম প্রজ্ঞাও আছে। আবেগ এবং মেধার সংমিশ্রণ না ঘটালে শৈল্পিক সিদ্ধি আনা সম্ভব নয়। কল্পনা তো বাস্তবকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়। আর বাস্তবের কেন্দ্রে থাকে জীবনধর্ম। এই জীবনধর্মের মধ্যেই আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের জাগরণ, আমাদের মানবিক চৈতন্য যা প্রেম-প্রণয়, লিপ্সা, যৌনতা, বিরহতাড়িতা, ভাবসম্মিলন ইত্যাদিতে অবস্থান করে। এমনকী আমাদের আত্মহত্যার প্রবণতাও এই জীবনধর্মেরই অংশ।
সুতরাং প্রকাশ অপ্রকাশ, দৃশ্য অদৃশ্য, বাস্তব অবাস্তব, স্বপ্ন কল্পনা, ধরা অধরা, বলা না-বলা সবই কবিতার বিষয়। তাহলে অন্যের মুখের ভাষা নকল করে শুধু বিবৃতির পর বিবৃতি লিখে আমাদের কৃত্রিম উপলব্ধিকে সঠিকভাবে কি কবিতায় লিখতে পারা সম্ভব? আমি যখন কোনো আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি হতে চাইছি এবং তাদের কথা বলতে চাইছি, তখন তাদের সমবর্তী হওয়া একান্তই দরকার আমার।
তাদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা, মৃত্তিকালগ্ন হাহাকার, ক্ষুন্নিবৃত্তির উপর্যুপরি সংগ্রাম আমার দ্বারা কি সম্ভব? ধুলোমাখা গা এবং ছিন্ন পোশাক পরা দেহাতি মানুষ যখন অর্ধাহারে-অনাহারে পশুপক্ষী শিকারকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করে, তখন তাদের কী অন্তর্বেদনার স্ফুটন হয় সেটা কি বাবু কালচারে বড় হওয়া মেট্রো কবির পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয়?
সম্ভব নয় বলেই আমি উক্ত কবির আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা লেখার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। তাঁর কবিতা লেখাকে সৌখিন মজদুরি হিসেবেই উল্লেখ করি। আগাগোড়া তাঁর প্রতিটি উচ্চারণকে কৃত্রিম এবং ভণ্ডামির প্রকাশ বলেই দাবি করি। তিনি হয়তো মানবদরদি সংবেদনশীল একজন মানুষ একথা মেনে নিলেও কবিতার মতো এক সত্য শিল্পকে বেনো জলে ভেসে যেতে দিতে পারি না। কবি সর্বদা নিজের অবস্থান, নিজের জীবনচর্যা, নিজের বোধ ও উপলব্ধিকেই কবিতা করে তুলবেন। অবশ্য তিনি অন্যের হয়েও কথা বলতে পারেন। কিন্তু সেই কথা তাঁর নিজের ভাষাতে বলাই কাম্য বলে মনে করি।
আঞ্চলিক ভাষায় তখনই সার্থক কবিতা লেখা সম্ভব, যে অঞ্চলের কবি যে সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছেন, তাঁর জীবন, তাঁর সমাজ, তাঁর সংগ্রাম, তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। যে ভাষায় তিনি কথা বলেন, যে ভাষায় তিনি বিদ্রোহ করেন এবং অবশ্যই যে ভাষায় তিনি প্রার্থনা করেন সেই ভাষাতেই যখন কবিতা লেখা হয় তখনই প্রকৃত কবিতা সৃষ্টি হয়। এরকম কবি ক’জন আছেন? এখনো আমার চোখে পড়েনি। সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলোতে যেসব কবিদের দেখা পাই এবং যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার কবিতা চর্চা করেন, তাঁরা অধিকাংশই সমাজের উচ্চ শ্রেণির মানুষ। মজদুর খাটা, অশিক্ষিত পরিশ্রমী তাঁরা কেউ নন। স্বাভাবিকভাবেই সেইসব কবিতায় প্রাণ থাকে না। শুধু কথোপকথনের একটা ভঙ্গি থাকে, কৃত্রিম একটা কৌশল থাকে, গরিব-দরদি সাজা কবির নাকি-কান্না থাকে। কবিতার সেইসব কচকচানির বাড়বাড়ন্ত আবৃত্তিকারদের দ্বারা আরও বিস্তৃত হয়। তাঁরা বলেন, এসব কবিতা নাকি খুবই স্পর্শাতুর, মানবহৃদয়কে উথালপাথাল করে দেয়।
আঞ্চলিক ভাষার কবিতার আবৃত্তিধর্মিতা এই কারণেই বেড়ে যায় যে, এই কবিতা সরাসরি বক্তব্য প্রধান বলে নাটকীয় ভাবে আমজনতা তাদের মনের মধ্যে একটা দৃশ্য তৈরি করে নিতে পারে। বিশেষ করে মেয়ে পাচার, মেয়ে বিক্রি, বাল্যবিবাহ, স্বামীর অত্যাচার, মাতালের সঙ্গে ঘরকন্না, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার হাহাকার, মাতৃ বিয়োগ, শিকার কাহিনি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মহাজনের শোষণ-অত্যাচার ইত্যাদি প্রচলিত নানা ঘটনা নিয়ে তার বিবরণ উল্লেখ করে এই কবিতাগুলি লেখা হয়। ‘বাবু’ কবিরা তাঁদের কবিতায় ওইসব গ্রাম্য আনপড় দীনদুঃখি মানুষদের সংলাপ কবিতায় বসিয়ে দেয়। নাটকীয় মোড় সৃষ্টি করে। মানবিক দয়া-মায়ার উদ্রেক করে। স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষকে তা আকৃষ্ট করে। কিন্তু শিল্পের বিচারে এই কবিতা চিরন্তনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে পারে না। মেধাবী আলোকে কবিতার রহস্যময়তা এবং গভীরতা এই সব কবিতায় থাকে না। সাময়িকভাবে তা ভালো লাগলেও সর্বকালীন বিচারে তার আবেদন মানুষের কাছে গৃহীত হয় না। এক সময় ‘নীলদর্পণ’ নাটক মানুষকে আন্দোলিত করেছিল। মনে হয়েছিল এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কিন্তু আজকের সময়ে সেই নাটক আর আগ্রহ নিয়ে কেউ পড়েও দেখে না। আঞ্চলিক ভাষার কবিতাও সময়ের নিরিখে ধুলোমলিন হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার, কবিতা শুধু অন্যকে বিনোদন দেওয়ার বা আনন্দ দেওয়ার জন্য নয়। কবিতা আত্মগত একটি বিস্ময়ও। এই বিস্ময়কে ভেদ করা যায় না, অথচ ভালোবাসা যায়। আঞ্চলিক ভাষার কবিতাতে শুধু বিবরণ ছাড়া আর কিছুই থাকে না। বৈচিত্রহীন, ভাবনাহীন, রহস্যহীন, মেধাহীন বক্তব্যের পর বক্তব্য। আঞ্চলিকতা কখনোই সিরিয়াস কবিতা নয়। আঞ্চলিকতা একটা সময়ের, কিছু মানুষের বিবরণ মাত্র। উত্তরণের কোনো মন্ত্র এই কবিতায় নেই। তাই শিল্প সিদ্ধিরও কোনো প্রশ্ন আসে না।
কিন্তু সেই কবির কবিতার প্রতিবাদ করা তিনি কিছুতেই মানতে পারেননি। যুক্তিতে না পেরে তিনি পাশবিক বল প্রয়োগ করেও আমাকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় উল্লেখ করে আমাকে গালিগালাজ করেছিলেন। কিছু স্বপক্ষীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন আঞ্চলিক ভাষার কবিতার গরিমা প্রচার করতে। হয়তো সফলও হয়েছিলেন। কেননা একদল মানুষ আজও মাছির মতন থেকে গেছেন। তারা বিষ্ঠার গন্ধ পেলেও যেমন ভন্ ভন্ শব্দ করে ঝাঁক বেঁধে উড়ে এসে জিহ্বা বের করে চাটতে শুরু করেন, তেমনি গুড়ের গন্ধ পেলেও ভন্ ভন্ শব্দে ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসেন। এদের জিহ্বায় কোনটার কেমন স্বাদ তার পার্থক্য বোধহয় তারা করতে পারেন না। ফলে তাদের কাছে গুড় এবং বিষ্ঠা সমান দামেই বিক্রি হয়।#