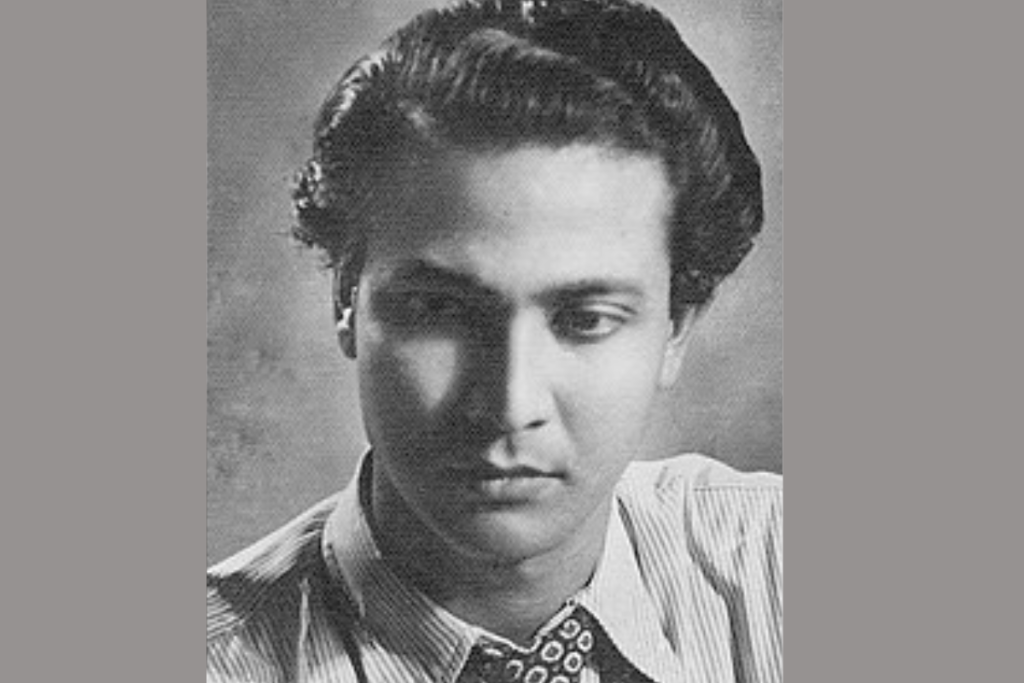।।তৃতীয় পর্ব।।
১৯৪৮-এর দ্বিবিধ সম্প্রসারণ ঘটে- বাস্তবে এবং ওয়ালীউল্লাহ্’র উপন্যাসে। ১৯৪৯-এ গঠিত হয় সরকারি ভাষা-সংস্কার কমিটি। এটির কাজ হয় বাংলা ভাষাকে যথাসম্ভব ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট করে তোলা। পাকিস্তান সরকারের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল, বাংলা ভাষা ‘হিন্দুয়ানি’ প্রভাবযুক্ত। কাজেই সেটি পাকিস্তানি তমদ্দুন-সংস্কৃতির পরিপন্থী। ফলে, নিত্যদিনের এবং নানা উদ্দেশ্যে বই-পুস্তক-পত্রপত্রিকায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষাকে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামানুসারী করে তোলা। সংস্কার কমিটি এমনকি পাঠ্যপুস্তকে সূচিবদ্ধ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাকেও পরিমার্জন করবার প্রস্তাব করে। সে-প্রস্তাবের আলোকে সংশোধন করা হয় নজরুলের কবিতাকেও। যেমন, তাঁর একটি কবিতায় ‘মহাশ্মশান’ শব্দকে বদলে সেটির পরিবর্তে বসিয়ে দেওয়া হয় সরকারি শব্দ ‘গোরস্তান’। রেডিওতে ‘সংবাদ’ শব্দের পরিবর্তে ‘খবর’, সমাপ্ত শব্দের পরিবর্তে ‘খতম’, ‘স্বাগতম’ শব্দের পরিবর্তে ‘খোশ আমদেদ’ বা বিদায় শব্দের পরিবর্তে ‘খুদা হাফেজ’ প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৫০ সালে ভূমি আইনের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেওয়া হয় জোতদার-জমিদার-মহাজন গোষ্ঠিকে। সমান্তরালে পশ্চিম পাকিস্তানে নিশ্চিত হয় জমিদার-আমলা শ্রেণির (পরবর্তীকালে সামরিক আমলা-শ্রেণির) শাসন। ১৯৫২ সালে বাঙালি’র ইতিহাসে প্রথমবারের মত একটি স্বাধিকার আন্দোলন আত্মদান সত্ত্বেও লাভ করে গৌরবময় সাফল্য। বাঙালির ইতিহাসে অর্জিত হয় ‘শহীদ মিনার’-এর চিরন্তন প্রতীক। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনৈতিক দলের নিকটে পরাজিত হয় মুসলিম লীগ যে-মুসলিম লীগ ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের অন্যতম শরিক। কিন্তু এসবের ধারবাহিকতায় ১৯৫৮ সালে সমগ্র পাকিস্তানে জারি হয় সামরিক শাসন এবং দেশ পুনরায় প্রবেশ করে আরও এক অন্ধকার যুগে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রচণ্ডতায় সেই অনড়-অটল দেয়ালে জাগে খানিকটা ফাটল। মাঝখানে ১৯৬৬ সালে ঘোষিত হয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছয়-দফা আন্দোলন। বস্তুত ১৯৫৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ এক যুগ পূর্ববঙ্গের ওপর চলে নিপীড়ন-নির্যাতনের ভয়ংকর শাসন-শোষণ। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত লালসালু উপন্যাসের উপসংহারে যে-মজিদের দেখা মেলে সে আরও শক্তিশালী ও প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত চাঁদের অমাবস্যা’র সম্প্রসারিত বাস্তবের মধ্যে।
এর অর্থ দাঁড়ায় ১৯০০ সালে মজিদ উপস্থিত এবং সে উপস্থিত ১৯৬২ সালেও। হ্যাঁ, ১৯০০ সালের মজিদের ১৯৬২ সালে শারীরিকভাবে বর্তমান থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যে-মজিদ ১৯০০ সালে সন্ত্রাস চালিয়েছিল তার অবলম্বন ছিল ধর্ম এবং সমাজশক্তি। আমরা দেখেছি দু’টোই ছিল তার সপক্ষে। ১৯৬২-তে এসে মজিদের (বা মজিদের উত্তরসুরীদের) শক্তিকে আরও মজবুত ভিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রীয় সহযোগ। ১৯০০ সালে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল আক্কাস। সে-প্রচেষ্টাকে নির্মূল করে দেয় মজিদ। সে-কাজে ধর্ম (মজিদ) এবং পুঁজি (এক্ষেত্রে জমিদার খালেক ব্যাপারি) জোটবদ্ধ। খালেক ব্যাপারির স্ত্রী নিঃসন্তান আমেনা’র প্রতিবেশি গ্রাম আওয়ালপুরের পিরের কাছ থেকে ‘পানিপড়া’ আনবার উদ্যোগটিকে মজিদ ব্যর্থ করেই ক্ষান্ত হয় না। সদলবলে আওয়ালপুরের পিরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাতে। মিথ্যে যুক্তিতে সে খালেক ব্যাপারিকে বাধ্য করে স্ত্রী আমেনাকে তালাক দেওয়ার জন্যে। আপাতদৃষ্টে জমিদার খালেক ব্যাপারি ছিল গ্রামের সবচাইতে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কিন্তু ধর্মের ক্ষমতা দিয়ে মজিদ জমির মালিকের ওপরও প্রতিষ্ঠা করে নিয়ন্ত্রণ। মজিদের নিশ্ছিন্দ্র ক্ষমতার সাম্রাজ্যে একটুখানিও টোল খাওয়ার জো ছিল না। যখনই তার পথে প্রতিপক্ষতার সম্ভাবনা জেগেছে তখনই সেটিকে উপড়ে ফেলেছে মজিদ। নিষ্ঠুর-নির্মম তার সেই নিধনপ্রক্রিয়া। উপন্যাসটি শেষ হয় মজিদের শক্তিমত্তার বিজয়-ঘোষণা দিয়ে। অবশ্য তার দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা-পর্ব ক্ষীণ আলোকরেখার মত উপপ্লব জাগায় মজিদের শক্তিসাম্রাজ্যে। কোনো-কোনো সমালোচক জমিলাসৃষ্ট মাজারকেন্দ্রিক প্রতীকটিকে আশাবাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন যে-আশাবাদ মজিদের ত্রাসের রাজত্বের মধ্যে সঞ্চার ঘটায় ইতিবাচক সম্ভাবনার। মজিদ এবং তার দ্বিতীয় স্ত্রী অসম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তরুণি জমিলা সম্পর্কিত অধ্যায়টি নিঃসন্দেহে উপন্যাসে গতি-বৈচিত্র্য এবং বিশেষ ধরনের দার্শনিকতার ইঙ্গিতবাহী। তবে মজিদ-জমিলা সংক্রান্ত পর্বটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র ঔপন্যাসিক মন ও মননকে উপলব্ধি করবার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক-সূত্রও বটে।
আরও পড়ুন: প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ভদ্র নারী এবং রবীন্দ্রনাথের ছায়াছবি পরিচালনা
ক্ষমতা যতই উত্তুঙ্গ হোক তার মধ্যেও থাকতে পারে ভঙ্গুরতা- উপন্যাসে জমিলা সেই সত্যের স্মারক। ক্ষমতার উৎসের মধ্যেই নিহিত থাকে সংকটের উপাদান। মজিদের দুর্বলতা হলো, মাটির ঢিবি তার প্রতিষ্ঠার অবলম্বন, অদৃশ্য বিধাতা তার শক্তির হাতিয়ার, ধর্ম তার শোষণের যন্ত্র কিন্তু এসবের তুলনায় অত্যন্ত দুর্বল বলে প্রতীয়মান মানুষের ওপরই তার নির্ভরতা- তাও আবার সে-মানুষ পুরুষ নয়, নারী। একনায়ক হিটলারের উপজিব্যতায় লেখা বার্টোল্ট ব্রেখটের কবিতাটি স্মরণ করা যায় যেখানে কবি বলছেন- জেনারেল তোমার বোমারু বিমানটা জব্বর, কিন্তু সেটার একটাই দুর্বলতা, চালাতে মানুষ লাগে। শূন্য মজিদ পূর্ণ হয়। ধর্মের ক্ষমতার আশ্রয়ে ছাড়িয়ে যায় ভূম্যধিকারীকেও। একটা গোটা গ্রামকে করে রাখে করতলগত। কিন্তু প্রথম স্ত্রী রহিমার সন্তানহীনতার কারণ থেকে উদ্গত হতে থাকে তার আপাত সংকটের আভাস। ক্ষমতার জোরেই সে প্রথম স্ত্রীকে সংসারে রেখে ঘরে তোলে কন্যাসম জমিলাকে। মজিদ চেয়েছিল তার সাম্রাজ্যের একজন উত্তরাধিকারী (যে আবশ্যিকভাবে পুরুষ) যে তারই মতন শক্তি দিয়ে টিকিয়ে রাখবে তার প্রভাববলয়টিকে। ক্ষমতাশূন্য জমিলা বৈষম্যকে মেনে নিলেও নিজের ভেতরের প্রাণশক্তিকে কোনোভাবেই বিসর্জন দিতে রাজি নয়। অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র জগতের মধ্যেই নিজের এষণাকে ছড়িয়ে দেয় জমিলা। জমিলার সূত্রেই প্রথম বারের মত মজিদের বিপরীত ধরনের জীবনচেতনার অভিজ্ঞতা হয় পাঠকের। জমিলা ক্ষুদ্র বৃত্তের বাসিন্দা হলেও মজিদের রুদ্ধতা ও ধর্মপুষ্ট-জীবনবিরোধী কর্মকাণ্ডকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না তার পক্ষে। পরিণামে আসন্ন হয়ে ওঠে সংঘট্ট, যদিও সেই দ্বান্দ্বিকতা ‘শঠে শাঠ্যং’ ধরনের নয়, একপক্ষীয়ই। কিন্তু জমিলার সূত্রে জীবনচেতনার একটা স্বস্তিকর পরিস্থিতিতে উপনীত হওয়া যায়। সে-পরিস্থিতি পাঠকের জন্যে ইতিবাচক কিন্তু স্বেচ্ছাচারী মজিদের জন্যে শতভাগ নেতিবাচক। জমিলার দৃপ্ত পদক্ষেপে যৌবনখচিত বিচরণ, তার স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যোচ্ছ্বাস অন্তঃপুরের সীমানা ডিঙ্গিয়ে মজিদের সাম্রাজ্যেও আছড়ে পড়ে। শুধু তা-ই নয়, মজিদের নিয়মকানুনের প্রতিও তার মধ্যে লক্ষিত হয় বীতস্পৃহা। কখনও কখনও তা পরিণত হয় অবজ্ঞা-অবহেলায়। স্বামী মজিদের বয়স নিয়ে সে ঠাট্টা করে সতীন মাতৃসম রহিমার সঙ্গে। নামাজ পড়বার সময় সে ঘটা করে সাজসজ্জা-কেশবিন্যাসে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইবাদতের লক্ষ্যে বিছানো জায়নাামাজে নামাজ পড়বার পরিবর্তে সে ঘুমিয়ে পড়ে। মজিদের বারংবারের নিষেধাজ্ঞা ও রহিমার সতর্কতা সত্ত্বেও জমিলার আত্মবিকাশকে ঠেকানো যায় না। এমনকি অন্তঃপুর-নির্ধারিত সীমানারেখা পেরিয়ে সে উঁকি দেয় বাইরের পৃথিবীতে যেখানে ‘মোদাচ্ছের পিরের মাজারে’ জিকিরে (এক ধরনের ধর্মীয় কোরাস) সমবেত মজিদের নেতৃত্বাধীন গ্রামবাসী। এভাবেই মজিদের প্রভাববৃত্তে একটি ফাটল হয়ে জমিলার আবির্ভাব।
উপন্যাসে সর্বপ্রাথমিক প্রত্যাখ্যান-চেতনা শক্তিহীন অবলা জমিলা’র সত্তা-স্ফূরিত। প্রবল ক্ষমতাদর্পী মজিদের প্রতাপের দেয়ালে সেটাই উল্লেখযোগ্য ও অকল্পনীয় ধাক্কা। উপন্যাসে এবং মজিদের পর্যবেক্ষণের মুকুরে জমিলার অস্তিত্ব এতই তুচ্ছ যে মজিদের সঙ্গে জমিলার কোনো সংলাপই নেই। মজিদের প্রাবল্যের সমান্তরালে দাঁড়ানো সম্ভবও নয় তার পক্ষে। বস্তুত তার কথা বলবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে আর সেটা কেড়ে নেয় একা মজিদ নয়, এক চিরপুরুষ শ্রেণি। এরকম একটি চির অবহেলিত অবস্থান থেকে উত্থানের শক্তির দেখা মিলবে- সেটা কল্পনাতীতই। কিন্তু সেই কল্পনাতীত ব্যাপারটাই ঘটে উপন্যাসে। মজিদের নিয়ন্ত্রণটা যে অসৎ ও অশুভ সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে জমিলা। পারে বলেই তার সত্তার গহিনে জেগে ওঠে প্রতিবাদ। সমাজবিজ্ঞানী এরিখ ফ্রম এমন প্রতিবাদকেই বলেছেন বিদ্রোহের প্রাথমিক শর্ত। জমিলার বিদ্রোহের পরিমণ্ডলটা খুব বড় নয় কিন্তু এর আবেদন অনেকখানি। মহব্বতনগর গ্রামের যে-মজিদ প্রতিবেশি আওয়ালপুর গ্রামে গিয়ে অন্য এক পিরের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় তার বিরুদ্ধে এক দুর্বল নারীর বিদ্রোহকে স্মরণযোগ্য মনে করা কঠিন। অথচ, ঔপন্যাসিক জমিলাকে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকতার সঙ্গে তৈরি করেছেন মজিদের সঙ্গে সামনাসামনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্যে। মজিদের সর্বগ্রাসী সন্ত্রাসের বিপরীতে ঔপন্যাসিকসৃষ্ট জমিলার বিক্ষুব্ধ প্রত্যাখ্যান চেতনাটি লক্ষ করা যাক-
“মাঝ-উঠানে হঠাৎ বেঁকে বসলো জমিলা। মজিদের টানে স্রোতে-ভাসা তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিলো, এখন সে সমস্ত শক্তি সংযোগ করে মজিদের বজ্রমুষ্টি হতে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলো। অনেক চেষ্টা করেও হাত যখন ছাড়াতে পারলো না তখন সে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসলো। হঠাৎ সিধা হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করলো।”
আরও পড়ুন: বাউলের পথেই রবীন্দ্রনাথ
এটা যে ভয়ংকর এক অকল্পনীয় কাণ্ড সেটা পাঠক এবং মজিদ উভয়েরই জানা হয়। যে-লোকের কথায় গ্রামের লোকে ওঠে-বসে, যার নির্দেশে গ্রামের প্রবল ক্ষমতাশালী জমিদারও ‘বউ তালাক’ দেয়, যার পা ‘খোদাভাবমত্ত’ গ্রামবাসীরা ‘চুম্বনে-চুম্বনে সিক্ত করে দেয়’ তার প্রতি ‘এমন চরম অশ্রদ্ধা’ সত্যি এক নবাধ্যায়। তবে, ঘটনাটি ঘটে অন্তঃপুরে। তবু সেটি মজিদের অন্তর্ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ব্যাপারটা পাঠকের চোখের সামনে ঘটলেও বৃহত্তর জনমানসের অগোচরেই থেকে যায়। তা থাকলেও আমাদের সমস্ত আশা শেষ পর্যন্ত জমিলাকেই ভর করে। কেননা, শত-শত মানুষের লোকালয়ে একটা মানুষ নেই যে মজিদের ভণ্ডামি আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। জমিলা প্রতিবাদী হয় পরিণতি না জেনেই। প্রতিবাদটা তার সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত। সেজন্যে তাকে চরম মূল্যও দিতে হয়। মজিদের উচ্চ- গার্হস্থ্য সন্ত্রাসের শিকার হয় জমিলা। প্রহারের শাস্তিবিধান করেই ক্ষান্ত নয় মজিদ। মুমূর্ষু জমিলাকে সে আটকে রাখে মাজারের অভ্যন্তরে। এবং তারপরেই ঘটে বাংলাদেশের উপন্যাসের সেই বেনজীর ঘটনা: “মেহেদি দেয়া তার একটা পা কবরের গায়ের সঙ্গে লেগে আছে।” কবর মানে ‘মোদাচ্ছের পীরের মাজার’- মাজারের গায়ে জমিলা’র পদস্পর্শের দৃশ্যটি লালসালু উপন্যাসে বিধৃত প্রত্যাখ্যানচেতনার উত্তুঙ্গ প্রকাশ। কোনো কোনো সমালোচক এটিকে বৈপ্লবিক বলে আখ্যা দেন। দৃশ্যটির বিশেষ ব্যঞ্জনা থাকা সত্ত্বেও এটিকে কোনোভাবেই বৈপ্লবিক বলবার উপায় নেই। কেননা, এই দৃশ্য বা চিত্র মজিদের ক্ষমতার সাম্রাজ্য একটুও চিড় ধরাতে পারে না। বরং আমরা দেখবো পরবর্তী চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসে মজিদের ক্ষমতার সাম্রাজ্যের ঘটে প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণ। এখন প্রশ্ন, তাহলে এমন দৃশ্যের কেন প্রয়োজন পড়ে ঔপন্যাসিকের। ঐ যে বোর্হেস বলেছিলেন, ”লেখকের অবলম্বন সীমাহীন, তাঁর অভাব নেই শিল্পের কাদামাটির।”
আমরা বরং বলতে চাই মাজারের গায়ে জমিলা’র পা নয়, লেগে ছিল ঔপন্যাসিকের পা। মাজারকে পায়ে স্পর্শ করবার মত সাহস বা দুঃসাহস কোনোটাই সম্ভব নয় জমিলা’র পক্ষে। মাজারকে তার ভয় এবং মাজার তার নিকটে পবিত্রতারই প্রতীক। কেবল তার নিকটে কেন, মহব্বতনগর গ্রামের সকলের নিকটেই মাজার এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সমার্থক। মাজারটি একই সঙ্গে বাস্তবের মাটিতে এবং তাদের প্রত্যেকের চেতনার মাটিতে লাল সালু-আবৃত। মাজারের গায়ে পা স্পর্শ করবার মুহূর্তটিতে জমিলা তার সজ্ঞানতার মধ্যে বর্তমান ছিল না, গ্রাসিত ছিল এক ধরনের অবশ আচ্ছন্নতায়। হয়তো সেই আচ্ছন্নতার মুহূর্তে তার পা স্পর্শ করেছিল কবর বা মাজারটিকে। সেই স্থির দৃশ্যটিকে ধরেছেন ঔপন্যাসিক এবং সেটিকে পরিণত করেছেন এক মুহূর্তের বিস্ময়ে। মিখাইল বাখতিন তাঁর উপন্যাসতত্ত্বে ভাষার যে-দ্বিবাচনিকতার মাত্রার উল্লেখ করেছেন লালসালু উপন্যাসের শব্দনির্মিত চিত্রটি তার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কেননা, এই দৃশ্যটি প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ রচনা করে পাঠকের সঙ্গে। বোর্হেস বলেন, একটি গল্প যখন শেষ হয় তখন আসলে সেই গ্রন্থের উপসংহারে আরে গ্রন্থের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।” মাজারের গায়ে জমিলা’র পদস্পর্শের বার্তার মধ্য দিয়ে আমরা আরেকটি গ্রন্থের উপক্রমণিকায় প্রবেশ করি যে-গ্রন্থ বাস্তবে তখনও লেখা হয় নি। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্’র প্রত্যাশা সেই গ্রন্থ লেখা হবে একদিন। লিখবে মহব্বতনগরেরই কোনো বাসিন্দা। হতাশায় ডুবে যেতে যেতে, অদৃষ্টবাদে নিমজ্জিত হতে হতে যখন লোকেদের নিশ্চুপ হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই তখন একটি মৌহর্তিক দৃশ্যের মাধ্যমে শত-সহস্র শব্দের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন লালসালু উপন্যাসের রচয়িতা।
আরও পড়ুন: গারো পাহাড়ের চিঠি: ঘোড়া ও রওশন সার্কাস
মহব্বতনগর নামের যে-জনপদটির দেখা লালসালু উপন্যাসে মেলে সেটিকে যদি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বলে ঘোষণা দেওয়া হয় তাহলে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়। যে-লোক গোটা গ্রামটার নিয়ন্ত্রক, যাকে সমগ্র গ্রামবাসী ভীতির চোখে দেখে সে মূলত জনপদটির বাসিন্দা নয়। সেখানে তার আগমন ঘটেছে জনপদটির লোকগুলির অদৃষ্টবাদী-সমর্পিত অবস্থাকে পুঁজি করে নিজের স্বার্থ হাসিল করা। সেখানে জমিলা নামের এক গৃহবধূর ব্যক্তিগত প্রতিবাদের ফল কী হতে পারে সেটা লক্ষ্য করা যায় উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে পৌঁছে। কিন্তু মহব্বতনগরের উপন্যাসের কী শেষ আছে! নেই বলেই প্রায় নেই হয়ে যাওয়া সত্তার কিনারায় দাঁড়ানো জমিলার পদস্পর্শ-দৃশ্যটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করানো। আসমুদ্রহিমাচর হতাশা’র মধ্যে ক্ষীণ হলেও একটি প্রত্যাশাবিন্দুর সৃষ্টি করেন স্বয়ং ঔপন্যাসিকই। ফরাসি দার্শনিক কথাশিল্পী ভলত্যের (১৬৯৪-১৭৭৮)-এর কাঁদিদ উপন্যাসটিকে স্মরণ করতে পারি। হতাশা’র চরম শিখরে পৌঁছানো মানুষের জন্যে ঈশ্বরের করুণা বা আশীর্বাদ নয়, মানুষেরই সাহসী যুযুধানতাকে একমাত্র বিকল্প হিসেবে দেখেছিলেন ভলত্যের। উপন্যাসটির শেষে কাঁদিদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সেই বিখ্যাত বাক্যটি: ইল্ ফো কুলতিভেগ্ নোত্র্ ঝাগদ্যাঁ (আমাদের অবশ্যই চাষ করতে হবে আমাদের বাগানগুলি)। হতাশাবাদী ভলত্যের ঈশ্বরের ওপর আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, মানুষ অশুভ তৎপরতার শিকার, তাই মানুষের উচিৎ সেসব থেকে যতটা সম্ভব দুর্ভাবনা সরিয়ে নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করা। কাঁদিদ-এর সর্বত্র নেতির বিস্তৃতি তবু গ্রন্থটির উপ-শিরোনাম ‘আশাবাদ’। ভলত্যেরের সমালোচনার শিকার ধর্ম, দর্শন, সরকার, সেনাবাহিনী ইত্যাকার যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ। ১৭৫৯ সালে বেরোবার পর গ্রন্থটি সাধারণ্যে নিষিদ্ধ থাকে অনেক দিন। গ্রন্থটিকে ব্লাসফেমি বলেও গণ্য করা হতো একসময়। যখন মহব্বতনগরের কোথাও কোনো আশার লক্ষণ নেই তখন জমিলার পদস্পর্শের ঔপন্যাসিকসৃষ্ট ঘটনাটি মুহূর্তের জন্যে হলেও পাঠককে এই বোধে উদ্দীপ্ত করতে পারে, মাজারটি আসলেই মাটির ঢিবি ছাড়া আর কিছু নয়। জমিলার পা তখনই প্রতিনিধিত্বশীল হয়ে উঠতে পারে যখন সমস্ত মহব্বতনগরবাসী মাজার তথা মজিদ তথা অদৃষ্টের ওপর নির্ভরতার চিন্তা বাদ দিয়ে একমাত্র নিজেদের মানবসম্মত সক্ষমতায় হয়ে উঠতে পারে আস্থাশীল। কবর বা মাজারের গায়ে পদস্পর্শ ঘটে প্রায় অচেতন জমিলা’র। কিন্তু সেটি যদি হতো সচেতন জমিলা’র তাহলে হয়তো এ-উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও ঘটতো ব্লাসফেমির পরিণতি। ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র এমন দার্শনিকতা পরবর্তীকালে কোন্ পরিণামে পৌঁছায় সেটা দেখা যাবে তাঁর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপন্যাসের মুখোমুখি হয়ে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) উপন্যাসের অন্তর্গত কালপ্রেক্ষাপট ১৯৬১/৬২ সাল। কালের দিক থেকে আমরা প্রথম উপন্যাসের ষাট বছর পরেকার সামাজিক জীবনে, ঔপন্যাসিকের সমকালীন পরিপার্শ্বে এসে পৌঁছাই। উপন্যাসের কালগত প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সরাসরি কোনো মন্তব্য নেই কিন্তু অনেকটা তথ্যজ্ঞান এবং সমকালীন পরিস্থিতির সাংকেতিকতা বিশ্লেষণ করলে উপন্যাসাভ্যন্তরীণ কালের মাত্রাটি স্পষ্ট হয়। এ-তথ্যজ্ঞানটুকু না থাকলে উপন্যাসের অন্তগর্ত সামাজিক কাল হতে পারে ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যে-কোনো সময়ের। কিন্তু একটি তথ্যই প্রথমত কালের মাত্রাকে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং দ্বিতীয়ত উপন্যাসের চরিত্রের ওপর ফেলে বিশেষ আলোক। উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামটির সবচাইতে প্রভাবশালী পরিবার বড়বাড়ি। সেটির কর্ণধার ‘দাদাসাহেব’ মৌলভি আলফাজউদ্দিন চৌধুরী ‘জেলা-শহরের সংবাদপত্রে’ প্রকাশিত একটি সংবাদে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত- “আমেরিকায় একজন বিশেষ গুণী এবং ধর্মাসক্ত ব্যক্তি তাঁর দেশবাসীদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে বিষম তোড়জোড় শুরু করেছেন।” তারপর জানা যায় লোকটা ‘হাবসী’। ধর্মান্তপ্রাণ দাদাসাহেব অজানা “মার্কিন নিগ্রোর বদৌলতে তিন গ্রামের ফকির-মিসকিন” খাইয়ে অন্তরের ধর্মোচ্ছ্বাসের বহিপ্রকাশ ঘটান গ্রামবাসীদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসটি রচিত হয় “ফ্রান্সের আলপ্স্ পর্বত অঞ্চলে ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।” এটি ওয়ালীউল্লাহ্’র স্ত্রী এ্যান মারি তিবো’র পিতা মানে লেখকের শ্বশুরমশায় তিবো সাহেবের পিতৃপুরুষদের গ্রাম। নিশ্চয়ই তখনকার দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদতথ্য ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। ‘হাবসী’ সেই মার্কিন ধর্মপ্রচারক ছিলেন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মার্কিন ম্যালকম এক্স (ম্যালকম লিটল, ১৯২৫-১৯৬৫)। আলহাজ¦ মালিক এল-শাবায নামেও তিনি পরিচিত। নেশন অব ইসলাম, মুসলিম মস্ক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তাঁর নেতৃত্বে। পঞ্চাশের দশকে ‘ব্ল্যাক সুপ্রিমেসি’, কৃষ্ণাঙ্গ অধিকার এবং কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি হজ্বব্রত পালন করেন এবং তাঁর গুরু এলাইজা মুহাম্মদের সঙ্গে ইসলাম প্রচারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হ’ন। অনেকগুলো সংগঠন ছিল তাঁর। তবে ‘প্যান-আফ্রিকান অর্গানাইজেশন অব এ্যাফ্রো-আমেরিকান ইউনিটি’ (ওএএইউ) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সবচাইতে সাড়াজাগানো সংগঠন যেটির মুখ্য লক্ষ্য ও তৎপরতা ছিল কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন ও আফ্রিকানদের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা। ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর সাক্ষাৎ হয় মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের, গিনির প্রেসিডেন্ট আহমেদ সেকুতুরে, জাম্বিয়া’র কেনেথ কাউন্ডা এবং ফিদেল ক্যাস্ত্রো’র সঙ্গে। কৃষ্ণাঙ্গ প্রশ্নে ম্যালকম মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রেরও কড়া সমালোচক ছিলেন। বিশ^খ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ক্যাসিয়াস ক্লে’কে তিনিই ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করেন এবং ক্লে পরে বিশ^খ্যাত হ’ন মোহাম্মদ আলী নামে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সাল এই দুই বছর ছিল ম্যালকম এক্স বা ম্যালকম মোহাম্মদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ দু’টো বছর। সেসময়কার তাঁর কর্মকা–প্রচারণা প্রায়ই পত্র-পত্রিকার শিরোনামে স্থান পেতো। অনেকেই ম্যালকম এক্স-কে ‘হার্ড লাইনার’ বা ‘চরমপন্থানুসারী’ মুসলমান হিসেবেই অভিহিত করে থাকেন যদিও কৃষ্ণাঙ্গ অধিকারের বিষয়টি ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের এক প্রধান দিক। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সালের মধ্যকার কোনো এক সময়ের ম্যালকম এক্স-এর সূত্রকেই তাঁর উপন্যাসে ‘হাবসী’ বা ‘নিগ্রো’ মুসলমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সূত্রটি প্রথমত চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের কালগত পরিধি সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা দেয় এবং দ্বিতীয়ত উপন্যাসটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ‘দাদাসাহেব’ আলফাজ উদ্দিন চৌধুরী ও তাঁর ‘বড়বাড়ি’-র সামাজিক অবস্থানের ওপর আলোকপাত করে। আমরা নিশ্চিত হই, দাদাসাহেব ম্যালকমভক্ত একজন কড়া ধার্মিক। ঔপন্যাসিকও সেরকম ধারণাই যোগান। একসময়ে ‘বিধর্মী’ শাসকদের (মানে ব্রিটিশ শাসক) অধীনে সরকারি চাকুরে চৌধুরী সাহেব শাসকদের বিধর্মিতা নিয়ে যথেষ্ট গ্লানিতে ভুগতেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলে (মানে ১৯৪৭-এর পরে) তাঁর সেই গ্লানি দূরীভূত হয়। তাঁর মনের ধর্মবোধ প্রগাঢ় হয়। ধর্মের রীতিনীতি অনুশাসন নিজের বাড়িতে এবং গ্রামে যাতে দৃঢ়মূল থাকে সে-বিষয়ে দাদাসাহেবের দৃষ্টি সজাগ। যে-হত্যাকাণ্ডটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় উপজীব্য বিষয় সে-ঘটনার নায়ক দাদাসাহেবের অনুজ কাদের বা দরবেশ কাদের। গ্রামে সকলেই তাঁকে একজন পরম ধার্মিক ও অবৈষয়িক লোক হিসেবেই জানে।
আরও পড়ুন: ইতিহাসের বাস্তব এবং লেখকের বাস্তব: সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ৩
একটি হত্যাকাণ্ড দিয়ে উপন্যাসটির শুরু এবং সেটিকে কেন্দ্র করে পর্বপরম্পরায় উপন্যাস এগোয় পরিণতির দিকে। প্রায় মধ্যরাতে গ্রামের বাঁশঝাড়ে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডটির একমাত্র দর্শক বড়বাড়ির গৃহশিক্ষক আরেফ আলী যাকে পাঠক অধিকাংশ সময়ে যুবক শিক্ষক নামেই চেনেন। উপন্যাসের কাহিনীর বুনন সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেটির বিশ্লেষণব্যাপ্তি সুপরিসর। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যাওয়া আরেফ আলীর আকস্মিকভাবেই বাঁশঝাড়টির নিকটে পৌঁছানো। পদশব্দে সন্ত্রস্ত কাদের যৌনসংসর্গের উদ্দেশ্যে ঝোঁপের মধ্যে নিয়ে যাওয়া দরিদ্র দিনমজুর করিম মাঝির স্ত্রীকে হত্যা করে চলে যায় দৃষ্টি এড়িয়ে। কিন্তু আরেফ আলীর দৃষ্টিসীমানা থেকেই অপসৃত হয় কাদের। এখান থেকেই কাহিনির সূত্রপাত। একটি হত্যাকাণ্ড সবকিছু এলোমেলো করে দেয় আরেফ আলীর। প্রথমত তার ‘ট্রমা’ (মানসিক আঘাত) হয় যেটা কাটতে সময় লাগে। তার পক্ষে বিশ্বাস করা অসম্ভব, ধর্মপ্রবল বড়বাড়ির প্রবল ধর্মপুরুষ দাদাসাহেবের অনুজ দরবেশ বলে কথিত লোকটাই এমন ভয়ংকর এক হত্যাকারী। এক নিরীহ নারীর হত্যাদর্শক হয়ে নিরব কালাতিপাত তার নিকটে প্রবল অন্যায় বলে প্রতীয়মান হলে সে ভেতরে ভেতরে প্রস্তুতি নেয় ঘটনাটিকে নিকটস্থ থানায় গিয়ে প্রকাশের। কিন্তু কাজটা ভাবা এবং করার মধ্যে চলে দারুণ টানাহ্যাঁচড়া। দরিদ্র আরেফ আলী বড়বাড়ির গৃহশিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত- সেটাই তার রুটিরুজি। গ্রামে শুধুমাত্র ছেলেদের জন্যে বড়বাড়ি প্রতিষ্ঠিত স্কুলেরও সে শিক্ষক। অর্থাৎ খুনের ঘটনাটি প্রকাশ করলে তাকে হারাতে হবে যুগপৎ দু’টো চাকরি। এমনকি গ্রামটিতেও বসবাসের সুযোগ হারাতে হবে তাকে। এরকম এক অন্তর্দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিতে তাকে মোকাবেলা করতে হয় নিজেরই পারা না-পারার ক্রিয়তার সঙ্গে। সেটা করতে গিয়ে একসময়ে সে অসুস্থতা বোধ করতে থাকে। তার প্রচণ্ড বিবমিষা হয়। আবার, দ্বান্দ্বিকতার মধ্যপর্বে রাতের বেলা স্বয়ং হত্যাকারী তাকে ডেকে নিয়ে যায় বাঁশঝাড়ে পড়ে থাকা মৃতদেহটিকে সরিয়ে নিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করবার কাজে। অবশ আচ্ছন্নতায় বা প্রাণভয়ে কাজটা করে সে কিন্তু কাজের শেষে ভোগে চরম অনুতাপে। এভাবে সমস্ত প্রতিকূলতাকে সরিয়ে দিয়ে শেষে আরেফ আলী সত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। একমাত্র সম্বল টিনের স্যুটকেসটা নিয়ে সে থানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কেননা, তার জানা, সত্য প্রকাশ পেলে তার পক্ষে গ্রামে থাকা হবে না। ঘটনার সেটাই শেষ নয়। বরং তা আরও জটিলতার মুখোমুখি। থানাকর্তৃপক্ষ যুবক শিক্ষকের সত্য প্রকাশের হত্যাকারীর নাম প্রকাশের মামলা গ্রহণে জানায় অপারগতা। শুধু তা-ই নয়, থানার কর্তাব্যক্তিরা তাকে হুমকি দেয়, গ্রামের মান্যগণ্য বড়বাড়ির সম্ভ্রান্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ধোপে টিকবে না। তাছাড়া, বড়বাড়ির কাদের বা অন্য কেউ নয়, আরেফ আলীরই হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত হওয়ার জোর সম্ভাবনা। ভয়ার্ত আরেফ আলী থানা ছেড়ে এবং গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে যায়।#
চলবে…