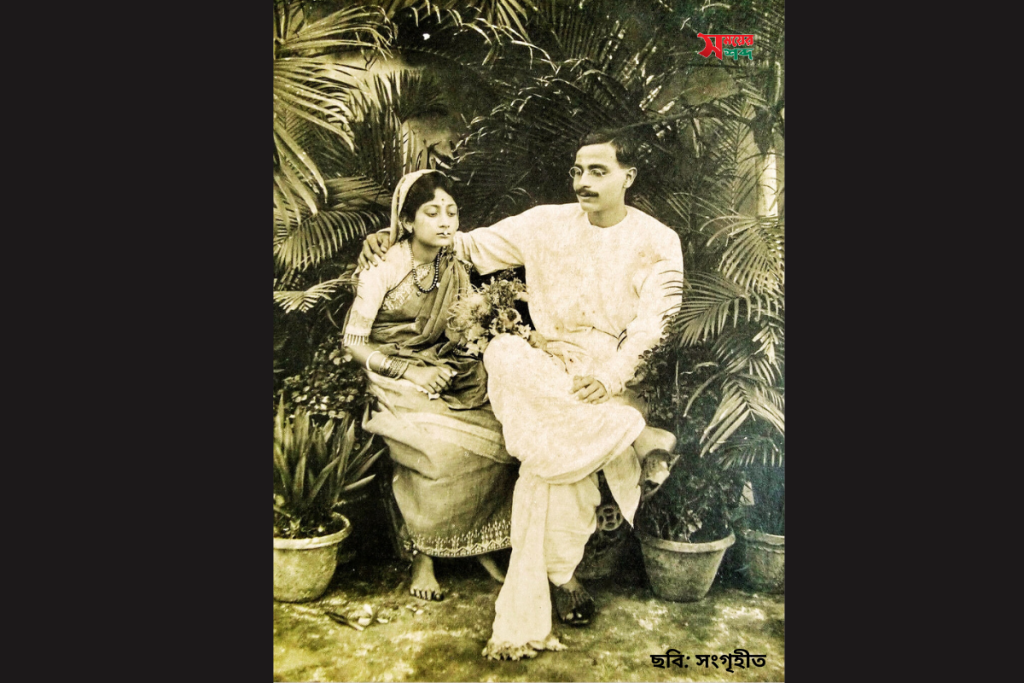ঊনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সেযুগের হিন্দুঘরের নারীরাও তখনকার নব মূল্যবোধ এবং উদার ভাব ভাবনার শরিক হয়েছিলেন। আলোচ্যযুগের প্রথমদিকে মহিলাদের সাহিত্যচর্চায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে দেখা না গেলেও, তখনকার বিভিন্ন সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সুষ্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে কিন্তু অবশ্যই দেখা গিয়েছিল। আর তাঁদের এই ক্ষোভ বিক্ষোভের তরঙ্গগুলিই পরবর্তীকালের বাংলা সাহিত্যে দানা বেঁধেছিল। বস্তুতঃ ঊনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত সেযুগের নানা বাংলা পত্রিকায় হিন্দুঘরের অন্তঃপুরচারিণীদের নানা অভাব অভিযোগ, দাবি ও আবেদন শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।
এবিষয়ে প্রথম যে উদাহরণটি ইতিহাসে পাওয়া যায়, সেটি হল ১৮২৫ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখের সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রকাশিত একজন চরকাকাটুনির একটি আবেদনপত্র। ওই সময়ে বিলাতি সুতো আমদানি শুরু হওয়ার ফলে দেশীয় সুতো প্রস্তুতকারকদের উপরে বিরূপ অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই পেশার উপরে নির্ভর করে থাকা বহু পরিবার সম্বলহীন হয়ে গিয়েছিল। তখনকার এমনি একটি পরিবারের প্রধানা চরকাকাটুনি সমাচার দর্পণ পত্রিকায় প্রেরিত নিজের দরখাস্তের শুরুতে লিখেছিলেন— “আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচগণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিনকন্যা সন্তান হইয়াছিল।” (চরকা কাটনির দরখাস্ত, ১২২৮ বঙ্গাব্দ, ৫ই জানুয়ারি, সমাচার দর্পণ, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ- ১৭৬)
এরপরে তিনি চরকাকেটে নিজের কন্যাদের বিবাহ, শ্বশুর-শাশুড়ির শ্রাদ্ধশান্তির খরচ বহন করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ে এদেশে বিলাতি সুতোর আমদানি শুরু হওয়ার ফলে তিনি তখন অনাথা ও অন্নহীনা হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এই পত্রটিতে সেযুগের নারীদের প্রতিকূল অবস্থায় অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার অভাবের কথা যেমন ব্যক্ত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তাঁদের দুঃসহ বৈধব্য জীবনের বেদনারও প্রকাশ ঘটেছিল।
এরপরে যে পত্রটির কথা উল্লেখ করতে হয়, সেটি হল ১৮৩১ সালের সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকায় ‘শ্রীমতী অমুকী দেবী’ নামের একজন মহিলার পত্র, যাতে তিনি কৌলীন্য প্রথার কুফল সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। আলোচ্য পত্রের লেখিকা প্রথমেই তাঁর নিজের জীবনের করুণকাহিনী বিবৃত করতে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, জন্মের পরে তিনি কোনদিনই নিজের পিতাকে দেখতে পাননি। কিন্তু তিনি বড় হওয়ার পরে তাঁর সেই পিতাই কর্তা সেজে তাঁর মা ও কন্যাদের মতের বিরুদ্ধে গিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে একরাতেই নিজের তিন কন্যার বিবাহ দিয়ে দিয়েছিলেন। আর তারপর থেকে— “সেই অবধি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম হইল পতির সহিত দশন নাই বর্তমানে আছেন কিনা তাহাও জ্ঞাত নহি কেবল মাতুলের ভবনে কখন পাচিকা কখন বা দাসীরূপে কালযাপন করিতেছি।” (সম্বাদ কৌমুদী, ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৩১ সাল, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, শ্রীঅমুকী দেবীর পত্রটি, পৃ- ২৪৬)
এই পত্রলেখিকা পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছিলেন যে, কুলীনদের বহুবিবাহ রোধ হলে কুলীন কন্যারা এধরণের দুঃসহ জীবনের থেকে মুক্তি পাবেন, আর তেমন কিছু ঘটলে— “আমাদের হর্ষের বিষয় এই যে তদ্দ্বারা আমাদের তুল্য দুঃখিনী আর কেহ হইবেক না।”
এর প্রায় চার বছর পরে ১৮৩৫ সালের সমাচার দর্পণ পত্রিকায় ‘প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের’ একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। (সমাচার দর্পণ, ১৪ই মার্চ ১৮৩৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬-২৫৭) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রাজা রামমোহন রায় রচিত প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদ পুস্তিকাটি সেযুগের হিন্দুদের ঘরে ঘরে পঠিত ও আলোচিত হত। এছাড়া তৎকালীন হিন্দু কলেজের তরুণ যুবকেরা নারী-মুক্তির বিষয় নিয়ে সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সভা-সমিতিতে যেসব আলোচনা করেছিলেন, সেসবের উত্তাপও তখন হিন্দুদের ঘরের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছিল। এমনকি এযুগের শিক্ষিত হিন্দুঘরের নারীরা বাংলার বাইরের বিভিন্ন জায়গার সামাজিক রাজনীতি সম্বন্ধেও যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত ছিলেন। আর একারণেই আলোচ্য পত্রটির একজায় বলা হয়েছিল— “শ্রীযুক্ত ইংরেজ বাহদুরের রীতিমধ্যস্থ অনেকানেক জাতীয় স্ত্রীলোকের বৈধব্যবস্থা হইলে তাঁহারদিগের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল আমারদিগের এই বাংলাদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের কন্যা বিধবা হইলে বিবাহ হয় না। যদ্যপি ঐ স্ত্রীলোকেরা উপপতি আশ্রয় করে তবে যে কুলোদ্ভবা সে কুল নষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমনপূর্বক উপস্ত্রী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না।”
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁদের এই পত্রটি ইংরেজ সরকারের কাছে শুধুমাত্র আবেদন নিবেদন ছিল না, বরং সেযুগের যুক্তিপূর্ণ পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও ছিল। তৎকালীন সমাজ-বিবেকের কাছে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন— “কেবল স্ত্রীলোকের সুখ সম্ভোগ নিষেধার্থে কি ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণতন্ত্র সৃজন হইয়াছিল।”
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে—সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ—এই সর্বক্ষেত্রেই নারীকে ভ্রষ্টচারিণী হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই তখন শাস্ত্রের বিধানকে অজুহাত হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল; অর্থাৎ—এগুলির মাধ্যমে তখন নারীর অধিকারকে সীমিত করা হয়েছিল। ‘প্রৌঢ়া পতিহীনা দীনা ক্ষীণা এবং অবিবাহিতা কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের’ পূর্বোক্ত পত্রে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, এরপরে সেটার উত্তর দিতে গিয়ে ‘কচিৎ শান্তিপুর নিবাসিনী’ জানিয়েছিলেন— “স্ত্রীলোক ব্যভিচারী কেবল পুরুষের দ্বারা যদ্যপি পুরুষ সকল উপস্ত্রী বর্জিত হন তবে স্ত্রীলোক কুলটা হইতে পারেন না।” (সমাচার দর্পণ, ১৪ই মার্চ ১৮৩৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭-২৫৮)
তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য ছিল যে, পুরুষেরা দুর্বলচরিত্র ও নীতিজ্ঞানহীন বলেই তাঁরা নিজের অধঃপতনের কারণস্বরূপ নারীকে দোষারোপ করে থাকেন। এই পত্রলেখিকা তাঁর পত্রের শেষে বিধবাবিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধি ও প্রাচীন শাস্ত্রীয় উদাহরণ উদ্ধৃত করে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করবার জন্য সকলের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং মুক্তমনে নারীদের সমস্যাগুলিকে বিচার করবার জন্য উৎসাহীদের তৎপর হতে বলেছিলেন।
সমকালের চন্দ্রিকা পত্রিকার সম্পাদক নারীদের এসব পত্রগুলিকে সাদা চোখে দেখতে পারেননি, এবং সমাচার দর্পণ পত্রিকার সম্পাদককে এজাতীয় পত্র প্রকাশ করবার জন্য তিরস্কার করে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে, জম্বুদ্বীপ ও ইংল্যাণ্ডের নিয়ম সম্পূর্ণ ভিন্ন।
১৮৩৫ সালের সমাচার দর্পণ পত্রিকায় সেযুগের হিন্দুঘরের নারীদের লেখা আরও দুটি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে ‘চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণস্য’ তাঁদের পত্রে পূর্বোক্ত শান্তিপুর নিবাসিনীদের পত্রের সমর্থনে লিখেছিলেন— “তাঁহারা এক্ষণে যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিতে আমাদেরও বহুকাল যত্ন ছিল। কিন্তু সহকারী না থাকাতে ভয়প্রযুক্ত আমরা অগ্রসর হইতে পারি নাই। এক্ষণে সে ভয় দূর হইল। অতএব আপনাদের সঙ্গে দুঃখ সম্বোদক রোদন করিতে আমরা লিখি।” (সমাচার দর্পণ, ১৪ই মার্চ ১৮৩৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮-৬০)
এভাবেই হিন্দুঘরের নারীরা তখন একই ভাবের জোয়ারে পাল তুলেছিলেন এবং বিভিন্ন সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে পুরুষদের প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি তাঁরাও সরব হয়ে উঠেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করবার বহু আগেই ঊনিশ শতকের বাংলার হিন্দুঘরের নারীরা তাঁদের সমস্যাগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরবার প্রচেষ্টায় রত হয়েছিলেন। এসময়ে পত্রলেখিকারা নিজেদের ‘পিত্রাদি ও ভ্রাতৃবর্গের’ কাছে বিচারের আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন যে—পারিবারিক মর্যাদা, ব্যক্তি ও অর্থ লোলুপতার বশে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে পিতা ও ভ্রাতারাই কন্যা ও ভগ্নিদের অত্যাচার করে থাকেন। নিজের ঘর সংস্কার না করে কখনোই সমাজ সংস্কার করা সম্ভব নয়। পূর্বোক্ত চুঁচুড়ার স্ত্রীগণ তাঁদের পত্রে সেযুগের নিরিখে কতগুলি যুগান্তকারী দাবি পেশ করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রথম দাবি ছিল যে, বিশ্বের অন্যান্য সভ্যদেশের নারীদের মত তাঁদেরও বিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ করে দিতে হবে। দ্বিতীয় দাবি ছিল— “অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমারদিগকে তদ্রূপ করিতে কেন না দেন।”
তৃতীয় দাবী ছিল, সেযুগের হিন্দুঘরের নারীরা আর ‘বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায়’ হস্তান্তরিত হতে চাননি। তাঁরা নিজেদের জন্য স্বামী নির্বাচন করবার সুযোগ এবং বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও পণপ্রথা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন যে, কুলধর্ম ও সম্ভ্রমের দোহাই দিয়ে নারীদের পুরুষের কামনার যূপকাষ্ঠে বলি দেওয়া চলবে না। চতুর্থ দাবি অনুসারে তাঁরা ক্রীতদাসীর মত জীবনযাপন করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যে, স্ত্রীধন—যা হিন্দুঘরের নারীদের জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট, সমাজে সেটার স্বীকৃতির দরকার রয়েছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় স্ত্রীরা ক্রীত সম্পত্তির মতোই গণ্যা হতেন। নিজেদের পঞ্চম দাবিতে তাঁরা বলেছিলেন— “যাঁহাদের অনেক ভার্যা আছে তাঁহাদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন। ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে করিতে না পারে। পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে ইচ্ছা তেমন কি স্ত্রীর নাই।”
লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, নারীদের এসব সামাজিক অধিকার নিয়ে জ্ঞানোপার্জিকা সভা এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবন্ধগুলি কিন্তু অনেক পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ‘কাসাৎ শান্তিপুর নিবাস্থ্যনেক বিরহিনীনাং’ একটি পত্রে নারীদের প্রতি সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকার সম্পাদকের বিরূপ মন্তব্যের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন— “কেবল অজ্ঞসমীপে বিজ্ঞতা যেন দ্বিতীয় কুন্তীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠির বজায় ধর্মপুত্র যেমন গঙ্গাপুত্র এইক্ষণে ধর্মসভা সম্পাদক কিবা সদ্বিবেচক উত্তরকারক যেমন যুদ্ধে বিরাটপুত্র উত্তর তেমনি উত্তোরত্তর পত্রের উত্তরে বিদ্যা প্রকাশ হইতেছে। সে যাহা হউক ধর্মশাস্ত্রানুযায়ী দেশাধিপতিকে মর্মবেদন অবগত করিয়া আমাদিগের যাতনা নিবারণার্থ ও লম্পটদিগেব লম্পটতা বারণকরণার্থ উদ্যোগী তাহাতে দুর্যোগি ধর্মপুত্র প্রতিবাদী।” (সমাচার দর্পণ, ১৪ই মার্চ ১৮৩৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৮-৬০)
চন্দ্রিকা পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে শ্লেষের এমন অব্যর্থ তীর সমকালের প্রভাকর পত্রিকার সম্পাদকও ব্যবহার করতে পারেননি বলে দেখতে পাওয়া যায়। বলাই বাহুল্য যে, এই পত্রে পত্রলেখিকা সেযুগের বকধার্মিকদের নিজের ঘৃণা ও শ্লেষ নিক্ষিপ্ত করেছিলেন। আর এজাতীয় শ্লেষের জন্য যে বোধ ও বুদ্ধির তখন প্রয়োজন ছিল, সেটাও এই পত্রলেখিকার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। এথেকে বোঝা যায় যে, হিন্দুঘরের নারীদের প্রচলিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে তখন ফাটল ধরেছিল; আর তাই তখন শাস্ত্রীয় বিধির থেকে বিবেক ও যুক্তির নির্দেশকেই হিন্দুসমাজের শিক্ষিতা মহিলারা অনেক বেশি মূল্য দিয়েছিলেন। শাস্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁদের কাছে তখন অপব্যাখ্যা মাত্র হয়ে উঠেছিল। আর একারণেই তাঁরা দেশাধিপতির কাছে নারীদের জন্য আইনের জন্য প্রার্থনা করতেও পিছপা হননি। একথার উদাহরণস্বরূপ এখানে ১৮৪০ সালে ‘শ্রীতাবিহক গশজ মর্গৌ ইত্যাদি’ পরিচয়ে হিন্দু জমিদার ও কুলবালাদের একটি পত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দুদের দায়ভাগ গ্রন্থ তখন কন্যাদের পিতৃধন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আর অতীতে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হওয়ার ফলে তখন পিতা বা ভ্রাতা কন্যাকে যে স্ত্রীধন দিতেন, সেটা পণরূপে পরিগণিত হত; এবং সেই ধনে কন্যার কোন অধিকার থাকত না ও কুলীন পাত্র কর্তৃক সমস্ত অর্থ আত্মসাৎ হত। এখানে মনে রাখতে হবে যে, বহুবিবাহের ফলে কুলীন স্বামীরা তখন নামেমাত্র স্বামী বলে পরিগণিত হতেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুঘরের কন্যাদের পিতৃগৃহেই দিন কাটাতে হয়। আলোচ্য পত্রটির একজায়গায় বলা হয়েছিল— “পুত্রবধূর তুল্য অলঙ্কারাদি কন্যাকে দেন না তাহার তাৎপর্য পরের ঘরে ধন যাইবে।”
এরপরে এই পত্রলেখিকা মনু, মিতাক্ষরা প্রভৃতি থেকে বিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তখনকার প্রচলিত নিয়ম শাস্ত্রের বিধানকে উপেক্ষা করছিল। এরফলে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাসহ অন্যান্য সব অধিকারই তখন পরিহাসের বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, রাজা রামমোহন রায় এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সতীদাহপ্রথা বন্ধ করবার পরে নারীদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন।
আসলে ঊনিশ শতকের প্রথম থেকেই এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচারবুদ্ধি জগতে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল। তখনকার এই সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেই একদল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীব আবির্ভাব ঘটেছিল। এই স্বাধীন মুক্ত চিন্তার নাগরিকেরা তখন সামাজিক দিক থেকে শাস্ত্রের নামে অহেতুক মিথ্যাচারের বাধা, অর্থনৈতিক দিকে কুলধর্মের বিধিনিষেধ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তার পায়ে পরিয়ে দেওয়া কঠিন নিগড় ভাঙতে চেয়েছিলেন। এখানে যে পত্রগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি আজও বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যদিও সেযুগের অনেকেই অবশ্য এই পত্রগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি অনেকেই আবার এগুলিকে সেকালের মৌলিক রচনা বলেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। একইসাথে একথাও অনস্বীকার্য যে, ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত নারীদের পত্রগুলিতে এযুগের নারীরা নিজেদের যেসব বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন, পরবর্তীকালের বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মকর্তাদের কাছে এগুলো ভবিষ্যতের কর্মসূচী হয়ে উঠেছিল। ঊনিশ শতকের বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রধান ফল ছিল পারিবারিক জীবনের গুরুত্ববৃদ্ধি। এর আগে প্রচলিত থাকা পারিবারিক ঐতিহ্যের থেকে ব্যক্তিজীবন তখন পরিবারমুখী হয়ে উঠেছিল। ক্রমে সতীদাহ বন্ধ হয়েছিল, বহুবিবাহ শিক্ষিত সমাজে প্রায় নিন্দিত হয়ে উঠেছিল, প্রগতিপন্থীরা নারীদের শিক্ষার কথা চিন্তার করতে শুরু করেছিলেন, কৌলীন্য প্রথা হিন্দুসমাজে ঘৃণিত হতে শুরু হয়েছিল, এবং বিধবাবিবাহের সব আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই তখন সমাজমুখীন পরিবার থেকে পরিবারমুখীন সমাজের জন্ম হয়েছিল। আর ঊনিশ শতকের বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের পাতায় পুরুষেরা যেসব সামাজিক কুপ্রথাকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, নারীদের জন্য যেসব নতুন সুযোগ সুবিধার জন্য আবেদন নিবেদন করতে শুরু করেছিলেন, সেসব কিন্তু বহুআগেই ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধের হিন্দুঘরের নারীদের দ্বারা সূচিত ও আলোচিত হয়ে গিয়েছিল। এভাবেই তখন হিন্দুঘরের নারীরা যেন পুরুষদের আন্দোলনের সমর্থনে নিজেদের গণস্বাক্ষর দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং ফরাসি বিপ্লবের ঢেউ ভারতের জীবনকেও স্পর্শ করেছিল। তৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যাপকদের অনেকেই ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারা দ্বারা পুষ্ট ছিলেন। আর তাঁদের ছাত্ররা, অর্থাৎ—‘বঙ্গীয় যুবকগণ’ তখন— “সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ-ভাঙ্গ-ভাঙ্গ এই তাঁহাদের মনের ভাব হইয়া দাঁড়াইল।” (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ: ৯৫-৯৬)
এই ভাঙ্গনের কাজ তখন ভেতরে বাইরে উভয় জায়গায় চলেছিল। আর এই ভাঙ্গনের ফলেই তখন থেকে নারীর কাছে পুরুষের চাওয়ার গুণগত পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে ১৮৩৮ সালের ৩রা মার্চ তারিখের জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল— “এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহারা অবশ্যই উচ্চ ও উত্তম কার্যে রত হইবেন। … অবস্থার পরিবর্তন হইলে কি মূর্খ স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্প্রীতি হইবেক। দিবসীয় মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরুষের সে সান্ত্বনা ও সাহায্যের আবশ্যকতা তাহা কি তিনি ঐ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন।” (জ্ঞানান্বেষণ, ৩রা মার্চ, ১৮৩৮, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৯-১০০)
নারীর উপরে পুরুষের এই নির্ভরশীলতা কিন্তু এযুগের আগে সৃষ্ট হওয়া সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে নারী ও পুরুষের উত্থান-পতন একই সঙ্গে ঘটেছে। এপ্রসঙ্গে কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য ছিল— “… a nation could never rise high in the scale of civilization, while illiterate mothers and wives obstructed its growth by perpetuating the moral degradation of the rising and the present generation.” (A prize Essay on Native Female Education, Rev. K. M. Banerjee, 1841, P- 16)
আর সমকালের বাংলার দুর্বল কুলবালারা ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন— “সম্পাদক মহাশয় এক ঔরসে ও এক গর্ভে জন্মিয়া আমরা এক ক্লেশের ভাগি কেন হইলাম রাজা কি আমাদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছে।” (সমাচার দর্পণ, ১লা জানুয়ারি, ১৮৪০, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ- ২৬০)
ইতিহাস বলে যে, এসময় থেকেই বিশ্বজুড়ে সমাজ ও পরিবারের সংজ্ঞা পরিবর্তিত হতে শুরু হয়েছিল। আর তাই ভারত তথা বাংলার নারীদের ক্ষেত্রেও রূপান্তর দেখা দিয়েছিল, এমনকি পরিবারের চেহারাও বদলে গিয়েছিল। একারণেই আলোচ্য সময়ের বাংলার নারীরা নিজেদের আর্দ্র কণ্ঠে তাঁদের প্রিয় পিতা ভ্রাতা ও বোদ্ধা সামাজিকদের কাছে আবেদন জানাতে গিয়ে বলেছিলেন— “হে প্রিয় পিতঃ ভ্রাতাগণ বিচার করিয়া কহুন দেখি যে আমাদিগকে আপনারা কিরূপ দুঃখিনী ও গোলামের ন্যায় অপমানিতা দেখিতেছেন।” (সমাচার দর্পণ, ২১শে মার্চ ১৮৩৫, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ- ২৫৮)
তবে তখনকার নারী জীবনের এই অশেষ বেদনা ও যন্ত্রণার কথা শুধুমাত্র সংবাদপত্রে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েই থেমে যায়নি। এর অনতিকাল পরেই সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় আধুনিকযুগের লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটেছিল এবং ঠাকুরাণী দাসী, থাকমণি দাসী, কৃষ্ণকামিনী দানী, কৈলাসকামিনী দেবী প্রমুখের রচনা প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল।#