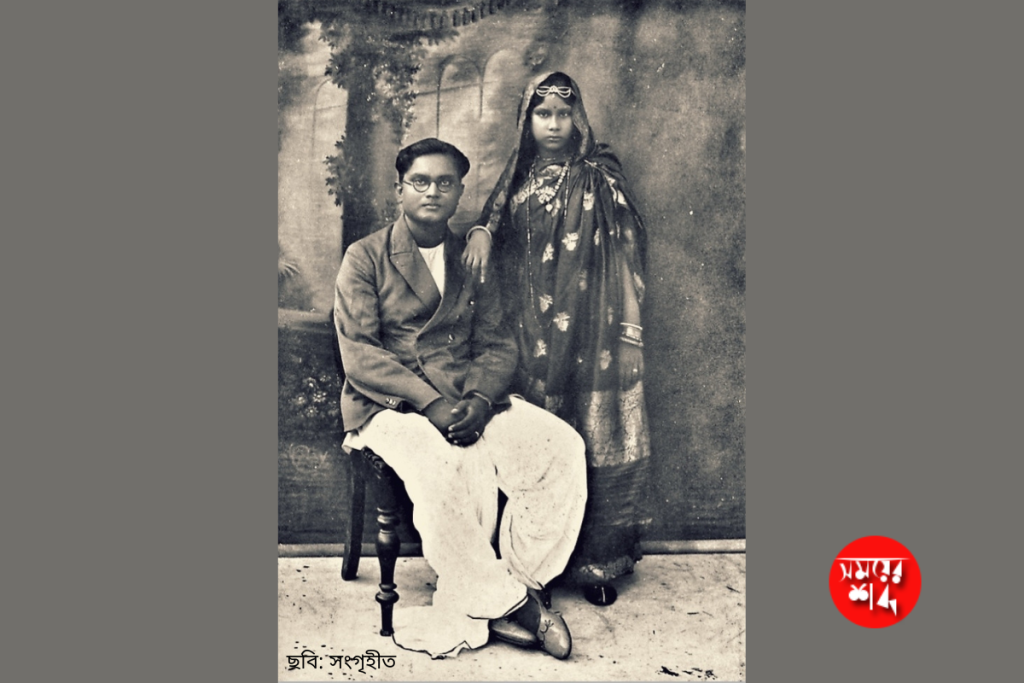বাল্যবিবাহ প্রথাটি ভারতবর্ষ তথা বাংলার অন্যতম প্রাচীন সামাজিক প্রথা হলেও একটাসময়ে এই প্রথাটি ঊনবিংশ শতকের বাংলার হিন্দুসমাজ-জীবনকে রীতিমত পর্যদস্তু করে তুলেছিল। ফলে তৎকালীন বাংলার হিন্দুসমাজের প্রগতিশীল সমাজ-নেতারা বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধিতায় নামতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঊনিশ শতকের বাংলার বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে, রামমোহন রায়ের ‘আত্মীয় সভা’র নামোল্লেখ করাটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই সভাতে রামমোহন ও অন্যান্য ব্যক্তিরা বাল্যবিবাহ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। গবেষকরা অনুমান করে থাকেন যে, রামমোহন ব্যক্তিগতভাবে বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। সেই সময়ের নিরিখে পনেরো বা ষোল বছর বয়সের আগে তিনি তাঁর নাতনীর বিবাহ দেননি বলেও জানা যায়। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত বাল্যবিবাহ নিয়ে তিনি নিজের লেখনী ধারণ করেননি এবং এসন্ধন্ধে কোন আন্দোলন গড়ে তুলবার প্রয়োজন বোধও করেননি। বস্তুতঃ সেযুগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে কেউই তেমনভাবে কোন আন্দোলনের কথা ভাবেন নি। এপ্রসঙ্গে এখানে কৃষ্ণনগর দেওয়ান ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের বক্তব্য অবশ্য উল্লেখ্য। তিনি লিখেছিলেন—
“বাল্যবিবাহের ইষ্টানিষ্ট কিছুই জানিতাম না, তদ্বিষয়ের কোন আন্দোলনও শুনিতে পাইতাম না এবং সকলকেই বালক বালিকার পরিণয়ের জন্য ব্যস্ত দেখিতাম।” (দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনচরিত, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৩১)
কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ঊনিশ শতকের প্রথম দিকেও কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে নি।
বাস্তবে ইতিহাস বলে যে, ওই শতকের চতুর্থ দশক থেকেই বাল্যবিবাহ নিয়ে সেযুগের গুণীজনদের মধ্যে প্রবল মতামত বিনিময় হতে শুরু করেছিল, এবং সেসবের মধ্যে দিয়েই একটাসময়ে এই আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। তখন ‘গুপ্তকবি’ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় বাল্যবিবাহ বিষয়ে বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হলেও, ১৮৫০ সালে সর্বশুভকরী পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বাল্যবিবাহের দোষ’ শিরোনামের প্রবন্ধটিকে এবিষয়ে প্রথম কোন সাড়া জাগানো রচনা বলা চলে। বাল্যবিবাহের দোষের প্রতি সেযুগের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ক্ষেত্রে উক্ত রচনাটি খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কার ও সামাজিক বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞাপত্রটি রচনা করে তাতে অনেকের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের ২ ও ৫ নং শর্তে বলা হয়েছিল—
“২. একাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।”
“৫. অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।”
(বিদ্যাসাগর, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৯৫ সাল, পৃ- ৩৩৫)
এভাবেই বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একটা জনমত গঠন করবার চেষ্টা করেছিলেন।
আরও পড়ুন: প্রাচীনকালে বাঙালি নারীর বসন
বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই বাংলার পত্রপত্রিকাতে বাল্যবিবাহ বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত বিনিময় বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ১৮৫৬ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বাল্যবিবাহ বিষয়ক একটি প্রবন্ধে এই প্রথাটি রদ করবার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল; এছাড়াও সেযুগের অন্যান্য পত্রিকাতেও এবিষয়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখালেখি চলেছিল। কিন্তু এবিষয়ে নির্ভেজাল ঐতিহাসিক সত্যিটি হল যে, তখন নানা লিখিত প্রবন্ধে ও মৌখিক আলোচনায় বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করা হলেও, সেকালের খুব অল্পসংখ্যক খ্যাতনামা প্রভাবশালী হিন্দুরাই এবিষয়ে কোন আন্দোলন সংগঠন করবার ব্যাপারে বাস্তব জীবনে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দই এবিষয়ে সবথেকে বেশি সোচ্চার হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়।
তখন ভারতসংস্কারক নামের একটি পত্রিকা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে রীতিমত জেহাদ ঘোষণা করে জনমত গঠন করবার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিল। ১৮৭৩ সালের ১৮ই জুলাই তারিখে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বাল্যবিবাহ’ নামক একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—
“হিন্দু সমাজে যতপ্রকার পাপ প্রখা আছে, বাল্যবিবাহ তন্মধ্যে প্রধান। কি শরীর কি মন সমুদয়ের দুরবস্থার প্রবল কারণ এক বাল্যবিবাহ।”
এই প্রবন্ধটিতে বাল্যবিবাহ রোধ করবার কিছু পদ্ধতির উল্লেখও করা হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধটি থেকে জানা যায় যে, তখন ঢাকা শহরের কিছু যুবক একত্রিত হয়ে ‘বাল্যবিবাহ নিবারণী’ নামের একটি সভা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সভার নিয়ম সম্বন্ধে ভারতসংস্কারক পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে জানানো হয়েছিল—
“সভার এই নিয়ম হইয়াছে যে কোন সভ্য যে বালিকার ১৪ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ না হইয়াছে, তাঁহাকে বিবাহ করিবেন না। পুরুষের বিবাহের কাল অন্যূন ২১ বৎসর নির্ধারিত হইয়াছে।”
শুধু এটুকুই নয়, ঐ সভাটি তখন— ‘মহাপাপ বাল্যবিবাহ’ — নামের একটি পত্রও জনগণের মধ্যে প্রচার করেছিল। সেকাজের জন্য উক্ত সভার সদস্যরা ব্রাহ্মসমাজের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।
আরও পড়ুন: আজকের বাংলায় লেখকদের পরিস্থিতি
তবে তখন শুধু ভারতসংস্কারক পত্রিকা নয়, সোমপ্রকাশ পত্রিকাও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোরালো প্রচারকার্য চালিয়েছিল। বিশুদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি হয়েও উক্ত পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পত্রিকাটির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সোমপ্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধের একজায়গায় তিনি বলেছিলেন—
“বাল্যবিবাহের উন্মূল একটা মহোপকারক বিষয়।” (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ- ২১৩)
আগেই বলা হয়েছে যে, বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করে ব্রাহ্মরাই তখন অন্যদের থেকে বেশি এগিয়ে এসেছিলেন। তবে সোমপ্রকাশ কিন্তু সবসময়ে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁদের সব কাজের প্রশংসা করতে পারেনি।
১৮৭০ সালে ‘ব্রহ্মানন্দ’ কেশবচন্দ্র সেন ‘ভারত সংস্কার সভা’ বা ‘ইণ্ডিয়ান রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপরে এই সভার পক্ষ থেকে বিবাহের বিজ্ঞানসম্মত বয়স নির্ধারণ করা হলে, কেশবচন্দ্র সেই বয়স অনুযায়ী একটি বিবাহবিধি প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন। এবিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ তখন বেশ জোরালো আন্দোলনই করেছিল। এপ্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন—
“এই ইণ্ডিয়ান রিফরম্ অ্যাসোসিয়েশন–এর পক্ষ হইতে কেশববাবু আর একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এক মুদ্রিত পত্র দ্বারা দেশের প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণের নিকট হইতে, এ দেশীয় বালিকাগণের বিবাহের উপযুক্ত কাল কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে অধিকাংশ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ডাক্তার ১৬ বৎসরের ঊর্ধ্বে সেই কালকে নির্দেশ করেন। কেবল ডাক্তার চার্লস চতুর্দশ বর্ষকে সর্বনিম্ন বয়স বলিয়া নির্দেশ করেন। তদনুসারে ১৮৭২ সালের তিন আইনে চতুর্দশ বর্ষকে বালিকার সর্বনিম্ন বিবাহের বয়স বলিয়া নির্দেশ করা হয়। তিন আইনের এই আন্দোলনে আমরা সকলেই তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলাম।” (আত্মচরিত, শিবনাথ শাস্ত্রী, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১০৮)
তবে এবিষয়ে আদি ব্রাহ্ম সমাজের কাছ থেকে কেবশচন্দ্র সেনকে বিস্তর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইনটি অবশ্য বিধিবদ্ধ হয়েছিল; তবে শেষপর্যন্ত যেভাবে সেটিকে চালু করা হয়েছিল, তাতে কেশবচন্দ্র সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সোমপ্রকাশ পত্রিকাও তখন কেশবচন্দ্র সেন প্রস্তাবিত তিন আইনের ঘোরতর বিরোধিতা করেছিল। উক্ত আইনটি বিধিবদ্ধ হওয়ার আগেই সোমপ্রকাশ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল—
“ব্রাহ্মবিবাহ বিষয়ক আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে, তাহাতে নানকল্প বয়স চতুদ্দশ বর্ষ স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু ব্রাহ্মেরা ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই, অধিক বয়সে বিবাহ হওয়াতেই ইউরোপীয় জাতি সকল এত বলবান ও তেজস্বী। ইউরোপীয়দিগের বলবত্তা ও তেজস্বিতার ইহাই প্রধান কারণ কিনা, এ স্থলে তাহার বিচার অনাবশ্যক। এ স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, দুর্ব্বলতার প্রকৃত কারণ বিবাহ, না অসাময়িক ও অসঙ্গত স্ত্রীসহবাস? যদি শেষোক্তটি কারণ হয়, তাহা হইলে আইন কি তন্নিবারণে সমর্থ হইবে?” (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; পৃ- ২৩৯)
আরও পড়ুন: ঊনিশ শতকের বাংলার মুসলিম সমাজ ও আধুনিকতা
সোমপ্রকাশ পত্রিকার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পত্রিকাটির তৎকালীন সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যেমন একেবারে বাল্যবয়সের বিবাহকে বরদাস্ত করতে পারেননি, তেমনি আবার খুব বেশি বয়সের বিবাহকেও মেনে নিতে চাননি। সেই সময়ে বাল্যবিবাহরোধ বিষয়ে আরেকটি একটি নতুন প্রস্তাবের উত্থাপন ঘটেছিল। ১৮৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে তৎকালীন বাংলার সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের ডিরেক্টর সাহেবের কাছে এ. ডাব্লিউ. গ্যারেট যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেটি থেকে এই বিষয়টি বুঝতে পারা সম্ভব। সেই পত্রে গ্যারেট সাহেব লিখেছিলেন—
“আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, বাল্যবিবাহ বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। প্রতিবর্ষেই ইনস্পেক্টর, ডিরেক্টর এবং গবর্ণমেন্ট এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে কন্যাদিগকে বিবাহের পূর্ব্বে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার অভিলাষ থাকিলেও হিন্দু সমাজের শিক্ষিত লোকেরাও তাঁহাদের কন্যাদিগকে ১০/১১ বৎসরের সময়ে বিবাহ দিয়া থাকেন। … ২০ বৎসর পূর্ব্বে বালিকাদিগের ৭/৮ বৎসরের সময় বিবাহ হইত, এক্ষণে ১০/১২ বৎসরের সময়ে বিবাহ হইয়া থাকে। এই যে কথঞ্চিৎ উন্নতি দেখা যায়, যাহাতে সত্বরে তাহা বৃদ্ধি হয়, তদুদ্দেশেই আমি এই প্রস্তাব করিলাম। সেই প্রস্তাব (যাহা কতিপয় হিন্দু সম্ভ্রান্ত লোক কর্তৃক প্রথম উপস্থিত করা হয়) এই যে—এই নিয়ম প্রকাশের পর যাঁহারা বিবাহ করিবে তাঁহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দেওয়া না হয়।” [সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; পৃ: ২৮৫-৮৬) কিন্তু গ্যারেট সাহেবের উপরোক্ত প্রস্তাবের মধ্যে ত্রুটি ছিল, কেননা— সেযুগে এভাবে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না।
এরপরে ১৮৮৫ সালে অবাঙালী বাইরাম জি. এস. মালাবারি বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন চালিয়েছিলেন বলে ইতিহাস থেকে জানা যায়। মালাবারির মতে বাল্যবিবাহ বিদূরিত করবার উপায় কি ছিল, সেটা নিম্নলিখিত অংশ থেকে বুঝতে পারা সম্ভব—
“শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ এই কথাটি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া দিন কোন বিবাহিত পুরুষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে দিবেন না। প্রস্তাবলেখক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এই পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহারা সভা করিয়া বিবাহের একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই স্থির করুন, তাঁহারা ন্যূন বয়সে বিবাহ করিবেন না এবং অতি বালিকারও পাণিগ্রহণ করিবেন না। তিনি গবর্ণমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কর্তাদিগকে এই নিয়ম অবলম্বন করিবার অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা তুল্য গুণ সম্পন্ন দুইজন কর্মার্থী উপস্থিত হইলে বিবাহিতকে পরিত্যাগ করিয়া অবিবাহিতকে কৰ্ম্ম দেন।” (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত; পৃ- ৩২৪)
বাল্যবিবাহ নিবারণ করবার জন্য মালাবারি আরও কয়েকটি উপায় নির্ধারণ করেছিলেন বলে জানা যায়। মালাবারির বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রভাব তৎকালীন ভারতবর্ষে মোটামুটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লেও সমকালীন বাংলা সমেত অন্যান্য প্রদেশের অনেকেই কিন্তু তাঁর প্রস্তাবগুলিকে গ্রহণীয় বলে মনে করেনি। একটা সময়ে মালাবারি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর প্রস্তাবিত বাল্যবিবাহ নিবারণের উপায়গুলি অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং সেই কারণে পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর প্রস্তাবকে সংশোধিত করে নিয়েছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলি সর্বজনের স্বীকৃতিলাভ করতে পারে নি। অবশ্য একইসাথে একথাও সত্যি যে, তাঁর বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলন অবহেলা করবার মতোও ছিল না। পণ্ডিতদের মতে বাল্যবিবাহ রোধে মালাবারির কর্ম পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকলেও তাঁর উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে না। তাছাড়া দেশজুড়ে বাল্যবিবাহবিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতেও তিনি সফল হয়েছিলেন। সবথেকে বড় সত্যিটা হল যে— খৃষ্টীয় ঊনিশ শতকে মালাবারির মত কোন বাঙালিই বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে এমনতর তীব্র ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হননি বা এবিষয়ে কোন আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন নি। বস্তুতঃ ঊনিশ শতকের বাংলায় বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যে পরিমাণে লেখালেখি হয়েছিল, সেই পরিমাণে কোন আন্দোলন গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়নি। এই কারণে সমকালীন অনেকে আক্ষেপও করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এই কারণেই ঊনিশ শতকের অষ্টম দশকেও সোমপ্রকাশ পত্রিকাকে মালাবারির সমালোচনা করতে গিয়ে লিখতে হয়েছিল—
“কিন্তু দূঃখের বিষয় আজ পূর্ণান্ত হিন্দু সমাজ মধ্যে বাল্যবিবাহ নিবারণের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এ বিষয়ে কিঞ্চিং চেষ্টা করিয়াছেন সত্য, পুস্তিকা প্রচার, বক্তৃতা ও অন্য অন্য উপায়ে আন্দোলন করিয়া তাঁহারা এই কুপ্রথার প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টি আবর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সমাজের লোক নন বলিয়া তাঁহাদের সমুদয় যত্ন ও চেষ্টা বিফল হইয়া গিয়াছে, সমাজ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তাঁহাদের যত্নে কেবল ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই যাহা কিছু বাল্যবিবাহের নিবারণ করিতে পারিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের স্থির ধারণা এই যে মালাবারি মহাশয় আজ যে রূপ যত্ন করিতেছেন, এবং কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্রাহ্ম সম্প্রদায় যতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দু সমাজভুক্ত কোনও পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ততটুকু যত্ন করিতেন এতদিনে এই কুপ্রথা বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়া যাইত।” (সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, পৃ- ৩২৬)
সোমপ্রকাশ পত্রিকার উপরোক্ত বক্তব্যকে ঊনিশ শতকের বাংলার বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যেতে পারে।
বাল্যবিবাহবিরোধী আন্দোলনের সময়ে বাংলার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তখন সেই সমাজের অনেকেই পুস্তক-পুস্তিকা বা প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে বাল্যবিবাহের পক্ষে নিজেদের মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার সরকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১২৯৪ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের চতুর্থ সংখ্যার নবজীবন পত্রিকায় মুদ্রিত ‘হিন্দুবিবাহ’ নামক প্রবন্ধে বাল্যবিবাহকে সমর্থন করে তিনি বলেছিলেন—
“বাল্যবিবাহ প্রশস্ত।”
আরও পড়ুন: রাসসুন্দরী দেবী
এছাড়া আলোচ্য সময়ে বাল্যবিবাহ সম্পর্কিত আন্দোলনের ব্যাপারে আরেকদল ব্যক্তি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, ১২৯২ বঙ্গাব্দের ৭ম সংখ্যার সমাজদীপিকা পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে জনৈক প্রবন্ধ রচয়িতা জানিয়েছিলেন—
“আমরা না বালিকার, না পূর্ণ যুবতীর বিবাহে পক্ষপাতী। আমাদের মত, দশ বৎসর হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের মুখ্যকাল। … স্ত্রীগণের দশ ও পুরুষের ষোড়শ বর্ষাবধি বিবাহই যুক্তিযুক্ত।”
এছাড়া সেযুগে আরও একদল মানুষ ছিলেন, যাঁরা বাল্যবিবাহের সমর্থক না হলেও কোন আইনের দ্বারা সেটাকে নিষিদ্ধ করবারও পক্ষপাতী ছিলেন না।
বস্তুতঃ বাল্যবিবাহের বিষয়ে সেযুগের নানা মহলেই নানা মতের বিনিময় চলেছিল, তখন— মৌখিক ও লিখিত —এই দু’ভাবেই মতামতের লড়াই ঘটেছিল। কিন্তু বাল্যবিবাহকে চিরতরে অবলোপ করবার বিষয়ে সেযুগের কোন চেষ্টাই শেষপর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। তখনকার উন্নত ব্রাহ্ম ও শিক্ষিত কিছু হিন্দুরা বাল্যবিবাহকে পরিহার করে চললেও বৃহত্তর হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন আগে যেমনটি ছিল পরেও ঠিক তেমনটিই থেকে গিয়েছিল।#