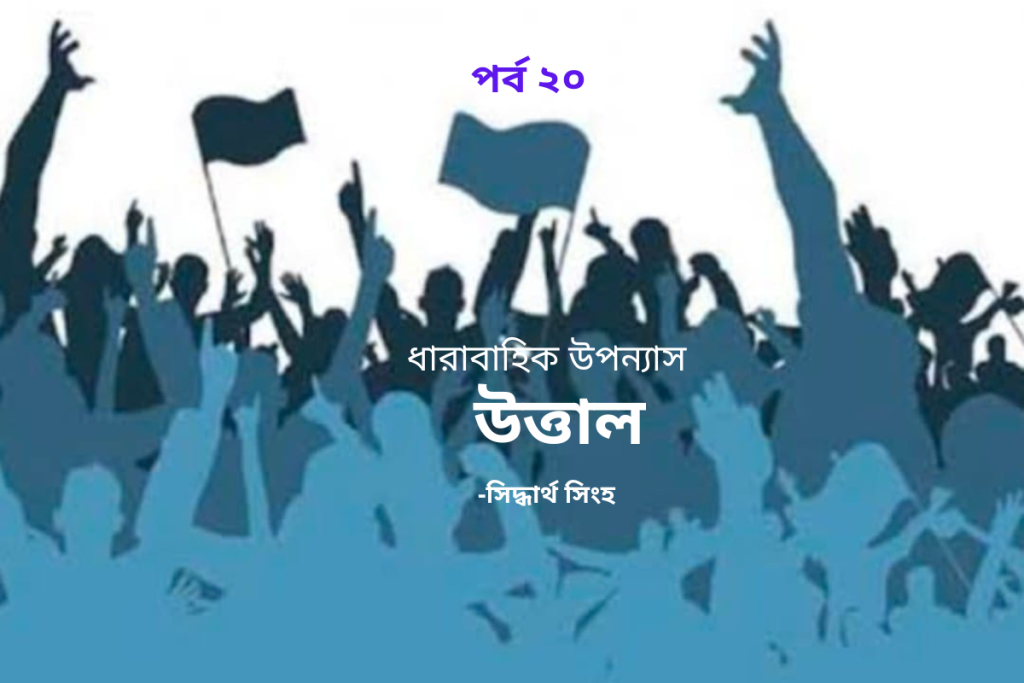।। পর্ব – কুড়ি ।।
কৌশিক সেন, জয়া মিত্র, ব্রাত্য বসু, অর্পিতা ঘোষ, সমীর আইচ, জয় গোস্বামী, দোলা সেনদের ধুধু মাঠের ভিতর দিয়ে দোবাঁদি গ্রামে নিয়ে এলেন রাজকুমার ভুল। ও গোপালনগরে থাকলেও ওকে এখানকার সবাই চেনেন। এই গ্রামে এক ঘর বাগদি ছাড়া সবাই বাউরি সম্প্রদায়ের। কারও পদবি পাত্র, মৈত্রী, দাস খামারু, হারারি। কারও কোটাল, বাগাল, মাসিক, বৈরাগী তো কারও আবার সর্দার, ধীবর বা দিগর। পদবি বা সম্প্রদায়গত মর্যাদা যা-ই হোক না কেন, এঁদের সবার সঙ্গে সবার কিন্তু অগাধ মেলামেশা, খাওয়াদাওয়া, কারও বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠান হলে একজন আরেক জনকে নিমন্তন্ন করা। এমনকী বিয়ে-থা পর্যন্তও হয়।
অনেক বছর আগে জুলকিয়া খালের ও পারের ধাড়াপাড়া থেকে গুটিকতক মানুষ দল বেঁধে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখন তাঁদের সন্তানসন্ততি বাড়তে বাড়তে প্রায় নব্বই ঘর হয়ে গেছে। একই জায়গায় পর পর সার দিয়ে ঘর। তার সামনে দিয়ে মাটির রাস্তা। বর্ষার সময় কাদা থিকথিক করে। হাঁটা বড় মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। দু’-তিনটে পাকাঘর বাদ দিলে সব ক’টাই মাটির। উপরে টালি বা খড়ের চাল। সারা গ্রামে একটাই তিন তলা পাকাবাড়ি। সেটা কানাই সর্দারের। তিনি ভাগচাষি। তাঁর তিন ছেলের মধ্যে দু’ছেলেই নৈনিতালে গত দশ বছর ধরে সোনা পালিশের কাজ করছেন। তাঁদের পাঠানো টাকাতেই নাকি তাঁদের এত বৈভব। তবুও ওঁরা ছাড়া এই গ্রামের আর কারওরই বাইরে যাওয়ার তেমন নজির নেই। আগ্রহও নেই।
ওঁদের মতো অত বড় নাহলেও এই গ্রামেই আর একটা পাকাবাড়ি আছে। সীমান্ত পাত্রের। তাঁদের আবার একটা মোটরগাড়িও আছে। তাই গ্রামের মধ্যে তাঁদের আর্থিক অবস্থা সত্যিই চোখে পড়ার মতো। অবস্থা যত ভালই হোক, এখানকার সবাই কিন্তু কৃষিজীবী। চাষ করেই খায়। দু’-একটা ঘর বাদ দিলে ওঁদের কারও কোনও জমি নেই। এমনকী, একটি মাত্র পরিবার ছাড়া কেউ নথিভুক্ত ভাগচাষিও নন।
বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সহায়তায় এখানে একটা প্রাথমিক স্কুল গড়ে উঠেছে। সেখানে গ্রামের বাচ্চারা সামান্য কয়েক ক্লাস লেখাপড়া করে। তার পর একটু বড় হতে না হতেই বাড়ির কাছাকাছি কোনও মাঠে বাবা-মা, কাকা-কাকি, দাদু, দাদা-দিদির মতো ওরাও চাষের কাজে লেগে যায়। সে ভাবে দেখলে বলা যায়, চাষের মধ্যেই বাউরিপাড়ার জীবন। চাষের মধ্যেই বাউরিপাড়ার মরণ।
সমীর আইচ ডাকাবুকো মানুষ। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ছবি আঁকলেও তাঁর চেহারাটাই এমন যে, যে-কোনও লোকই তাঁকে দেখলে ভয় পাবেন। তবু কী অদ্ভুত কাণ্ড, যাঁকে সারাক্ষণ টিভির পর্দায় অভিনয় করতে দেখা যায়, সেই কৌশিক সেনকে একেবারে সামনে দেখেও, তাঁর কাছে নয়, ওই গ্রামের গৃহবধূ বিজয়া দেবী নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন সেই সমীরবাবুর দিকে। না, গ্রাম্যবধূর মতো তাঁর মাথায় এক-হাত ঘোমটা দেওয়া নেই। দশ বছর আগে স্বামীকে হারিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে দু’মুঠো অন্ন জোটাবার জন্য তিনি এখন মরিয়া।
আরও পড়ুন: ধারাবাহিক উপন্যাস ‘উত্তাল ১৯
এঁদের একটাই সমস্যা, কাকে কতটুকু কী বলতে হয় এঁরা জানেন না। গুছিয়েও কথা বলতে পারেন না। উনি যেন নিজের জীবনী বলছেন কাউকে, এমন ভাবে বলতে শুরু করলেন– আমি বিয়ে হয়ে আসার পর প্রথম কয়েক বছর মাঠের কাজ করিনি। আমাদের বড় পরিবার। আঠারো জন লোক। দেওর-ননদ তখন সব ছোট ছোট ছিল। তাদের রান্নাবান্না, খাওয়ানো-দাওয়ানোর জন্য একটা লোক সব সময় বাড়িতে থাকতে হত। শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী, দেওর– সবাই মাঠে যেত কাজ করতে। আমি সংসার সামলাতাম। বছর তিনেক পর ওরা একটু বড় হতেই আমি চাষের কাজে বেররুতে শুরু করি। তখন ছ’টাকা রোজ ছিল। কিন্তু এত অভাব ছিল না। এখন পঞ্চাশ টাকা রোজে কাজ করেও থৈ পাচ্ছি না।
– ছ’টাকা থেকে একেবারে পঞ্চাশ টাকা রোজ। কী ভাবে বাড়ল?
– আপনা-আপনিই বেড়েছে। এর জন্য আমাদের কোনও আন্দোলন করতে হয়নি। তা বলে আপনি আবার ভাববেন না, এক লাফে ছ’টাকা থেকে বেড়ে পঞ্চাশ টাকা হয়েছে। আগে যখন রমরম করে চাষের কাজ হত, প্রত্যেক বছর কিছু কিছু করে বাড়ত। বাজারে যখন চাল-ডালের দাম হুহু করে বাড়তে লাগল, আনাজপত্তের দাম আকাশছোঁয়া হতে লাগল, তখন ছ’টাকা থেকে বেড়ে খেতমজুরি দশ টাকা হল। তার পর পনেরো টাকা। তার পর কুড়ি টাকা। বছরে, কখনও কখনও এক বছর অন্তর পাঁচ টাকা করে বাড়তে বাড়তে এখন পঞ্চাশ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।
– জমির মালিকরা এমনিই বাড়িয়ে দিল?
– হ্যাঁ, আসলে তখন তো এ রকম ছিল না। আমরা টাকার বিনিময়ে কাজ করলেও আমরা ছিলাম মনিবদের বাড়িরই একজন। তাঁদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী। ফলে বাজারের দাম বাড়ছে দেখে, আমাদের কথা ভেবে ওঁরা নিজেরাই আমাদের রোজ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।
– বাহ্, দারুণ তো। কিন্তু রোজই কি কাজ পেতেন?
– না, রোজ না। এই ধরুন অঘ্রাণ মাসটা কাজ হত। পৌষ মাসটা পুরোটা হত না। দশ-পনেরো দিন ধান ঝাড়া হত। মাঘ মাসটা অফ সিজিন। সে সময় কেউ কেউ অবশ্য বোরো ধান চাষ করত। তখন কাজ হত। তাও মাঘ মাস থেকে ফাল্গুন মাসের দশ-পনেরো তারিখ অবধি, ধরুন মোটামুটি এক মাস কাজ হত। চৈত্র মাসটায় আবার আট-দশ দিন নিড়ানোর কাজ পেতাম। তার পর জৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাটা-ঝাড়ার কাজ থাকত। ভাগ্য ভাল থাকলে আষাঢ় মাসেও দু’-চার দিন টুকটাক হয়তো হত। খুব ভাল কাজ হত শুধু শ্রাবণ মাসে। তাও বাদ-টাদ দিয়ে সব মিলিয়ে হিসেব করলে বছরে ধরুন আট-দশ মাস কাজ হতই।
– আপনি হঠাৎ এ কাজে এলেন কেন?
– কী করব! স্বামী মারা গেল। বাচ্চাকাচ্চা মানুষ করতে হবে। মেয়ে আছে। তার বিয়ে-থা দিতে হবে। কাজ না করলে হবে? নিজের পেটটাও তো চালাতে হবে, নাকি?
ওঁরা কথা বলছিলেন। বলেই যাচ্ছিলেন।
যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছু দিন ধরে খুব জ্বরে ভুগছিলেন কৌশিক সেন। সারা গা-হাত-পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা। তবু সে সবের তোয়াক্কা না করেই যেমন নিয়মিত নাটক করে চলেছেন মঞ্চে, একটার পর একটা ধারাবাহিকে রোজই প্রায় শট দিয়ে যাচ্ছেন, তেমনি অসহায় মানুষের ওপরে নির্যাতনের কথা শুনে আর চুপ করে বসে থাকতে পারেননি তিনি। ছুটে এসেছেন এখানে। পাশ থেকে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, যখন কাজ থাকে না তখন কী করেন?
বিজয়া দেবী বললেন, আমার বড়দা মানে ভাসুর মাছ ধরার জন্য জুলকিয়া খাল ছাড়াও আশপাশের অনেকগুলো পুকুরে ঘুনি বসাতেন। আটুল বসাতেন। তাঁর দেখাদেখি আমিও ঘুনি পাততে শুরু করলাম। কোনও দিন পাঁচশো, কোনও দিন এক কিলো, আবার কোনও দিন দেড় কিলো মাছ পড়ত। যা পড়ত, তা-ই বেড়াবেড়ির বাজারে নিয়ে যেতাম। বিক্রি হয়ে যেত।
– যে দিন মাছ পড়ত না, সে দিন কী করতেন?
উনি বললেন, সে দিন মাঠ থেকে যতটা পারা যায় শাকপাতা তুলে কিংবা পুকুর থেকে শামুক-গেঁড়ি তুলে, মোট কথা, এটা না হলে ওটা, ওটা না হলে সেটা, কিছু না কিছু একটা নিয়ে বাজারে চলে যেতাম। আর যা নিয়ে যেতাম, তা-ই বিক্রি হয়ে যেত। এই ভাবেই কোনও রকমে সংসারটা চালাতাম।
– এখন তো চাষবাস খুব একটা হচ্ছে না। ফলে আপনাদের তেমন কোনও কাজও নেই। এখন কী ওই ভাবেই চলছেন?
– তা ছাড়া আর কী করব?
কৌশিক বললেন, আপনি যে কাজের কথা বলছেন, সেটা তো সকালের দিকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজ। বাকি সময় কী করেন?
উনি বললেন, বাঁশ কেটে সরু সরু ছিলে করে বড়দা ঘুনি তৈরি করতেন। তাঁর পাশে থেকে থেকে আমিও ওগুলো তৈরি করা শিখে নিয়েছি। যে দিন কোথাও কোনও কাজ পাই না, সে দিন ওগুলিই বানাই।
– বছরের কোন সময়টা আপনাদের কাছে সবচেয়ে বেশি কষ্টের?
– কার্তিক মাসটা।
– কেন?
– তখন তো পুকুরের জলটা শুকিয়ে যায়। মাছ তো নয়ই, গুগলি-শামুক-গেঁড়ি কিছুই পাওয়া যায় না। শাকপাতাও সে ভাবে মেলে না।
কৌশিক জানতে চাইলেন, তখন কী করেন?
– ধার-দেনা করি।
– তখন তো আপনাদের সবারই এক দশা। কার কাছে ধার করেন?
বিজয়া দেবী বললেন, এখানে এক সাহাবাড়ি আছে। ওঁদের কাছে জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়ে আসি।
– বন্ধক রেখে?
– না হলে ধার দেবে কেন? যদি দিতে না পারি? খালি হাতে কেউ কিছু দেয়? আবার যখন কাজ পাই, সুদে-আসলে যা হয়, একেবারে মিটিয়ে দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে আনি।
– সাহাবাড়ি? এখানে কি ওঁরাই সব চেয়ে বড়লোক নাকি?
– না না, বারুইরা আছে না? ঘোষেরাও কম যায় না। এই এলাকায় তো এঁদের তিন জনেরই সবচেয়ে বেশি জমি।
– ওঁদের তিন জনের জমিতেই এখানকার লোকেরা মূলত খেতমজুর খাটে, না?
– কথাটা ভুল না। খাটে। তবে কেউ কেউ আবার জমির মালিকের কাছ থেকে এক-একটা ফসলের সিজিনে জমি নিয়ে ভাগেও চাষ করে। অবশ্য আমন চাষের সময় জমি পাওয়াটা খুব ভাগ্যের ব্যাপার।
কৌশিক জিজ্ঞেস করলেন, কেন? ভাগ্যের ব্যাপার কেন?
– ওটাই তো আসল চাষ। যাঁদের জমি, তাঁরা ওই চাষটা নিজেরাই করে।
– নিজেরা করে! অবাক হয়ে গেলেন কৌশিক।
উনি বললেন, নিজেরা করবে কেন? ওরা মুনিশ দিয়ে চাষ করায়। কিন্তু কিছুতেই ভাগে চাষ করাতে চায় না।
– ও… তা হলে কখন চায়?
– বোরো চাষের সময়। অনেকেই তো ওই চাষটা করতে চায় না, তাই।
কৌশিক জানতে চাইলেন, যে যাঁর জমিতে ভাগে চাষ করে, সে-ই কি তাঁর জমিতেই বরাবর ভাগচাষ করে?
– না, ফসল অনুযায়ী জমির মালিকেরা প্রতি বছর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এক-একজনকে ভাগ চাষের জন্য লিজ বা ঠিকায় জমি দেন। একই লোককে সাধারণত একনাগাড়ে পর পর তিন-চার বার জমি দেন না।
– তাই নাকি?
বিজয়া দেবী বললেন, হ্যাঁ, এখানকার লোকেরা এটাকে বলে ‘ভাগে-ভূতে-খাওয়া’।
– ভাগে-ভূতে-খাওয়া? অদ্ভুত কথা তো! আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, বরাবরের জন্য একজনকে ভাগচাষ করতে দিলেই তো সুবিধে, তাই না? সেটা না দিয়ে ওঁরা এই ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একেক বার একেক জনকে জমি দেন কেন?
উনি বললেন, সবাই তো আর সমান হয় না। একই লোককে পর পর কয়েক বছর জমি দিলে সে যদি ভাগচাষি হিসেবে নিজের নাম নথিভূক্ত করতে চান, তখন?
তাঁর কথা শুনে মাথা দোলালেন কৌশিক। যেন বলতে চাইলেন, ও বুঝেছি।
আরও পড়ুন: পরব ভাঙা হাটের হাটুরে ১
ও দিকে তখন এই গ্রামের আরও কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন দোলা সেন। তিনি কথায় কথায় একজনের কাছে জানতে চাইলেন, আমরা তো আসার সময় দেখছিলাম, ঘরে ঘরে লোকেরা মাছ ধরার জাল বুনছেন। কেউ কেউ বাঁশের কঞ্চি কেটে মাছ ধরার নানা রকম ফাঁদ তৈরি করছেন। ওগুলো বিক্রি করে ওঁরা নিশ্চয়ই যথেষ্ট টাকা পান। তা হলে তার পরেও আপনাদের এখানে এত অভাব-অনটন কেন?
উনি বললেন, অফ সিজিনে এমনটাই হয়। আবার ঠিক মতো চাষের কাজ-বাজ শুরু হলে তখন সমস্ত খরচখরচা বাঁচিয়ে কেউ কেউ কিছু জমায়ও। বেশ কয়েক জন তো পোস্ট অফিসেও টাকা রাখে। শুনলাম, সড়ক পথের ওখানে যে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কটা হয়েছে, সেখানেও নাকি কেউ কেউ টাকা জমায়।
দোলা দেবী বললেন, গ্রামে ঢোকার সময় দেখলাম এখানে সেখানে ছাগল চরে বেড়াচ্ছে। হাঁস-মুরগি ঘুরছে। ওগুলো কাদের?
উনি বললেন, ওগুলি সব আমাদেরই। এই গ্রামেরই কারও না কারও।
– ওগুলো থেকে কিছু আয় হয় না?
– কেন হবে না? ওগুলি হচ্ছে অসময়ের সম্বল।
– অসময়ের সম্বল মানে?
উনি বললেন, অসময় মানে বড় কোনও অসুখ-বিসুখ করলে কিংবা তেমন কোনও বিপদ-আপদে পড়লে অথবা বিয়ে-থা-র ব্যাপার হলে, মানে আচমকা মোটা টাকার দরকার হলে, তখন ওগুলি বিক্রি করেই সেই সমস্যার সামাল দেওয়া হয়।
– এ ছাড়া এখানকার লোকদের আর কোনও রোজগারের রাস্তা নেই?
– থাকবে না কেন? আছে।
দোলা দেবী জানতে চাইলেন, সেটা কী?
– যেমন ধরুন, যাঁদের পাওয়ার টিলা আছে, মানে ছোট ট্রাক্টর। অনেকে সেগুলি চালিয়েও প্রচুর টাকা আয় করেন। এই গ্রামে অন্তত দশ জনের সাইকেল-ভ্যান আছে। তাঁরা সেগুলি চালিয়ে তাঁদের সংসারটা ঠিকই চালিয়ে নিচ্ছেন।
– এ ছাড়া?
– এ ছাড়া! এ ছাড়া! উনি এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে মাথা চুলকোতে লাগলেন। দোলা দেবী বুঝতে পারলেন, উনি আর কিছু মনে করতে পারছেন না। তাই শহর বা শহরতলির যে-কোনও ছেলেমেয়ের পক্ষেই পকেট খরচা বা হাতখরচা তোলার জন্য যেটা সবচেয়ে সহজ রাস্তা, উনি নিজে থেকেই সেই প্রাথমিক রাস্তাটার কথাই বললেন, এখানে কেউ টিউশুনি-টুনি করে না? বা কেউ কোনও কোচিং-টোচিং চালায় না?
উনি বললেন, না। এখানে কেউ পড়াশোনা করলে তো টিউশুনি করবে কিংবা কোচিং খুলবে। সে সবের কোনও বালাই নেই এখানে।
আরও পড়ুন: রথযাত্রার সাংস্কৃতিক উৎস
গ্রামবাসীদের ছোট যে জটলার মধ্যে জয়া মিত্র দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজনকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সারা বছরই শুধু পরিশ্রম আর দুঃখ-দুর্দশা? তা হলে আনন্দ করেন কখন? দুর্গাপুজোর সময়?
ভদ্রলোক এক গাল হেসে বললেন, না, দুর্গাপুজোর সময় না। আমাদের এই দোবাঁদি গ্রামের সবচেয়ে বড় উৎসব হল মনসা পুজো।
জয়া দেবী মাঝে মাঝেই গ্রামগঞ্জে ছুটে যান। তিনি জানেন, মানুষ শক্তের ভক্ত। যাঁরা তাঁদের ওপরে আক্রমণ করতে পারে, জীবন সংশয় ঘটাতে পারে, তাঁদের ঠান্ডা করার জন্য তাঁদের সর্বময় কর্তার আরাধনা করা হয় সর্বত্র। যেমন, সুন্দরবন হল বাঘের জায়গা। মাছ ধরতে গেলে বা জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলে কিংবা মধু পাড়তে গেলে আড়ালে-আবডালে ঘাপটি মেরে বসে থাকা বাঘেরা আচমকা মানুষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু’-চার জন সৌভাগ্যক্রমে কোনও রকমে বেঁচে গেলেও বেশির ভাগেরই কপালে জোটে অবধারিত মৃত্যু। তাই ওখানকার মানুষেরা ও সব জায়গায় যাওয়ার আগে কিংবা এমনিই, বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়কে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করেন। বনের দেবী বনবিবির মন্দিরও গড়ে তোলেন যত্রতত্র। মানত পূরণ হলেই তাঁর উদ্দেশে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন মুরগি।
যখন গ্রামে গ্রামে, এমনকী শহরেও চিকেন পক্স বা মায়ের দয়া দেখা দেয়, তখন ওই রোগের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য লোকেরা শীতলা মায়ের শরণাপন্ন হন। ঠিক তেমনি, এখনও এই দেশের আনাচে কানাচে, যেখানে জলজঙ্গলই বেশি, সাপের উপদ্রপ অহরহ লেগেই আছে, সাপের ছোবলে মৃত্যুর হার যে-কোনও লোকের ঘুম কেড়ে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, সেই সব জায়গাতেই সাপের দেবী মনসা মায়ের পুজোর বহরও অনেক বেশি। তিনি জানেন, ওই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, মনসা মাকে তুষ্ট করতে পারলেই, তাঁর বাহনরাও শান্ত থাকবে। সহজে কাউকে দংশন করবে না। এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মানুষের কী বিশ্বাস, না! হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবেই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, মনসা পুজো!
আরও পড়ুন: অনুসুয়ার মা
জয়া দেবীকে অবাক হতে দেখে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মনসা পুজো। আমাদের এখানে মনসা পুজো প্রতি বছর খুব ধুমধাম করে হয়। তখন সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে সারা গ্রাম মেতে ওঠে। সবাই যোগ দেয়। পুজোর আয়োজন করে মনসামাতা ক্লাব।
– সেটা কোথায়?
– ওই মনসাতলার পাশেই আমাদের ক্লাবঘর।
– আপনি কি ওই ক্লাবের মেম্বার নাকি?
তিনি বললেন, শুধু আমি নই। এই গ্রামের প্রত্যেকটা ছেলে-বুড়োই ওই ক্লাবের সদস্য।
– তাই?
– হ্যাঁ।
জয়া দেবী জানতে চাইলেন, পুজো ছাড়া ওই ক্লাব আর কী কী করে? খেলাধুলো?
– হ্যাঁ, খেলাধুলোও করে। তবে সেটা তেমন কিছু নয়। আমাদের মূল লক্ষ্য হল, গ্রামের কেউ অসুবিধায় পড়লে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো।
– পাশে গিয়ে দাঁড়ানো মানে? টাকা-পয়সা দিয়ে?
– হ্যাঁ, আমরা টাকা-পয়সা দিই তো।
– কোথায় পান?
তিনি বললেন, আমাদের একটা তহবিল আছে।
– তহবিল!
– হ্যাঁ, তহবিল। আমরা গ্রামের সবাই মিলে গায়ে-গতরে খেটে সেটা তৈরি করেছি।
জয়া দেবী প্রশ্ন করলেন, কী ভাবে?
– মাছ ধরে। ধান বিক্রি করে, এ ছাড়া পুজোর চাঁদা থেকে কিছুটা বাঁচিয়ে।
– তাতেই ফান্ড তৈরি হয়ে গেল?
তিনি বললেন, শুধু ওতেই হয়নি। গ্রামের ভিতরে একটা বড় গোমস্তা পুকুর আছে। ওটা আগে ঘোষপাড়ার বদ্যিনাথ গোমস্তা, পূর্ণ গোমস্তাদের দখলে ছিল। পরে ওঁদের পরিবার বড় হতে থাকায় শরিকদের সংখ্যাও দিনকে দিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল। তাঁদের নানা মুনির নানা মত। তাঁদের রেষারেষির ফলে ওই পুকুরে মাছ চাষ বন্ধ হয়ে গেল। বহু দিন ধরে এমনিই পড়ে ছিল। তার পর ওঁদের অনুমতি নিয়ে এক-একটা গ্রাম পালা করে ওই পুকুরে ভাগে মাছ চাষ করতে শুরু করল। এখন বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা ক্লাবের ছেলেরাই চাষ করি। সেই মাছ বিক্রির টাকা দিয়েই তো ওই ক্লাব ঘরটা বানিয়েছি।
জয়া দেবী ভ্রু কোঁচকালেন। আগে যে গ্রামগুলো পালা করে ভাগে মাছ চাষ করত, তারা বাধা দেয়নি!
– কে বাধা দেবে? সব গ্রামের লোকেরা মিলেই তো ওই ক্লাবটা বানিয়েছি।
– ও, আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা, এখানে রাজনৈতিক নেতারা কেউ আসেন না?
তিনি বললেন, এক সময় মার্ক্সবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা রাম চ্যাটার্জি খুব আসতেন। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ভাইপো জয় চ্যাটার্জিও আসতেন। তবে এখন উনি আর আসেন না।
– কেন?
– কারণ, এখানে এখন সবাই একচেটিয়া তৃণমূল।
– এখানে তো দেখছি আশপাশে কোনও হাসপাতাল-টাতাল নেই। আপনারা কোনও চেষ্টাচরিত্র করেননি?
তিনি বললেন, করে কোনও লাভ নেই। কারণ, ওরা তো জানে এখানে ওদের বিরোধী দলের লোকেরা থাকে। সি পি এমকে কেউ একটাও ভোট দেয় না। তাই আমরা হাজার চেষ্টা করলেও ওরা আমাদের কথায় গা করবে না।
– তা হলে অসুখ-বিসুখ হলে কোথায় যান?
– ছোটখাটো রোগ-বালাই হলে কেউ আর হাসপাতাল-মুখো হই না। আমাদের এই গ্রামেই একজন ওঝা আছেন। তাঁর নাম সূর্যকান্ত মৈত্রী। তাঁর কাছে গেলে উনিই ঝাড়-ফুঁক করে দেন। জলপড়া দিয়ে দেন। ব্যস, তাতেই সেরে যায়।
জয়া দেবী বললেন, আর তাতেও যদি না সারে?
– তখন সোজা আঁধারগ্রাম হাসপাতালে।
– সেখানে সব রকম চিকিৎসা হয়?
– হয়, তবে তেমন গুরুতর কিছু হলে আমরা কলকাতায় নিয়ে যাই। এখান থেকে তো খুব একটা বেশি দূরে নয়।
– সে নয় হল… কিন্তু মাঝরাতে আচমকা যদি কারও প্রসব-বেদনা ওঠে, তখন কী হবে?
তিনি বললেন, বাচ্চা হওয়ার জন্য আমাদের গ্রামের মেয়ে-বউরা কেউ হাসপাতালে যায় না।
অবাক হয়ে গেলেন জয়া দেবী। বললেন, তা হলে?
তিনি ফের বললেন, এখানকারই এক খেতমজুরের বউ আছেন। ভারতী দাস। তিনিই ধাইমার কাজ করেন।
– তাই? তিনি কি প্রশিক্ষিত? মানে তার জন্য কি তিনি কোনও ট্রেনিং-ফেনিং নিয়েছেন?
– তা জানি না। তবে মনে হয়… না।
– তা হলে? যদি কোনও অঘটন ঘটে?
তিনি বললেন, এখনও পর্যন্ত তো কোনও অঘটন ঘটেনি। আর এত দিনেও যখন কোনও অঘটন ঘটেনি, আমার মনে হয় না, আর কিছু ঘটবে। তবে শুনেছি, কারও কোনও সমস্যা থাকলে, উনি নাকি সেটা আগে থেকেই বুঝতে পারেন। ফলে তাঁর বাড়ির লোকদের তিনি আগাম বলে দেন আঁধারগ্রাম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা। বহু দিন ধরে করছেন তো! অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। একেবারে ডাক্তারের বাবা। আমার দুটো বাচ্চা তো ওঁর হাতেই হয়েছে।
– তাই? তা, উনি কত করে নেন?
– কী? টাকা?
– হ্যাঁ।
– না না, ভারতী কোনও টাকা-পয়সা নেন না।
– টাকা নেন না! নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন জয়া। এত অভাবের মধ্যে থেকেও টাকা নেন না! একেবারে তাজ্জব হয়ে গেলেন তিনি।
চলবে…