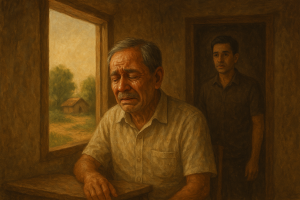মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর মুসলিম পদকর্তাদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটা উল্লেখ্য, সেটা হল যে, এঁরা কেউই ধর্মের দিক থেকে বৈষ্ণব ছিলেন না; এঁরা সকলেই বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন। এখানে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অতীতে যেসব বাঙালি গবেষক বৈষ্ণবপদাবলী নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এসব কবিদের জন্য এই বিশেষ শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছিলেন। এবিষয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বৈষ্ণবপদাবলীতে তিনি মধ্যযুগের বাংলার মোট ১০২ জন মুসলিম পদকর্তার পদ আবিষ্কার করেছিলেন, এবং পরবর্তীসময়ে এই পদগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার সময়ে নিজের এই গবেষণাগ্রন্থটির নাম ‘বাংলার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি’ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর পরবর্তীসময়ের কোন কোন সমালোচক অবশ্য এই গবেষণাগ্রন্থে সংকলিত পদগুলি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করে মধ্যযুগের এসব মুসলিম পদকর্তাদের খাঁটি বৈষ্ণব বলবার পক্ষেই নিজেদের রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ও গবেষকরা আবার তাঁদের এই মতের বিপক্ষে গিয়ে স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন যে, তাঁদের এই ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। কারণ, এমনতর ধারণার পরিপোষকতার কোন সঠিক প্রমাণ এখনো পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে ঐতিহাসিকদের মত হল যে, আসলে প্রবল যুগ-ধর্মের প্রভাবেই বৈষ্ণবপদাবলীতে তখন এই আপাতঃ বিরুদ্ধ কাজটি সম্ভব হয়েছিল। মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস বলে যে, বাংলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই এই যুগধর্মের প্রবর্তক ছিলেন। উদার মানবতার পটভূমিতে মহাপ্রভু তাঁর নিজের সমগ্র জীবনাচরণের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের বাংলায় ভক্তি ও প্রেমের যে বিপুল প্লাবন নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, সেটা তখন শুধু বাংলার হিন্দুদের ঘরের পাশ দিয়েই প্রবাহিত হয়নি, বরং বাঙালি মুসলমানদের বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়েও সমবেগে প্রবাহিত হয়েছিল। একারণেই মধ্যযুগের বাংলায় চৈতন্যমহাপ্রভুর বাপক প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে অতীতে বৈষ্ণবপদাবলীর এক সমালোচক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নিঃসঙ্কোচে বলেছিলেন—
“প্রাণ জাগিলেই গান জাগে। মধ্যযুগে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপ্ত করিয়া যেন একটা সংগীতের আসর বসিয়াছিল। ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া বাংলাদেশের সুরোন্মত্ত মানুষগুলি বিশ্বজীবনের মহাপ্রাঙ্গণ-তলে সেই সুর-সভায় আসিয়া মিলিত হইল। উপরে অনন্ত নীলাকাশ—নীলকৃষ্ণ; তাহার উপরে রাধা চন্দ্রাবলী—ভুল হইল, চৈতন্যচন্দ্রোদয় হইয়াছে। বাঙালীর ভাবের উচ্ছ্বাস, রসের উল্লাস, আনন্দের উৎসার বাধা মানে নাই। প্রাণ যে জাগিয়াছে—মহাপ্রাণ, মহাগান তো জাগিবেই।”
আর এই মহাসঙ্গীতের সুর-সভাতলে তখন কোন বাঙালির পক্ষেই বধির হয়ে বসে থাকা সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ, এসময়ে যাঁরা এই মহাসঙ্গীত শুনেও স্থির হয়ে বসে ছিলেন, তাঁরা হয় বধির ছিলেন, আর নয়ত কোন না কোনভাবে অসুস্থ ছিলেন। আর এজন্যই তৎকালীন বাংলার মুসলিম কবি এবং শ্রোতাদেরও পক্ষেও তখন এই সুর-সভাতল থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি; বরং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবল ব্যক্তিত্বে এবং যুগধর্মের অনতিক্রম্য প্রভাবে তাঁরাও তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই এই সভাতলে এসে যোগদান করেছিলেন। তবে শুধু যোগদান করা নয়, এসময়ে তাঁরা নিজেদের অন্তরের প্রেরণাবেগ দিয়ে বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন, এমনকি কীর্তনও গেয়ে উঠেছিলেন। একারণেই মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলীতে তখনকার নিষ্ঠাবান বহু বৈষ্ণবের কণ্ঠেই মুসলিম পদকর্তাদের পদ সংকীর্তিত হয়েছিল, এমনকি সেকালের বৈষ্ণবপদ সংকলিয়তাদের পক্ষেও এই পদকর্তাদের রচিত পদগুলি তখন এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।
কিন্তু এসব পদকর্তারা যে আদৌ বৈষ্ণব ছিলেন না, এবিষয়ে ইতিহাসে আরো বড় যে প্রমাণটি পাওয়া যায়, সেটা হল যে, এরকম দু’-একটি বৈষ্ণবপদ রচনা করা ছাড়া এঁদের মধ্যে অধিকাংশ কবিরাই কিন্তু আজীবন মুসলিম-সংস্কৃতি নিয়ে নিজেদের চর্চা চালিয়ে গিয়েছিলেন, এবং এমনকি এবিষয়ে বিশালায়তন কাব্যও লিখেছিলেন। সুতরাং ইতিহাসচর্চার সুস্থ মন নিয়ে বিবেচনা করলে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের রচিত এসব বিপুলায়তন কাব্যের মধ্যে কবির মানসভঙ্গির যে প্রতিফলন ঘটেছিল, সেটাই সত্যি ছিল। আর তাঁদের রচিত সামান্য দু’-একটি পদে—সেসব পদ যত তন্ময়তাপূর্ণই হোক না কেন, তাঁদের কবি-মানসিকতার যে ছায়াপাত ঘটেছিল, সেটা তীব্র ছিল।
তাই অতীতে যাঁরা মধ্যযুগের বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর মুসলিম পদকর্তাদের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলে প্রচার করেছিলেন, তাঁদের মত যেমন ভ্রান্ত ছিল; ঠিক তেমনি যাঁরা জানিয়েছিলেন যে, তৎকালীন বৈষ্ণবধর্মের কোন কিছুতে আকৃষ্ট না হয়ে এসব মুসলিম পদকর্তাদের পদগুলি ‘বৃন্তহীন পুষ্পসম’ নিজে নিজেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল—তাঁরাও এহেন মন্তব্যের মাধ্যমে নিজেদের একদেশদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীতার কোন কিছুতেই আকৃষ্ট না হয়ে এই স্বতোৎসারিত পদগুলি রচনা করা যে তখন কারো পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, একথা কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। আসলে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ না করলেও এসব পদকর্তারা যে তখন বৈষ্ণবীয়তায় প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ইতিহাসের দিক থেকে এই কথাটাই ধ্রুব সত্য। ইতিহাস বলে যে, বাস্তবে এসব পদকর্তারা যেমন বৈষ্ণব ছিলেন না, ঠিক তেমনি আবার অবৈষ্ণবও ছিলেন না; বরং তাঁরা বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন। সেযুগের বাংলার আকাশে বাতাশে যে উদার প্রেমের মন্ত্র-গুঞ্জরণ ধ্বনিত হ’য়েছিল, সেই গুঞ্জরণে এসব বাঙালি কবিও তখন নিজেদের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলেন বলেই তাঁদের রচিত পদগুলিতে যুগধর্মের সার্থক প্রতিফলন ঘটতে পেরেছিল।
এবারে এখানে এতক্ষণ ধরে যে যুগধর্মের কথা বলা হল, সেই যুগধর্ম, অর্থাৎ—ভিন্ন ধর্মের এসব পদকর্তাদের উপরে চৈতন্য-সংস্কৃতি এবং চৈতন্য-প্রভাব কতটা পড়েছিল, সমকালীন ইতিহাস থেকে সেটা বিশ্লেষণ করে এখানে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের আদিলীলার ১৩’শ পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়—
“কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন।
রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥”
এখানে এই নগরে নগরে ভ্রমণ করে কীর্তন করবার মাধ্যমেই মহাপ্রভুর জীবনাচরিতে প্রেমধর্মের অভিব্যক্তি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইতিহাসও বলে যে, এই কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি তখনকার জনসাধারণকে সবথেকে বেশি আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। একারণেই অতীতে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলেছিলেন—
“চৈতন্য-জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যায়, পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নিকট তর্কে পরাজিত হইয়া অথবা তাঁহার অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ, যাঁহারা পাণ্ডিত্যের ধার ধারে না, যাঁহারা পণ্ডিত চৈতন্যকে বুঝিবার মত পাণ্ডিত্যের অধিকারী নহে, তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিল তাঁহার কীর্তনে ও নর্তনে। যাঁহারা কীর্তনরত শ্রীচৈতন্যের প্রস্ফুট কদম্বপুষ্পতুল্য প্রেম-রোমাঞ্চিত কলেবর ও শিশির সজল পদ্ম-কোরক-সদৃশ প্রেমাশ্রুপূর্ণ অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়ন একবার দেখিয়াছে, তাঁহারাই ভুলিয়াছে।”
সুতরাং এথেকে বোঝা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের এই কীর্তনগান এবং অর্ধনিমীলিত নয়নে তখন সরল পল্লীবাসী ও পথের কর্ম-ক্লান্ত পথিকদের সঙ্গে একেশ্বরবাদী মুসলিমরাও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেননা এই চৈতন্যদেব শুধু বৈষ্ণবধর্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না, এই চৈতন্যদেব তখন জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই মহাপ্রভু—সকলের মহাপ্রভু বলে গণ্য হয়েছিলেন। সেযুগের বাংলার সব জাতি-ধর্ম ও বিভেদ-গ্লানির ঊর্ধ্বে তাঁর উদার প্রেমের মূর্ত-বিগ্রহর অবস্থান ছিল। কারণেই বুদ্ধিমন্ত খান শুধু চৈতন্যের প্রতি আকৃষ্টই হননি, বরং তিনি চৈতন্যের সেবক প্রধানও হয়ে পড়েছিলেন। এবিষয়ে ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের আদিলীলার ১০’ম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—
“শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমান্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিহো সেবকপ্রধান॥”
শুধু এই গ্রন্থে নয়, বুদ্ধিমন্ত খানের অনুরূপ চৈতন্য-নিষ্ঠার পরিচয় বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের অন্তঃলীলার ৯’ম পরিচ্ছেদেও এভাবে পাওয়া যায়—
“চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্মচৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥”
তাছাড়া ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ এবং ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের বর্ণনা থেকে একথাও জানা যায় যে, সেসময়ে বহু কাজী, এমনকি স্বয়ং সুলতান হুসেন শাহও পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের কীর্তন শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। অনুরূপভাবেই বৈষ্ণবপদাবলীর মুসলিম পদকর্তারাও তখন চৈতন্যের কীর্তনে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই, তাঁদের রচিত গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে চৈতন্যদেবের এই আবেশ-বিহ্বল মূর্তির সুনিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। গবেষকদের মতে, সেকালের এসব বৈষ্ণব মহাজনদের গৌরচন্দ্রিকার পদগুলিতে যে ঐকান্তিকতা ফুটে উঠেছে বলে দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের রচিত পদগুলিতেও সমকক্ষ ঐকান্তিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এমনকি এসব পদগুলি পড়তে পড়তে একসময়ে একথাও মনে হয় যে, গৌরচন্দ্রিকার পদরচনায় এসব কবিদের মানস-চক্ষে গৌরাঙ্গদেবের গৌরমূর্তি তখন স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছিল। একথার উদাহরণস্বরূপ এখানে সাহা আকবরের একটি পদের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটিতে তাঁর গৌর-নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার পরিচয় নিবিড়ভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। পদটি নিম্নরূপ—
“জীউ জীউ মেরে মন চোর গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
খির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥”
এখানে স্পষ্টভাবেই দেখতে পাওয়া যায় যে, এই কবি চৈতন্য-বিষয়ে তাঁর মুগ্ধ মনের সমুদয় ঐকান্তিকতাটুকু যেন উজাড় করে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ তাঁর এই বাণী বন্ধনের ভিতর দিয়ে পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে আবেশ বিহ্বল মূর্তিতে স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব যেন স্পষ্টভাবেই ধরা দেন।
অনুরূপভাবে লাল মামুদের রচিত একটি পদে সোনার মানুষ গৌরাঙ্গদেবের রূপ-মূর্তি আর সোনার মানুষের পরশে কত লোহার মানুষের সোনা হওয়ার কথা—পাপীর পুণ্যাত্মায় পরিণত হওয়ার ইতিহাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। পদটি এরকম—
“সোনার মানুষ নদে এল রে!
ভক্তসঙ্গে প্রেমতরঙ্গে ভাসিছে শ্রীবাসের ঘরে॥
…
সোনার মানুষ, সোনার বরণ, সোনার নুপুর, সোনার চরণ।
চারিদিকে সোনার কিরণ ছুটছে আলোকিত করে।
কত লোহার মানুষ সোনা হ’ল গৌর অবতার॥”
ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, শ্রীচৈতন্যর জীবনই ছিল তাঁর বাণী। আর নিজের আজীবন আচরণের মাধ্যমেই তিনি তাঁর বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তাই তখন যে নতুন ভাব-বন্যায়—‘শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়’—এই নতুন ভাবই তাঁর আচরণের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। আর মহাপ্রভুর—‘এই আপনি মেতে জগৎ মাতানোর’ কথাই সেযুগের ভাবদ্রষ্টা কবি লালনের পদে অপূর্ব চিত্রগরিমায় বিকশিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, এই একটি মাত্র পদেই যেন মহাপ্রভুর রূপ এবং সমগ্র জীবনাচরণের মর্ম-নির্যাসটুকু বিধৃত হয়েছে বলে দেখতে পাওয়া যায় —
“আর দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপীন ধরা॥”
এভাবে নিজের পদে এপর্যন্ত এই কবি গৌরাঙ্গের বাহ্য-প্রকৃতিকে তুলে ধরবার পরে মহাপ্রভুর জীবন-কণার মূল সুরে, মানব-প্রেমের মধ্যে, আপনি মেতে জগৎকে মাতিয়ে তোলবার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—
“গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা হ’য়েছে কি ধন হারা॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপিন পরেছে।
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে॥”
উপরোক্ত পদে—‘জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা হ’য়েছে কি ধন হারা’—পংক্তিটির মধ্যে দিয়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবেগ-বিহ্বল মূর্তির কথাই মনে পড়ে যায়। তবে এই পদের কবি এমনতর চিত্রাঙ্কনের মধ্যে না থেমে এরপরে আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন, এবং গৌরাঙ্গদেব যে স্বয়ং একটা যুগের স্রষ্টা, একথা এই ভাবুক কবি উপলব্ধি করতে পেরে এরপরে লিখেছিলেন—
“সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়।
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায়॥”
গবেষকদের মতে, মধ্যযুগের একজন বাঙালি মুসলিম কবির এই সামান্য পংক্তির মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র গৌরাঙ্গদেবের স্বরূপটি নয়, বরং সেকালের চৈতন্য-প্রভাবিত বাংলা ও সাহিত্যের সমগ্র ছবিটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলেই দেখতে পাওয়া যায়।
সমকালীন ইতিহাস বলে যে, তখনকার অনেক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্র উপায় নন, বরং উপেয়, এবং উপাসক নন, বরং উপাস্য ছিলেন। আরো ভালো করে বললে, তাঁদের কাছে শ্রীচৈতন্য তাঁদের কাছে কোন সাধারণ মানুষ নন, বরং রীতিমত দেবতা ছিলেন। আর একারণেই সেযুগের বাংলার মুসলিম পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই চৈতন্যদেবকে দেবতার আসনে বসিয়ে নিজেদের উপেয় রূপেও কল্পনা করেছিলেন। এমনকি শ্রীচৈতন্যকে নিজেদের আরাধ্য দেবতার আসনে বসিয়ে তাঁর পদে জীবনোৎসর্গের আকুতি জানিয়ে তাঁরা বলেছিলেন—
“গৌরচান্দ আমার।
তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥”
ছৈয়দ আলির রচিত একটি বৈষ্ণবপদে গৌরাঙ্গ এভাবেই তাঁর আরাধ্য দেবতার নামান্তর হয়ে গিয়েছিলেন বলে দেখা যায়—
“গৌর-আজ্ঞায় বিচারিলে পাইবার তার দরশন।
এই তনে ছাপিয়া রইছে সেই রতন॥”
‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে গৌরাঙ্গদেবকে রাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপ বলা হয়েছে। এই গ্রন্থমতে কৃষ্ণই হলেন শ্রীচৈতন্য, এবং তাঁদের একে অপরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত ছিল যে, রাধা-লীলাস্বাদন, এবং নিজের প্রেম-মাধুর্য উপলব্ধি করবার জন্যই দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর বিপুলায়তন এই গ্রন্থে নিজের এই কথাটিই বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। আর সেকালের মুসলিম পদকর্তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর এই সুরে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন—গরিব খাঁ তাঁর রচিত একটি পদে, শ্রীচৈতন্যই যে আসলে রাই-কানুর সমন্বিত রূপ, একথা সুন্দর ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন—
“শরমে শরম পোলায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু
যেমন দুধে জলে ম্যালায় গেল॥”
সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা এবং উদ্ধৃত পদসমূহ থেকে স্পষ্টভাবেই একথা উপলব্ধি করতে পারা যায় যে, মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম কবিদের বৈষ্ণবপদ রচনায় অবতীর্ণ হওয়ার মূলে শ্রীচৈতন্যের একটা ব্যাপক এবং গভীর প্রভাব অবশ্যই ছিল। বস্তুতঃ তখনকার মুসলমান কবিরা শুধু নন, তৎকালীন বাংলায় শ্রীচৈতন্যের প্রেম-বন্যা প্রবাহিত না হলে সমকালীন হিন্দু কবিরাও রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক পদরচনায় কতটুকু এগিয়ে যেতে পারতেন, এবং এবিষয়ে সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন, তা নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। ইতিহাস বলে যে, বর্তমানে বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম বলতে যা বোঝানো হয়, সেটা আসলে শ্রীচৈতন্যেরই দান ছিল। শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই তখন বৈষ্ণবধর্মে নবযৌবনের সঞ্চার ঘটেছিল। পরবর্তীসময়ে জয়দেব-বড়ুচণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রীচৈতন্যের দ্বারাই নতুন মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এমনকি জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, রায়শেখর প্রমুখ সব বৈষ্ণব মহাজনই আসলে শ্রীচৈতন্যদেবেরই সৃষ্টি ছিলেন। ঠিক একইরকমভাবে মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম পদকর্তারাও তখন চৈতন্যের জীবন থেকে বেগ নিয়ে বৈষ্ণবকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, এবং চৈতন্যই তাঁদের এই কাব্য-প্রেরণার উৎসভূমি ছিলেন।#