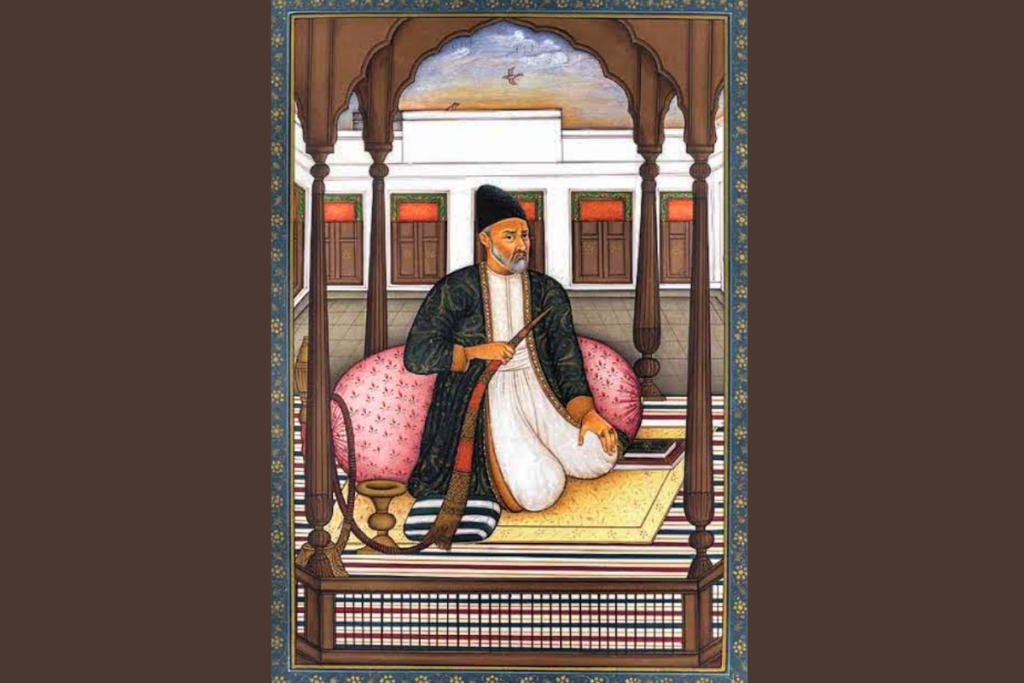মির্জা গালিবের জীবদ্দশায় ১৮৫৭ সালের মে মাসে ভারতের ইতিহাসের সেই ঘটনাটি ঘটেছিল, যেটাকে বৃটিশদের ভাষায় ‘সিপাহী বিদ্রোহ’ বলা হয়ে থাকে, এবং কিছু দেশীয় মানুষ যেটিকে পরাধীন ভারতের ‘প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ’ নামে অভিহিত করে থাকেন। বর্তমানে ভারতের ইতিহাসের সাথে পরিচিত প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন যে, এই ঐতিহাসিক ঘটনার ফলে তখন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে তৈমুর-চেঙ্গিস রাজবংশের নাম চিরকালের মত অপসৃত হয়ে গিয়েছিল এবং ভারত-ভূমি পুনরায় আরেকটি বিদেশী শক্তির পদানত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, গালিবও তখনকার এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সংকটকে এড়াতে পারেন নি। অনেকের মতে, ইংরেজদের রাজনৈতিক দমন-নীতি ও অত্যাচারই এই বিপ্লবের মূল কারণ ছিল। এই কাণ্ড দীর্ঘদিন আগে শুরু হয়েছিল, মূলতঃ যখন থেকে এদেশে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ইংরেজেরা দেশ-শাসনের ব্যাপারে নিজেদের নাক গলাতে শুরু করেছিলেন। ইতিহাস বলে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মানুষের সঙ্গে ইংরাজেরাও বণিকরূপে এদেশে পদার্পন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় সনদের বলে ইংল্যাণ্ডে তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এরপরে প্রথমে দিল্লী ও পরে আগ্রায় যতদিন কেন্দ্রীয় মুঘল শাসন শক্তিশালী ও সক্রিয় ছিল, ততদিন পর্যন্ত এই কোম্পানি অধ্যবসায়ের সঙ্গে এদেশে বাণিজ্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেই দিল্লীর সরকারের প্রভাব দেশের দূরপ্রান্তস্থিত স্থানগুলির উপরে শিথিল হয়ে পড়বার জন্য সমগ্র দেশে অস্থিরতা ও অন্তর্দ্বন্দ দেখা দিয়েছিল। আর থেকেই এই অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে এদেশে তাঁদের শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা শুরু করেছিল, এবং এই উদ্দেশ্যে এদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে তাঁরা তখন থেকেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে নেমে পড়েছিল। মূলতঃ ওই সময় থেকেই নিজেদের কুঠী-শহরগুলি সুরক্ষিত করে নিয়ে তাঁরা নিজস্ব বেতনভুক সৈন্যবাহিনী রাখতে আরম্ভ করেছিল। শুধু সেটাই নয়, উচ্চাভিলাষী স্থানীয় শাসকদের ক্ষমতার লড়াইয়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের দুটি বণিক সংস্থা তখন থেকেই নিজেদের পছন্দমত শাসকদের পক্ষ নিয়ে একে ওপরের বিরুদ্ধে লড়াইতে অবতীর্ন হয়েছিল। এতে তাঁদের নিজেদের মনোনীত ব্যক্তির জয়লাভ ঘটলে তাঁদের একপক্ষের নিজেদেরও শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি ঘটত। শেষপর্যন্ত বোঝা গিয়েছিল যে, এই লড়াইয়ের শেষ পরিণাম ইংল্যাণ্ড অথবা ফ্রান্সের এদেশে প্রভাব ও শক্তিবৃদ্ধি হবে। অন্যদিকে দেশে বহুদিন ধরে শান্তি ও সমৃদ্ধির স্রোত প্রবাহিত থাকবার পরে হঠাৎই তখন থেকে দেশের শাসন ও সামাজিক ব্যবস্থার বেশ অবনতি ঘটতে শুরু করেছিল। অঙ্গরাজ্যগুলি তখন তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়ছিল, এবং সে জায়গায় রাতারাতি নতুন নতুন রাজ্য গজিয়ে উঠছিল। এই অবস্থাটা স্বভাবতঃই তখন যে কোন ভাগ্যান্বেষীর পক্ষে অনুকূল ছিল। এভাবে অনেক বছর ধরে বৃটেন ও ফ্রান্স এদেশে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করবার জন্য প্রতিদ্বন্দিতা চালিয়ে যাওয়ার পরে শেষপর্যন্ত এই দ্বন্দ্বে বৃটিশদেরই জয়লাভ ঘটেছিল, এবং ভারতের বিস্তৃত ভূখণ্ডে তাঁদেরই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অন্যদিকে ফরাসিরা ধীরে ধীরে তাঁদের অধিকার হারিয়ে শেষপর্যন্ত ক্ষমতার দ্বন্দ থেকে পিছু হঠে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরপরে নিজের শক্তিতেই হোক অথবা নিজেদের বংশবদদের সাহায্যেই হোক, বৃটিশ শক্তি ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তাঁরা অধ্যবসায় সহকারে সমগ্র দেশকে নিজেদের কুক্ষিগত করবার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ তখন যেসব ভারতীয় শাসক বা রাজাকে তাঁরা অধিকারচ্যুত করেছিলেন, তাঁরা বৃটিশদের উপরে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু একটা সুসম্বদ্ধ প্রতিরোধের সুযোগ না থাকবার জন্য এই বিদ্বেষের আগুন তখন শুধু ধিকি ধিকিভাবে জ্বলেছিল, বাইরে থেকে এটা কোনভাবেই প্রকাশ পায় নি। শুধু একটা উপযুক্ত ক্ষণে বিস্ফোরণের অপেক্ষা ছিল। অবশেষে নতুন বন্দুকের কার্টিজ বা গুলিকে কেন্দ্র করে সেই উপযুক্ত ক্ষণটি উপস্থিত হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের প্রাথমিক কারণ সম্পর্কে বর্তমানে প্রায় সকলেই অবগত রয়েছেন বলে, এখানে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এছাড়া ইতিহাস একথাও বলে যে, বৃটিশরা এদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু ও মুসলমান ভারতীয়দের মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রচার করবার নীতিও নিয়েছিল। বৃটিশদের এই প্রচেষ্টার পরিচয় ইতিপূর্বেই তখন পাওয়া গিয়েছিল, যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদের মেয়াদ ১৮৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের গভর্নমেন্ট এই যুক্তিতে বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, এরফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে সহায়তা হবে। এরপরে বৃটিশ সরকার এদেশের নানা জায়গায় যেসব স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিল, খৃষ্টধর্মের বিষয়গুলি যেখানে আবশ্যিক পাঠ্য করা হয়েছিল। তখন খোদ দিল্লী শহরেই পুরোনো দিল্লী কলেজের যেক’জন ছাত্র প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র ও ডাঃ চমনলালের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যদিও ভারতের জনসাধারণ আগে থেকেই ইংরেজ মিশনরিদের উদ্দেশ্য ও কাজকর্মকে সন্দেহের চোখে দেখত, কিন্তু তবুও এই ঘটনার পর এদেশীয়দের মধ্যে কারো মনে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকেনি যে, এদেশের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করে তাঁদের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করাই হল পাশ্চাত্যদেশীয় শাসকদের আসল উদ্দেশ্য। যাই হোক, এরকম একাধিক ঘটনার ফলস্বরূপ অবশেষে ১৮৫৭ সালে ভারতে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা ঘটেছিল, সেই বছরেরই ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে বৃটিশ কর্তৃক বিদ্রোহীদের হাত থেকে দিল্লী পুনরুদ্ধার হওয়ার পরেও এর শেষ হয়নি। কারণ, এরপরেও দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল প্রতিশোধমূলক দমন-নীতির পালা চলেছিল, হাজার হাজার নাগরিককে নামমাত্র বিচারের পরে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-দৌলত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল; এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ফাঁসির বিনিময়ে অভিযুক্তদের কাছ থেকে অসম্ভব রকমের ক্ষতিপূরণও আদায় করা হয়েছিল। এছাড়া বহু সংখ্যক ব্যক্তি তখন দিল্লী শহর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতেও বাধ্য হয়েছিলেন ও দীর্ঘকাল ধরে কঠোর দারিদ্র্য ও কষ্টের সঙ্গে অন্যত্র আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেক পরে অবস্থার উন্নতি হওয়ার পরে তবে তাঁরা নিজের নিজের বাড়িতে ফিরতে পেরেছিলেন।
এই বিপ্লবের সময়ে গালিব কিন্তু দিল্লীতেই অবস্থান করেছিলেন, তিনি তখন শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যান নি। আসল কথা হল যে, তাঁর তখন অন্য কোথাও যাওয়ার মত কোন আশ্রয়ও ছিল না। এই সময়টি তাঁর খুব কষ্টেই কেটেছিল। এর আগে অনেকদিন ধরেই তাঁর আয়ের মাত্র দুটি সূত্র ছিল; সেগুলোর মধ্যে একটি হল বৃটিশদের খাজানা থেকে প্রাপ্ত বার্ষিক ৭৫০ টাকা, আট দ্বিতীয়টি ছিল মুঘল রাজবংশের ইতিহাস-লেখকরূপে বাহাদুর শাহের কাছ থেকে বার্ষিক পাওনা ৬০০ টাকা। কিন্তু বিদ্রোহীরা দিল্লীতে পৌঁছানোর পরেই যেহেতু তখন শহরের বৃটিশ শক্তি বা শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল, এবং সেখানে বৃটিশ শাসনের কোন ঘাঁটি আর অবশিষ্ট ছিল না, কাজেই গালিবের পক্ষেও তখন কোন পেনসন প্রাপ্তি সম্ভব হয়নি। আর বাহাদুর শাহের নিজস্ব ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন দামই তখন ছিল না, বরং ওই সময়ে তিনি সম্পূর্ণভাবে অন্যদের হাতের খেলার পুতুল হয়ে পড়েছিলেন; তাছাড়া তখন তাঁর নিজেরও যেহেতু অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল, সেহেতু গালিব বা অন্য কারো পাওনা মেটানোর সামর্থ্য ওই সময়ে তাঁর আর ছিল না। এরফলে তখন স্বাভাবিক কারণেই গালিবকে খুব কষ্টের মধ্যেই নিজের দিনাতিপাত করতে হয়েছিল। অবশেষে দিল্লী বৃটিশদের অধিকারে ফিরে আসবার পরে যখন দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল, তখন গালিব ভেবেছিলেন যে, তাঁরও আগেকার অবস্থা ফিরে আসবে এবং তাঁর পারিবারিক পেনসনের টাকা আগের মতোই বৃটিশদের কোষাগার থেকে পাওয়া যাবে। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, গালিবের এই আশায় ছাই পড়েছিল।
গালিব বেশ দূরদর্শী ছিলেন এবং তাঁর সাংসারিক বুদ্ধিও বেশ প্রখর ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে দিল্লীতে যখন প্রথম গোলমাল শুরু হয়েছিল, তখন কিন্তু কেউ-ই বুঝতে পারেন নি যে পরবর্তী সময়ে এই হাওয়া কোনদিকে বইবে। কিন্তু গালিব প্রথম থেকেই বৃটিশ-বিরোধী সমস্ত রকমের কাজকর্ম থেকে নিজেকে যথাসম্ভব নির্লিপ্ত রেখেছিলেন। তবে লালকেল্লা বা বাহাদুর শাহের দরবার যেহেতু তখন বৃটিশ-বিরোধী কাজকর্মের মূল কেন্দ্র ছিল, তাই গালিবের পক্ষে এই দরবারের সংস্রব সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা অবশ্য সম্ভব হয় নি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, ১৮৫৪ সালে বাদশাহের সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা মোহাম্মদ ইব্রাহিম জৌকের মৃত্যুর পরে গালিব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তবে এর আগে থেকেই তিনি যেহেতু দিল্লী দরবারের সরকারি ইতিহাস-লেখক ছিলেন, এরপরে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে তিনি বাদশাহের সাহিত্য-বিষয়ক পরামর্শদাতা হওয়ায় তখন প্রায় নিয়মিতভাবেই তাঁকে বাদশাহের কাছে যাওয়া-আসা করতে হত। ফলে ওই সময়ে দিল্লীতে এমন কোন ইংরেজ রাজকর্মচারী ছিলেন না, যাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারত। তাই ওই অবস্থায় গালিব ভেবেছিলেন যে, শাহী দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেও প্রকাশ্যে কোন পক্ষে যোগ না দেওয়াটাই বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে। কিন্তু তাঁর এই সতর্কতা সত্ত্বেও ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয় নি, বরং তাঁর বিপদ ঘটেছিল।
ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হওয়ার পরও ইংরেজরা দিল্লী শহরে ও লাল কেল্লার ভেতরে কি ঘটছে, সেকথা জানবার জন্য একটি সক্রিয় গুপ্তচর-চক্রের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এই গুপ্তচর-চক্র তখন বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য—সবধরণের সংবাদই সংগ্রহ করে সেগুলোকে বৃটিশ বাহিনীর সৈন্যাধক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিত। দিল্লীর কাশ্মীরী গেটের বাইরে অবস্থিত উচ্চভূমির উপরে তখন এই সেনাধ্যক্ষের আস্তানা ছিল। একদিন একজন গুপ্তচর মারফৎ সেখানে সংবাদ পৌঁছেছিল যে, বাহাদুর শাহ-আমন্ত্রিত একটি দরবারে গালিবও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি একটি ‘সিক্কা’ রচনা করে বাদশাহকে উপহার দিয়েছেন; বাহাদুর শাহ যে নূতন মুদ্রা প্রবর্তন করতে চলেছেন সেটার উপরে উৎকীর্ণ হওয়ার জন্যই এই সিক্কাটি রচিত হয়েছে। আসলে ঘটনাটি বিকৃত করে পরিবেশন করা হয়েছিল। কারণ, তখন যে সিক্কাটি গালিব-রচিত বলে রটনা করা হয়েছিল, সেটি আদৌ গালিব লেখেন নি। সেটি আসলে সেযুগের অল্প-খ্যাত একজন কবির রচনা ছিল, এবং শাহী দরবারে বাদশাহের সামনে পঠিত হওয়ার আগেই একটি স্থানীয় কাগজে সেটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিকৃত বা অসত্য হলেও এই খবরটি তখন ইংরেজদের দপ্তরে নথিভুক্ত হয়ে থেকে গিয়েছিল। এরপরে দিল্লী ইংরেজ-কর্তৃক পুনরধিকৃত হওয়ার পরে গালিব যখন দিল্লীর ইংরেজ চীফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে এই অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ চলবার সময়ে দিল্লীতে গালিব যেহেতু বৃটিশ-বিরোধী কোন কাজের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন না, সেই কারণে দিল্লী পুনরধিকৃত হওয়ার পরেও গালিবের জীবন বা সম্পত্তির নিরাপত্তা বজায় থেকে গিয়েছিল। আর সিক্কার ব্যাপারটাকেও ইংরেজরা তাঁর একটা কবিসুলভ দুর্বলতা বলেই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। স্মরণীয় যে, বিদ্রোহ দমন করবার সময়ে শুধুমাত্র সন্দেহ বশবর্তী হয়েই তখন ইংরেজরা বহু মানুষকে হত্যা বা কারারুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং এক্ষেত্রে গালিবের প্রতি ইংরেজরা যে বিশেষ দয়া দেখিয়েছিলেন, এটা খুবই সত্যি কথা। কিন্তু গালিবের বিরুদ্ধে তখন যে অভিযোগটি নথিবদ্ধ হয়েছিল, সেটার একমাত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে এরপরে ইংরেজদের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য পারিবারিক পেনসনটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া তাঁর অন্য যে ক্ষতিটা হয়েছিল, সেটা ছিল যে, এরপর থেকে গভর্নর জেনারেল বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দরবারে তাঁর নিমন্ত্রণও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যদিও গালিব ভেবেছিলেন যে, দিল্লীতে ইংরেজদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আগের অবস্থা সর্বতোভাবেই ফিরে আসবে, সেহেতু পেনসন ও দরবারে নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে যাওয়া তাঁর কাছে প্রত্যাশার অতীত ছিল; এবং এই ঘটনার ফলে তিনি তখন খুবই হতাশাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, ওই সময়ে তাঁর আগের অবস্থা ফিরে আসা তো দূরের কথা, এমনকি বর্তমান অবস্থারও বেশ অবনতি ঘটেছিল। তখন কিছু সংখ্যক বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তি তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে না আসলে হয়ত তাঁর পক্ষে এই অবস্থাটা আরও দুঃসহ হয়ে উঠত। তবে সৌভাগ্যক্রমে, রামপুরের তৎকালীন নবাব ইউসুফ আলি খান তাঁকে তখন এই দুরবস্থার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন।
১৮৫৫ সালে রামপুরের নবাব মোহাম্মদ সঈদখানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ইউসুফ আলি খান রামপুরের নবাবী গদিতে আসীন হয়েছিলেন। এই তরুণ যুবক সাহিত্য বিষয়ে বেশ পারদর্শী ছিলেন বলে অল্পবয়সেই তাঁর পিতা এঁকে শিক্ষালাভ করবার জন্য দিল্লীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের ছাত্রাবস্থায় তিনি যাঁদের কাছ থেকে ফারসি শিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে গালিব অন্যতম ছিলেন। তবে নবাবপুত্র রামপুরে ফিরে যাওয়ার পরে অবশ্য গালিবের সাথে তাঁর এই যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এরপরে ১৮৫৫ সালে তিনি নিজে যখন নবাব হয়েছিলেন, তখন গালিব আগের সেই ছিন্ন সংযোগ পুনঃস্থাপন করবার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। তবে তখন গালিবের এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি; কারণ, নবাব এতে কোন সাড়া দেন নি। আর তাই গালিব এরপরে নিজে থেকে এবিষয়ে আর কোনও চেষ্টা করেন নি। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়ার আগে থেকেই গালিবের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামপুরে থাকতেন। তাঁর নাম ছিল মৌলবী ফজল হক। তরুণ নবাবের উপরে তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। এই ফজল হকের পরামর্শে গালিব তখন একটি ‘কসীদা’ রচনা করে নবাবকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ফজল হক আশা করেছিলেন যে, এর দ্বারা গালিব ও তরুণ নবাবের মধ্যে ছিন্ন সংযোগ পুনঃস্থাপিত হবে, এবং এর ফলে গালিবের পক্ষে নবাবের কাছ থেকে একটা স্থায়ী পেনসন, অন্ততঃপক্ষে এককালীন মোটা রকমের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হবে। সৌভাগ্যক্রমে এবারে গালিবের কপাল খুলেছিল। কারণ, নবাব ইউসুফ আলী এই কসীদাটি পেয়ে শুধু খুশিই হন নি, তিনি এটাও ঠিক করেছিলেন যে, তিনি নিজে কাব্য রচনা করবার ব্যাপারে গালিবের ‘সাদে’ বা শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু গালিব ও নবাবের মধ্যে এই নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠবার কয়েক মাস পরই তখন দেশের রাজনৈতিক আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। তবে এই দুর্যোগের মধ্যেও গালিব ও নবাবের মধ্যে নিয়মিত পত্রব্যবহার চালু ছিল। এর আগে নবাবের কাছ থেকে মাঝে মাঝে গালিব কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য পেলেও বেতন হিসাবে কোন নিয়মিত কোন টাকা পান নি। অবশেষে দিল্লীতে ইংরেজদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে গালিব যখন দেখেছিলেন যে, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর আগের সম্পর্ক আর ফিরছে না এবং তাঁর পারিবারিক পেনসনও বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি রামপুরের নবাবকে তাঁর জন্য একটি স্থায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেছিলেন। এই বৃত্তি যে নিত্য আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে তাঁকে মুক্তি দিতে পারে, একথাও তখন নবাবকে জানানো হয়েছিল। এরপরে তাঁর এই আবেদন পেয়ে নবাব আদেশ দিয়েছিলেন যে, অতঃপর তাঁকে রামপুর কোষাগার থেকে মাসিক একশো টাকা বৃত্তি দেওয়া হবে।
সিপাহী-বিদ্রোহের উত্তাল তরঙ্গময় দিনগুলিতে গালিবকে ঘরের মধ্যে বসে নিজের সময় কাটাতে হয়েছিল। আর কর্মহীন এই দিনগুলি কাটানোর জন্যই সম্ভবতঃ তখন তিনি তাঁর চারপাশের দিল্লী শহরে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছিল, সেগুলি টিপ্পনী বা নোটের আকারে লিখে রাখবার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। এগুলো যে ঠিক নিয়মিত দিনলিপির আকারে লিখিত হয়েছিল—তা নয়, তবে সেই সময়ে সংঘটিত বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি এমনভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যতে এগুলি একটি বিশেষ যুগের বিস্তৃত বিবরণ লেখবার কাজে প্রয়োজনমত ব্যবহার করা যায়। বৃটিশ-শক্তি কর্তৃক দিল্লী বিজয়ের পরে গালিব এই টিপ্পনীগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে ফারসি ভাষায় ‘দস্তম্বু’ নামের একটি পুস্তিকা রচনা করেন। গালিবের দাবি ছিল যে, এতে ব্যক্তি ও স্থান-নামের ক্ষেত্রে ছাড়া তিনি কোন কিছুতেই আরবি ভাষার কোন শব্দ ব্যবহার করেন নি। কিন্তু গবেষকদের মতে গালিবের এই দাবি সর্বাংশে যথার্থ ছিল না। কারণ, যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি নিজের এই রচনায় কিছু আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ রুদ্ধ করতে পারেন নি। তবে আরবি শব্দের ব্যবহার রোধ করতে গিয়ে তিনি সেযুগের বহু প্রচলিত ও পরিচিত আরবি শব্দের পরিবর্তে ফারসি ভাষার এমনকিছু শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, যেগুলো তখন অপ্রচলিত ছিল। আর একারণেই তাঁর ‘দস্তম্বু’ পুস্তকটি মোটেই সুখপাঠ্য হয়নি, এবং এতে কিছু দুর্বোধ্যতাও থেকে গিয়েছিল। এমনকি সমসাময়িক কালের ইতিবৃত্তমূলক পুস্তক হিসাবেও এটি কোন নির্ভরযোগ্য রচনা হয় নি। আগেই বলা হয়েছে যে, সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে গালিব বাহাদুর শাহের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছিলেন, এবং কিছুটা বাধ্য হয়েই তখন তাঁকে এমনসব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়েছিল, যাঁরা আপাদমস্তক বৃটিশ-বিরোধী ছিলেন। তবে বৃটিশ-বিরোধী এমন কোন কাজে তিনি নিজে লিপ্ত হন নি, যার ফলে তাঁকে বৃটিশ-বিরোধী বলে চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও এরপরেও গালিবের মনে শঙ্কা থেকে গিয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি বৃটিশ-বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত না থাকলেও বৃটিশেরা তাঁকে সুনজরে দেখছেন না। অন্যদিকে তিনি এবিষয়ে নিঃসন্দেহে ছিলেন যে, মুঘল বাদশাহের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যের ব্যাপারটিকে সহজেই বৃটিশ-বিরোধিতা বলে ধরে নেওয়া হবে। কাজেই, এই পুস্তকটি সংকলন করবার সময়ে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন যে, এতে ভারতীয় সিপাহীদের দোষ-ত্রুটিগুলি যেন কোনমতেই ছোট করে না দেখা যায়, আর একইসাথে বৃটিশদের অত্যাচার ও নিপীড়নের ঘটনাগুলি এতে যেন প্রাধান্য না পায়। এছাড়া তিনি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলেন যে, এই বইটি ছাপিয়ে তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগী ইংরেজ রাজকর্মচারীদের উপহার দেবেন। এরফলে এঁদের অভিরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে গালিব এতে কিছু ঘটনার উল্লেখ যেমন এড়িয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি আবার কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকেও পূর্ণমাত্রায় রঙ চড়িয়ে উল্লেখ করেছিলেন। গবেষকদের মতে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে রচনার লক্ষ্য হয়, সেটা কখনও ইতিহাস হওয়ার যোগ্য হতে পারে না, এবং সেটা থেকে ইতিহাসের উপাদানও কোনমতেই আহরণযোগ্য হয় না। গালিব চেয়েছিলেন যে, এই বইটি বৃটিশদের কাছে তাঁকে নতুনভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এছাড়া এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি ইংরেজদের একথাও বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের দুঃসময়েও তিনি তাঁদের বন্ধুর মতোই কাজ করেছিলেন। যাই হোক, বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে গালিব এর কপি তৎকালীন ভারতে অবস্থিত বহু বিশিষ্ট ইংরেজ রাজকর্মচারীদের উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন; এমনকি ইংল্যাণ্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছেও তখন এই বইটি উপহারস্বরূপ প্রেরিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও এই বইটি কোন ইংরেজের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। আর তাই গালিব যে উদ্দেশ্যে এই বইটি রচনা করেছিলেন ও ইংরেজদের উপহার দিয়েছিলেন, সেটা ব্যর্থ হয়েছিল। গবেষকদের মতে, গালিবের এই বইয়ের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল এর ভাষা; এটি মোটেও সুবোধ্য ছিল না। আর তাই ইংরেজদের সঙ্গে একটা হৃদ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবার জন্য গালিবের এই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তখন সাফল্যলাভ করতে পারে নি।
ইতিমধ্যে, গালিবের বহু বন্ধু এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে, ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যাতে তাঁকে ক্ষমার চোখে দেখেন; তবে তাঁদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা খুবই অল্প ছিল। কারণ, গালিব যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নি, এটা তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে স্বীকার করানো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু এটা শুধুমাত্র রামপুরের নবাবের হস্তক্ষেপের ফলে সম্ভব হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১৮৬০ সালের মে মাসে ইংরেজ সরকার তাঁদের পূর্বতন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে গালিবের পারিবারিক পেনসন পুনরায় চালু করেছিল। এর ঠিক তিন বছর পরে, ১৮৬৩ সালের মার্চ মাসে গালিবকে আবার দরবারে যোগদান করবার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর এভাবেই এইভাবে ১৮৫৭ সালের মে মাসের আগে গালিব যেসব সুযোগ-সুবিধা ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পেতেন, সেগুলি পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছিল।
গালিব মূলতঃ একজন কবি ও লেখক ছিলেন। আর তাই আর্থিক দুরবস্থা ও সাংসারিক অশান্তি সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে সাহিত্যচর্চা থেকে বিরত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহ চলবার সময়ে তাঁকে মাঝে মাঝে লাল কেল্লায় যেতে হলেও অধিকাংশ সময়েই তিনি একা একাই বাড়িতে বসে থাকতেন। তিনি আজীবন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন। এছাড়া তাঁর স্মৃতিশক্তিও অসাধারণ ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের দিনগুলিতেও বই-ই তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিল। সেই বইগুলির মধ্যে একটি ছিল ‘বুরহন-এ-কাতি’, যেটি আসলে ফারসি ভাষার একটি বিখ্যাত শব্দ-কোষ ছিল। নিজের অবসর সময়ে গালিব এই বইটি উল্টেপাল্টে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। মুহম্মদ হুসেন তব্রীজী নামের একজন ব্যক্তি সেযুগের এই বিখ্যাত অভিধানটির সংকলক ছিলেন। তৎকালীন কলকাতা থেকে এটির একটি নতুন সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই বইটি উল্টেপাল্টে দেখতে দেখতে গালিবের চোখে এর বহু দোষত্রুটি ধরা পড়েছিল। গালিবের কাছে এই অভিধানের যে কপিটি ছিল, সেটার মার্জিনে এটার দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে তিনি নিজের মন্তব্য লিখে রাখতেন। ফলে দেখতে দেখতে তাঁর সেসব মন্তব্যগুলি সংখ্যায় বেশ স্ফীত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের পরে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবার পরে, গালিব তাঁর এই মন্তব্য বা নোটগুলিকে একথা ভেবে আলাদাভাবে নকল করিয়ে নিয়েছিলেন যে, এগুলি থেকে তাঁর বন্ধু এবং ছাত্রেরা উপকৃত হবেন, এবং এগুলি তাঁদের কাজে লাগবে। কিন্তু এগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রথমদিকে তাঁর ছিল না। কিন্তু শেষকালে, তাঁর কোন কোন বন্ধু তাঁকে এসব একটি পৃথক বইয়ের আকারে ছাপাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁদের যুক্তি ছিল যে, এই বইটি প্রকাশিত হলে সাধারণ পাঠকের বেশ কাজে লাগবে এবং একজন ফারসি-পণ্ডিত হিসেবেও গালিবের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, গালিব সেযুগের ভারতীয় ফারসি-লেখকদের কঠোর সমালোচক ছিলেন; তাঁর মত ছিল যে, ফারসি ভাষার বিষয়ে তাঁদের রচনা বা জ্ঞান মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ‘বুরহান-এ-কাতি’ গ্রন্থের সংকলনকর্তা ভারতেই জন্মেছিলেন ও এদেশেই তিনি নিজের শিক্ষা-লাভ করেছিলেন; তবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইরানবাসী ছিলেন। ভারতীয়েরা ফারসি ভাষায় সুদক্ষ নয়—গালিবের এই মতটি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যও যে তাঁর বইটি ছাপানো প্রয়োজন, গালিবের বন্ধুরা তখন তাঁকে একথা বুঝিয়েছিলেন। এরপরে গালিবের এই বইটি ‘কাতি’বুরহন’ নামে ১৮৬২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়েছিল। আসলে মানুষ কোন পরিবর্তনকেই সহজে মেনে নিতে চায় না। আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা শুধুমাত্র পূর্বপুরুষদের জীবনধারাই অনুসরণ করে চলেন; কারণ, তাঁরা কোন পরিবর্তন বা কোন কিছু নতুনকে ভয় পান। ‘বুরহন-এ-কাতি’ তখন দীর্ঘকাল ধরে ফারসি ভাষার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা পেয়ে আসছিল। সেযুগের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই গ্রন্থটিকে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্যরূপে অনুমোদন করতেন। সুতরাং গালিব কর্তৃক সেকালের এমন একটি পুস্তকের বিরূপ সমালোচনা ঔদ্ধত্য এমনকি অধর্মরূপেও তখন বিবেচিত হয়েছিল। আর তাই গালিবের বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় বইতে শুরু করেছিল। শুধু সেটাই নয়, তখন গালিবের মতের কড়া সমালোচনা করেও একের পর এক পুস্তক অথবা পুস্তিকা প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল। বলাই বাহুল্য যে, গালিব ও তাঁর বন্ধুরা এসব সমালোচনাকে নিঃশব্দে বরদাস্ত করতে পারেননি, এবং তাঁরাও তখন নিজেদের সাধ্যমত এসব আক্রমণের সমুচিত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এরপরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গালিবের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ মন্দীভূত হয়ে গেলেও একেবারে স্তব্ধ কিন্তু হয়ে যায় নি। বরং একটাসময়ে ঘটনা এমনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে মানহানিকর রচনা প্রকাশ করবার জন্য গালিবকে ক্ষতিপূরণ আদায় করবার উদ্দেশ্যে আদালতের শরণও নিতে হয়েছিল। আমিনুদ্দীন নামের সেযুগের একজন ‘খিস্তি’ লেখকের বিরুদ্ধে তখন এই অভিযোগ করা হয়েছিল। তবে গালিব অবশ্য এই ক্ষতিপূরণের মামলায় জিততে পারেন নি। কারণ, সেযুগের কয়েকজন নামকরা পণ্ডিত ব্যক্তি ওই লেখককে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে গালিবের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যবহৃত আপত্তিজনক শব্দগুলির উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা করে আদালতে একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, অপমানটা এমনকিছু গভীর নয় যে তাতে গালিবের মানহানি ঘটতে পারে। এরফলে গালিব শেষপর্যন্ত আদালত থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি আদালত তুলে নিয়ে এবিষয়ে একটা আপস-মীমাংসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।#