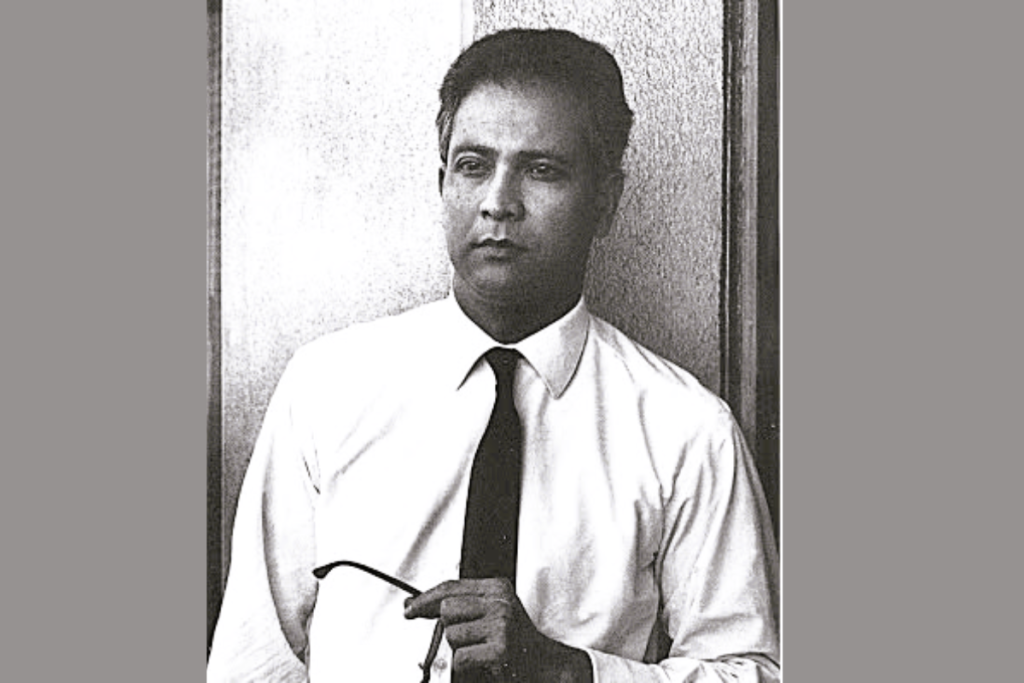।।দ্বিতীয় পর্ব।।
১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে-দেশ ভাগ হয়ে যায় সেই দেশের একটি নতুনাংশের নাগরিক ওয়ালীউল্লাহ্ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর উপন্যাসের জনপদ মহব্বতনগরের জনগণকে ফেলে দেন একটা সংশয়গ্রস্ততা ও সংকটের মধ্যে। যদিও উপন্যাসের ভেতরকার সময় আনুমানিক ১৯০০ সাল কিন্তু ১৯৪৮ সালেও সেই সংকটের সুরাহা হয় না। কাজেই ১৯০০ এবং ১৯৪৮- পারস্পরিক পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে দাঁড়ানো দু’টি কালস্তম্ভ হলেও বাস্তবে গ্রামটির জনগোষ্ঠি একই মুহূর্তে অবস্থান করে দুই কালের পাটাতনে। অর্থাৎ ১৯০০ সালে যে-সংশয়গ্রস্ততা ও সংকট তাদের মধ্যে বিরাজমান ছিল ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালেও সেই অবস্থাটা অপরিবর্তনীয়ই রয়ে যায়। এই সংশয়গ্রস্ততা ও সংকটের বিন্দুই ঔপন্যাসিকের যাত্রাবিন্দু। লালসালু উপন্যাসে চিত্রিত মহব্বতনগর গ্রামের জনসমষ্টির মধ্যে এমন একজন লোকের জন্ম হয় নি যে গ্রামের লোকেদের নেতৃত্ব দেবে। বহিরাগত মজিদ আসে গ্রামটিতে ত্রাতা হয়ে। এক অদ্ভুত বিরোধাভাসের মধ্য দিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি গ্রামটির অধিবাসী যখন তাদের গ্রামের মধ্যে প্রাচীন পরিত্যক্ত একটি মাটির ঢিবিকে মজিদ ‘মোদাচ্ছের পিরের মাজার’ বলে ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণার মধ্যে থাকে নির্দেশ, দৈববাণীর মত উচ্চারণ এবং ভবিষ্যদ্বাণীর চরিত্র। মজিদ, মাজার এবং মজিদের নির্দেশনাই লালসালু’র গ্রামের নতুন অস্তিত্বের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। বিপুল এক ব্যর্থতার ভার দিয়ে শুরু উপন্যাসের। সে-ব্যর্থতা গ্রামবাসীর, জনগণের। এত-এত বছরের অতিক্রান্তির পরেও জীবনসমুদ্রে তাদের তরি ঘুরপাক খায় কাণ্ডারিহীনতায়। মজিদ সেই কাণ্ডারি, স্বঘোষিত মেসায়া। বলা যায়, একেবারে শূন্য থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় মজিদের অস্তিত্ব। মুহূর্তেই একটি গ্রামের একটি জনগোষ্ঠির সমস্ত ইতিহাস সমস্ত জীবনচক্র হয়ে পড়ে মূল্যবিহীন। মজিদের ইচ্ছের যূপকাঠে সমার্পিত তাদের মস্তক। অদৃশ্য মাটির ঢিবি এবং অদৃশ্য বিধাতা’র নিয়ম চালু হয় মহব্বতনগরে। আর সবকিছুর ওপরে দণ্ডায়মান সকল শক্তির কারবারি মজিদ। এভাবেই পূর্ববঙ্গের জাতিতাত্ত্বিক অন্বেষণের শব্দচিত্র হয়ে আসে লালসালু। লক্ষ করতে হয়, এক শ্রাবণে দেশবিভাগ এবং পরের শ্রাবণে লালসালু উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। দেশবিভাগের ডামাডোলের মধ্যেই চলছিল তাঁর উপন্যাস-রচনার কাজ। স্বাধীনতা ও নতুন দেশপ্রাপ্তির এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পাওয়া গেল এমন এক জনজীবনের কাহিনি যেখানে মানুষের বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা রুদ্ধ। লেখক কথিত ‘শস্যহীন মরার দেশ’-এ জাগরণ দূরে থাকুক, ‘দিনের পর দিন’ সেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় মানুষের ‘মর্মন্তুদ কান্না’।
জগতের কোনো কাজই উদ্দেশ্যশূন্য নয়। উপন্যাসেরও থাকে লক্ষ্য। ঔপন্যাসিক যেহেতু তাঁর সেই লক্ষ্য সম্পর্কে আগাম কিছু বলেন না সেক্ষেত্রে শব্দে গড়া তাঁর পৃথিবী-পর্যটনের মধ্য দিয়েই রচিত উপন্যাসটির মর্ম উদ্ধার করতে হয়। যখনই আমরা কোনো উপন্যাস পাঠে যাত্রা করি, আমরা একটি নতুন জগতে প্রবেশ করি। বাখতিনের দৃষ্টিতে আমরা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করি জীবনে। মিশেল ফুকো’র মন্তব্য অনুযায়ী, ভাষা আসলে সূচক হলো মুক্তির। সে-অর্থে উপন্যাসের জগত লেখকের মুক্তি আস্বাদনের জগত। কিন্তু লেখকের মুক্তিরও নির্দিষ্ট সীমা-পরিসীমা থাকে। নিজস্ব মুক্তির অনুভবের রেখাপথ ধরে কতটুকু যেতে পারেন লেখক তার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়-
“লেখক যে ভাব আর ভাবনাই সাজিয়ে দিন উপন্যাসে, ভিত্টা তাঁকে গাঁথতেই হবে খাঁটি বাস্তবতার। যতই খাপছাড়া উদ্ভট
হোক উপন্যাসেরই চরিত্র, মাটির পৃথিবীর মানুষ হয়ে তাকে খাপছাড়া উদ্ভট হতে হবে। যত অসম্ভব ঘটনাই ঘটুক উপন্যাসে,
সম্ভাব্য ঘটনাকে আশ্রয় করেই তাকে কাল্পনিক অসম্ভতার স্তরে উঠতে হবে। উপন্যাসেও কাব্য সৃষ্টি করা যায়, কল্পনা পার হয়ে
যেতে পারে বাস্তবতার সীমা, গড়ে উঠতে পারে এমন এক মানস জগৎ যার অস্তিত্ব লেখকের মন ছাড়া কোথাও নেই; কিন্তু বাস্তব
মানুষ বাস্তব জীবন বাস্তব পরিবেশ অবলম্বন করেই এসব ঘটাতে হবে।” [‘উপন্যাসের ধারা’, লেখকের কথা]
কল্পনা যত অতলস্পর্শীই হোক না কেন তার সুতো যে বাস্তবের লাটাইয়ে আটকানো সেটা অসম্ভব কল্পনার উদ্ভাবক গালির্ভস্ ট্রাভেল্স্-এর স্রষ্টা জোনাথান সুইফ্ট্ও স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেন না- ১৭২৬ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাসের সঙ্গে কাজেই জুড়ে দেন এমন মন্তব্য: ট্রাভেল্স্ ইন্টু সেভারেল রিমোট নেশন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। কিন্তু কেউ প্রশ্ন ওঠান না, আদতে তেমন জাতির বা তেমন জনপদের অস্তিত্ব আদৌ রয়েছে কিনা। কেননা, সুইফ্ট্-এর অদ্ভুতত্বের ভেতরে নিহিত তাঁরই সমকালীন ইংল্যান্ড। আর, সমকালীন ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতার পুঁজির নির্ভরতায় তিনি রচনা করেন সমগ্র মানবজাতির বাস্তবতা।
আরো পড়ুন: ইতিহাসের বাস্তব এবং লেখকের বাস্তব : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১
সেদিক থেকে দেখলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র লালসালু এবং অন্য উপন্যাসদ্বয় যথেষ্ট বাস্তবতাশ্রয়ী, যথেষ্ট প্রত্যক্ষ। ১৯৫৪ সালে রবার্ট হাম্ফ্রে স্ট্রিম অব কনশাসনেস-এর আঙ্গিকে উপন্যাসকে বিচার করতে গিয়ে বলেছিলেন, মানবমনের গহিনে নিত্য ক্রিয়মান নাটকের নানা রূপ নানা বিভঙ্গ উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে ঠাঁই নেয়। ১৯৬৩ সালে গেঅর্গ লুকাচ (দ্য থিওরি অব দ্য নভেল) উপন্যাস প্রসঙ্গে জানান, সমস্যাপীড়িত নায়কের আত্মমুখী অভিযাত্রা হলো উপন্যাস। উপন্যাসে ঘটে নায়কের আত্মআবিষ্কার, তার সত্তার উৎস-সন্ধান। ১৯৬৬ সালে উপন্যাস প্রসঙ্গে ডেভিড লজ মন্তব্য করেন, উপন্যাস আমাদেরই পৃথিবী। এমনকি উপন্যাসের যে-জীবন আমরা দেখি নি বলেই যে সে-জীবন থাকবে না সেটাও বলার উপায় নেই। ১৯৬৮ সালে ফরাসি সমালোচক এ্যানে না (দ্য নভেল অব দ্য ফিউচার) বলছেন, উপন্যাস আপাত আড়াল হয়ে থাকা সত্তার বিশ্লেষণ। উপন্যাসে জীবনের ব্যর্থতা, কুশ্রিতা সবই প্রকাশিত হয়, কোনোকিছুই বাদ পড়ে না। ১৯৭৩ সালে রচিত পৃথিবীর প্রথম মাওরি উপন্যাস উইটি আইহিমায়েরা’র ট্যাঙ্গি-র দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। উপন্যাসটি ইউরোপিয় কিংবা পাশ্চাত্য অভ্যাসে অভ্যস্ত পাঠকের নিকটে ঠেকতে পারে অচেনা। নায়কের পিতার মৃত্যু, অন্ত্যেষ্টি, শোকসঙ্গীত, মৃতের প্রশস্তি, বক্তৃতা সবকিছুই আছে উপন্যাসে। পরিবার, সংঘ, সংস্কৃতি সব। পড়তে গেলে মনে হতে পারে, উপন্যাস জিনিসটা আদতে কী তা না জেনেই উইটি রচনা করেছেন তাঁর উপন্যাসটি। কিংবা ধরা যাক, রুশদি’র মিডনাইট চিলড্রেন বা টুটুঅলা’র দ্য পাম-ওয়াইন ড্রিংকার্ড উপন্যাসদ্বয়ের কথা। এক ধরনের অস্থির ও অস্থিতিশীল আঙ্গিকে রচিত দু’টো উপন্যাসই। বোর্হেস যখন বলেন, যা-ই ঘটে তা-ই অবলম্বন, তা-ই উপকরণÑ অপমান, অসম্মান, দুর্ভাগ্য সবই শিল্পের কাদামাটি লেখকের নিকটে। উপকরণগুলোর মাধ্যমে ঘটাতে হয় রূপান্তর। ঔপন্যাসিক দস্তয়ভস্কির কিংবা মানিকের স্ব-স্ব মৃগিরোগের ইতিহাসও তাঁদের সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। আঙ্গিকের বিচারে ওয়ালীউল্লাহ্’র লালসালু উপন্যাসটি সমগ্র পূর্ববঙ্গের উপন্যাসের ইতিহাসেই অভিনব। উপন্যাস প্রসঙ্গে ওপরে যেসব কথা বলা হলো সেসবের অনেক কিছুই উপন্যাসটিতে বর্তমান। কিন্তু উপন্যাসটির অভিনবত্বের হেতু নয় এসব বিশেষত্ব। উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লেখা নয় কিন্তু উপন্যাসটির সর্বত্র উপস্থিত একজনই- সে মজিদ। যত ঘটনা ঘটে, চরিত্রদের মধ্যে যত কথাবার্তা হয় সবই তাকে কেন্দ্র করে। অর্থাৎ গোটা উপন্যাসের ভরকেন্দ্র মজিদÑ আদি, মধ্য ও অন্ত সর্বত্র তার বর্তমানতা বিরাজমান অনেকটা অন্তর্যামীর মতন। মজিদ তার চোখ দিয়ে দেখে গোটা জনপদ এবং আমরাও মজিদেরই চোখ দিয়ে দেখি মহব্বতনগরকে। উপন্যাসের সমাপ্তিতেও কিন্তু মজিদের শেষ নয়, লালসালু’র যেখানে শেষ চাঁদের অমাবস্যা-র সেখানে শুরু। এবং আবার ছয় দশকের ব্যবধানে হয়তোবা সেই জনপদেরই কাহিনি বর্ণিত হতে থাকে। বড়বাড়ি, দাদাসাহেব এবং কাদের যেনবা মজিদেরই নবতর সংস্করণ। সেখানেই শেষ নয়। চাঁদের অমাবস্যা’র যেখানে শেষ, কাঁদো নদী কাঁদো’র সেখানে শুরু। দাদাসাহেব এবং কাদেরেরই উত্থান যেনবা কালু গাজি ও খেদমতুল্লা। অর্থাৎ এক দীর্ঘ মজিদ-পরম্পরা’র কাহিনি আমরা পাই ঔপন্যাসিকের কাছ থেকে যেটির শুরু লালসালু’তে এবং যেটির শেষ কাঁদো নদী কাঁদো’তে নয়, যদিও কাঁদো নদী কাঁদো উপন্যাসও একসময়ে পরিসমাপ্ত হয়।
সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর ওয়ালীউল্লাহ্’র উপন্যাসবিষয়ক আলোচনায় দেখিয়েছেন, লালসালু-তে ভয়-ভীতিসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ৭০ বার, চাঁদের অমাবস্যা-য় ১৫০ বার এবং কাঁদো নদী কাঁদো-তে ১৭৫ বার। দেশ স্বাধীন এবং নতুন তবুও ভয়ের। ভয়-ভীতি ছিল ১৯০০ সালে এবং ভয়-ভীতি থাকে ১৯৬৫ পর্যন্ত। বোঝাই যায়, সেই ভয়-ভীতি অমূলক নয়। এর সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষমতা-নিয়ন্ত্রণ-স্বৈরাচার-সমর্পণ-পুরুষাচার এবং সর্বোপরি ধর্মীয় আচরণের। ঐতিহাসিক-সমাজতাত্ত্বিকভাবে দেখলে মজিদ চরিত্রটির জন্ম সভ্যতার প্রাচীন পরিবৃত্তে। যুগে-যুগে এবং স্থানে-কালে তার নাম-পরিচয় পাল্টেছে মাত্র। ওয়ালীউল্লাহ্’র উপন্যাস আমাদের জানান দেয়, ব্যক্তির বিকাশের পথ রুদ্ধ থাকলে, সামাজিক জীবন প্রবল স্থবিরতায় আক্রান্ত হলে সেখানে স্বাধীনতা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় অনুষঙ্গ অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই, তাঁর উপন্যাস সমগ্র বাঙালি জাতির ব্যক্তিক-সামাজিক অসহায়তা অনিরাপত্তা ও বিকাশহীন অবরুদ্ধতার প্রতিচিত্রণ। মহব্বতনগর, আওয়ালপুর, চাঁদপারা, কুমুরডাঙ্গা এসব জনপদ বৃহত্তর স্থানিকতারই প্রতীকায়ণ। তবু এসব প্রতীক প্রত্যক্ষতাচিহ্নিত। ক্ষমতা পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় বলয়ে কতদূর পর্যন্ত এবং কেন স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে তারই বৃত্তান্ত ওয়ালীউল্লাহ’র উপন্যাসসমূহ। চতুর্দশ শতাব্দীর সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের আল মুকাদ্দিমা গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছিল সেই সময়কার মজিদদের চরিত্র। জনসাধারণের বিশ্বাসকে পুঁজি করে ধর্মীয় শীর্ষাবস্থানে থাকা পুরুষ (প্রাচীন পুরোহিতদের মতন) একটি জনপদে যেভাবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে তারই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন খালদুন। ওয়েবারিয় সমাজবিজ্ঞানের (১৯২২) আলোকেও আমরা দেখবো, ব্যক্তির ক্ষমতা এমনই কার্যকারিতায় পৌঁছায় যা শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে পরিণত করে বিশাল প্রতিষ্ঠানে। ব্যক্তির ক্ষমতার সেই বলয়ে গ্রাসিত হয় তার বিপুল পরিপাশর্^। ওয়েবারিয় তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, মজিদের ক্ষমতার রয়েছে একটি কর্তৃত্বপরায়ণতার ঐতিহ্য যেটির পরবর্তীতে সম্প্রসারণ ঘটে ওয়ালীউল্লাহ্’রই অন্য দু’টি উপন্যাসে। ক্ষমতাকে মজিদ ব্যবহার করেছে প্রচ- চমক এবং নাটকীয়তার একত্র সমন্বয় ঘটিয়ে। মহব্বতনগর গ্রামে ঢোকার তার গল্প থেকে শুরু সেই চমক এবং পরিত্যক্ত মাটির ঢিবিকে লাল সালুকাপড়ে আবৃত করাটা তার আরেকটি চমক। এভাবে গোটা উপন্যাসজুড়ে চলমান থাকে মজিদসৃষ্ট চমক-তৎপরতা। মজিদ তার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং স্বেচ্ছাচারিতাকে ধর্মীয় যুক্তির দ্বারা আইনসিদ্ধ করবার চেষ্টা চালায়। তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে চাঁদের অমাবস্যা-য় যেখানে অলিখিত আইনের অনুশাসনে বাঁধা থাকে গ্রামবাসী। কাঁদো নদী কাঁদো¬-তে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ইশারা মজিদ, বড়বাড়ি এবং ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব সবকিছুকে গেঁথে দেয় একসূত্রে। তিনটি উপন্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভয়-ভীতির শেষ হয় না, মজিদের শারীরিক মৃত্যু ঘটলেও এক বিস্ময়কর মজিদাবর্তন চলতেই থাকে জনপদ জুড়ে।
আরো পড়ুন: গারো পাহাড়ের চিঠি: পাতিল হাঁটি ও জ্যোতির শৈশব
খালদুনের ধর্মীয় পুরুষ যেভাবে মহাজন-ভূমিদার ও কর্তৃপক্ষ হয়ে ওঠে, ওয়েবারিয় ক্ষমতাপুষ্টরা যেভাবে নেতৃত্বের অবস্থানে পৌঁছায়, সেভাবেই মজিদেরও ঘটে ক্ষমতাসন-নিশ্চয়তা। তবে খালদুন-ওয়েবারের তত্ত্বে রক্তমাংস ও অনুভূতিপ্রবণ ক্ষমতাপুরুষের দেখা পাই না, যেটা আমরা পাই ওয়ালীউল্লাহ্’র উপন্যাসে। একজন ক্ষমতাহীন মজিদ ক্ষমতাপুষ্ট হয়ে ক্রমে আগ্রাসী অনুভূতিশূন্য হিংস্র সত্তায় পরিণত হয়। তার সেই হিংস্রতার প্রকাশ সর্বত্র- পারিবারিক অন্তঃপুরে, গ্রামীণ সমাজের সীমানায়, এমনকি গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরের জগতেও। গ্রিক দার্শনিক পিত্তেকাসের (৬৪০-৫৬৮ খ্রি: পূ:) মন্তব্যানুসারেই যেন নিজের ক্ষমতাকে নিজের যোগ্যতা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে মজিদ। আর সেটা করতে গিয়ে প্রাথমিক ক্ষমতার সিঁড়ি বেয়ে সে সর্বনাশের চূড়ায় পৌঁছায়। ১৮৮৭ সালে লর্ড এ্যাকটন (১৮৩৪-১৯০২) যেকথা বলেছিলেনÑ ক্ষমতার কাজই হলো দুর্নীতি করা আর চূড়ান্ত ক্ষমতা দুর্নীতি করে চূড়ান্ত রকমের, সেকথা মজিদ সম্পর্কেও শতভাগ প্রযোজ্য। মজিদ চরিত্রের তৎপরতা, তার মনোভাবনা, তার সংলাপ সবকিছুতেই আমরা হয়তো একজন ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি লক্ষ করি। কিন্ত মজিদ আসলে বহুগুণিতক এবং তার ভাবনা, কার্য, সংলাপ এসবকিছু নিয়ে সে একটি বহুবাচনিক বিন্যাস ও কাঠামোর প্রতিনিধি। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির সমন্বয়ে একা মজিদ একদিকে এবং একটি বিপুল জনসমষ্টি আরেকদিকে। মজিদের উচ্চারিত সংলাপ (প্রায়শ তা নির্দেশনামার মত শোনায়।) তারই কণ্ঠনিঃসৃত হলেও তাতে থাকে দ্বিবাচনিকতা এমনকি বহুবাচনিকতার প্রক্ষেপ। মিখাইল বাখতিন যেমন বলেন, ভাষা বলে একজন কিন্তু সে-ভাষা তবু নয় একক ভাষা। মজিদ চরিত্রের সংলাপে এবং মজিদের সমগ্র সত্তায় আশ্চর্যজনকভাবে প্রলিপ্ত থাকে একক নয় বহু। মজিদ যখন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে সে-কথাও কথনের অঞ্চলগত সীমানা ছাড়িয়ে বহুস্তর বক্তব্যে রূপ নেয়। মজিদের চারিত্রিক সত্তার মৌল কাঠামোটি বুঝতে পারা দরকার ওয়ালীউল্লাহ্’র পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়কে পাঠ করবার জন্যে। কেননা, লালসালু’র মজিদ চাঁদের অমাবস্যা’র বড়বাড়ি এবং কাঁদো নদী কাঁদো’র কালুগাজি-খেদমতুল্লা’র প্রেল্যুড। কালু গাজি-খেদমতুল্লা’র পৃথিবীতে বিকশিত হওয়া ব্যক্তিসত্তা উপন্যাসটির নায়ক মুহাম্মদ মুস্তফাই একপর্যায়ে আত্মহত্যা করে।
[ক] কিন্তু এই কথা জাইনো- কোন কথা আমার অজানা থাকে না।
[খ] মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও যানি কেউ হুনে না।
প্রথমটি জনৈক গ্রামবাসীর প্রতি এবং দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় স্ত্রী জমিলা’র প্রতি মজিদের সংলাপ। ধর্মীয় শক্তিতে বলবান মজিদের অস্তিত্বের শেকড়টি সুপ্রতিষ্ঠিত। তার সঙ্গে সর্বান্তর্যামীর পার্থক্য ঘুচে যায় গণমনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে। সেই অবস্থান থেকে যখন তার দ্বিতীয় সংলাপটি উচ্চারিত হয় সেটি আসলে আর সংলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই একটিমাত্র বাক্যের নেপথ্যে তাকে শত-সহ¯্র বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য। এমনকি বাক্যটির স্বত্বও আর মজিদের নিজের নয়। সংলাপটি পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সীমানা পেরিয়ে এক আন্তঃমহাদেশীয় ইঙ্গিতে পরিণত হয়। তখন মজিদ এবং তার ক্ষমতার অবস্থানটি পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিকতা উৎরে ভিন্ন এক জীবনচক্রের প্রতিফলক হয়ে দাঁড়ায়। পুরনো নয় একেবারে আজকের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়েও যদি বলি, সোমালিয় ডাচ-মার্কিন লেখক আয়ান র্হিসি আলি’র (জন্ম ১৯৬৯) কথা বলা যাবে। তাঁর গ্রন্থগুলো (দ্য কেইজ্ড্ ভার্জিন, ইনফিডেল : মাই লাইফ, নোম্যাড : ফ্রম ইসলাম টু আমেরিকা) পাঠ করলে আজ এই ২০২০ সালে পাঠকের মনে হতে পারে, আয়ান হচ্ছে জমিলা এবং তার বিপরীতে বিবিধ কানুন-নিষেধাজ্ঞার দ-ধারী অযুত মজিদ। লালসালু উপন্যাসের বাহাত্তর বছর পরেও মজিদের কণ্ঠনিঃসৃত সংলাপের উচ্চারণ বাংলাদেশে নয়, সোমালিয়ায় এবং আরও আরও দেশে-প্রদেশে এবং সেই সংলাপ অনন্তর মৃত্যু পরোয়ানা হয়ে নিষেধ-না-মানা আয়ানের পিছু-পিছু ধাওয়া করে চলেছে। এবারে লক্ষ করা যাক, মজিদের উচ্চারণ এবং সেটির প্রতিক্রিয়া এবং কার্যকারণ লালসালু উপন্যাসে কী পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।
খালদুন এবং ওয়েবারের তাত্ত্বিকতার সৃজনশীল সম্প্রসারণ ওয়ালীউল্লাহ্’র মজিদ চরিত্রটির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নির্ধারিত হয় উপন্যাসটির গতিপথ। একটি চরিত্রকে এমন সর্বময় করে তোলেন ঔপন্যাসিক স্বয়ং নাকি মজিদকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোনো উপায় ছিল না কারও হাতেইÑ না মহব্বতনগরের অধিবাসীদের না স্বয়ং ঔপন্যাসিকের। আসলে মজিদের নির্ণায়ক ইতিহাসই, ঔপন্যাসিকের পক্ষে সেই গতির বিপরীতে হাঁটাটা সম্ভব হয় না। মহব্বতনগরের তথা পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় সমস্ত ক্ষমতার আপাত দৃশ্যমান উৎস ভূমি। দেশভাগের পরে ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান ল্যান্ড এ্যান্ড টিনেন্সি এ্যাক্ট অনুসারে ক্ষমতাধারী ভূমির মালিকদেরই দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। সমাজবিজ্ঞানী আন্দ্রে বেতেইও বলেছিলেন, ভারতীয় উপমহাদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে দৃশ্যমান একমাত্র সম্পদ হলো ভূমি। কাজেই লালসালু উপন্যাস সে-অর্থে সমাজতাত্ত্বিক সত্যতার অনুগামী। উপন্যাসটিকে পূর্ববঙ্গের সামাজিক বিন্যাসের সমান্তরালে দেখলে মহব্বতনগরের সবচাইতে ক্ষমতাবান লোকটি অঢেল জমির মালিক খালেক ব্যাপারী। ভূমিই তার অবস্থান, ভূমিই তার শরাফতি বা সামাজিক উচ্চাবস্থানের ঐতিহ্য। সমাজবিজ্ঞানী নাজমুল করিম তাঁর পূর্ববঙ্গ বিষয়ক সমাজগবেষণায় দেখান, বস্তুত ‘আশরাফ’ এবং ‘আতরাফ’ এই দু’টি মুখ্য শ্রেণিতে বিভক্ত পূর্ববঙ্গের সমাজ। সে-হিসেবে খালেক ব্যপারীরা জমির মালিক বলে ‘আশরাফ’ বা অভিজাত-স্থানীয় এবং বাকিরা ‘আতরাফ’ বা মূলত উৎপাদক শ্রেণি বা নিম্নশ্রেনিভুক্ত। নাজমুল করিম ‘আরজাল’ নামের একটি মধ্যশ্রেণির অস্তিত্বের কথা বলেছেন যদিও সে-শ্রেণি সেভাবে ক্ষমতাশালী নয়। এটি হলো লিখিত-গবেষিত ইতিহাসের উপাত্ত। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, গ্রামের সবচাইতে ক্ষমতাবান লোক খালেক ব্যাপারীও সে-অর্থে জমির মালিক না-হওয়া মজিদের ক্ষমতার নিকটে মেনে নিচ্ছে পরাভব। মজিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মত প্রতিপক্ষতা লক্ষণীয় নয় গ্রামে। যখনই মজিদের ক্ষমতার আসন খানিকটা দুলে উঠবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে মজিদের আগ্রাসন। একপর্যায়ে সেই আগ্রাসন পরিণত হয় সন্ত্রাসে। তার সেই সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয় ঘর এবং বাহির। মজিদের ক্ষমতার উৎস কাজেই ধর্ম। ধর্মের অপরিসীম ক্ষমতা ভূমিস্বীকৃতির অবস্থানকেও ছাড়িয়ে যায়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র সমকালীন অন্যান্য ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের সামাজিক বাস্তবতার প্রতিতুলনায়ও একথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। শহীদুল্লা কায়সারের সংশপ্তক উপন্যাসে গ্রাম্য সালিশের হুরমতি-বিচারপর্বে বিচারের রায় ঘোষিত হয় জমিদার ফেলু মিঞা নয়, মসজিদের ইমামের কণ্ঠে। এটি ১৯৩৭ সালের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঘটনা। আবু ইসহাকের সূর্যদীঘল বাড়ী উপন্যাসে জয়গুনের ‘বেপর্দা’-কর্মের শাস্তিবিধান করেন মসজিদের ইমাম। জয়গুনকে ‘তওবা’ (প্রায়শ্চিত্ত) করানো হয় তার কৃতকর্মের কারণে। এটি ১৯৪৭-৪৮ সালের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ঘটনা। অর্থাৎ লালসালু’র অর্ধ শতাব্দী কাল পরেও জমির মালিকদের চাইতেও ক্ষমতাবান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের প্রধানগণ।
আরো পড়ুন: নজরুলকাব্যে মানিকগঞ্জের চিত্রকল্প
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর মজিদ চরিত্রের মাধ্যমে একটি প্রচলিত সত্যের নতুনতর শিল্পপ্রতিষ্ঠা দেন। তাছাড়া তাঁর রচিত পর-পর তিনটি উপন্যাস সেই শিল্পরূপকে পৌঁছে দেয় সুদৃঢ় গাঁথুনিতে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের যেমন রাবণ, ওয়ালীউল্লাহ্’র মজিদ। মধুসূদন যেভাবে রাবণ চরিত্রের নবনির্মাণের মাধ্যমে ভেঙে দেন প্রচলিত নিয়মের দেয়াল, আঘাত করেন শাস্ত্রীয় ধারণাকে ঠিক সেরকম ওয়ালীউল্লাহ্’র মজিদ দুমড়েমুচড়ে দেয় পবিত্রতার ধারণাস্পৃষ্ট ধর্মীয়-সামাজিক বিশ্বাসকে। মজিদের মত এমন আগ্রাসী এবং সন্ত্রাসী চরিত্র বাংলাদেশের সাহিত্যে ছিল অকল্পনীয়। তার অতল সন্ত্রাসের শিকার প্রধান-অপ্রধান নির্বিশেষে উপন্যাসটির প্রায় সবক’টি চরিত্র। ঔপন্যাসিকের কৃতিত্বের জায়গাটাও মজিদের সন্ত্রাসকেন্দ্রিকতার মধ্যে নিহিত। মনে হতে পারে, একচ্ছত্র সন্ত্রাসের স্রষ্টা মজিদ চরিত্রটি মাত্রিকতাহীন, একমুখী। মজিদের শক্তির ভেতরেই সুপ্ত থাকে তার দুর্বলতার বীজ। সে-বীজের উদ্গম বা নিষিক্ততার লক্ষণ আসন্ন হয়ে না উঠলেও বীজটির বিদ্যমানতা চরম আশাহীনতার ঊষর প্রান্তরে ক্ষীণ হলেও জাগিয়ে রাখে প্রত্যাশা। সে-প্রত্যাশা উপন্যাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে না, ঔপন্যাসিকের দার্শনিকতা সেটির উদ্ভাবক। উদ্ভাবনার কাজটি তাঁকে করতে হয় জীবনের ইতিবাচক প্রেরণার অগ্রগামিতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। ওয়ালীউল্লাহ্ তলস্তোয়ের মত বিশ্বাসী মানুষ নন, তাঁকে খানিকটা সংশয়বাদীই বলতে হবে। মজিদের একচেটিয়া বিস্তার দেখে এমনটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, শেষ পর্যন্ত নষ্ট-ভ্রষ্ট মজিদদেরই জয় ঘোষিত হবে। বস্তুত ওয়ালীউল্লাহ্’র উপন্যাসের জন্যে জীবনের যে-বাস্তবতা অপেক্ষমান থাকে তা এতই নিরাশাজনক, এতই ভয়াবহ যে লেখকের পক্ষে মিথ্যে আশার আভাসও সৃষ্টি করা দুরূহ। কাফকা তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রডকে বলেছিলেন, আশা হয়তো কোথাও না কোথাও রয়েছে কিন্তু তা আমাদের জন্যে নয়, হয়তো তা ভবিতব্যের জন্যে। লালসালু’র ¯্রষ্টাকে পরিস্থিতির শিকার অসহায় পর্যবেক্ষক হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। তবু, অন্তিমে বন্ধ্যা জমিতে ফসলের মত, মরুমাটিতে সবুজাভ জাগরণের মত ঘটনা উপন্যাসে ঘটে। মধুসূদনের রাবণ যেমন পরম করুণার আধার হয়ে দেখা দেয় তেমনি ওয়ালী’র মজিদ দেখা দেয় চরম ঘৃণার আধার হয়ে। ঔপন্যাসিক কুশলতার সঙ্গে মজিদের একমাত্রিক চরিত্রটিকে বিভিন্ন মোচড় দিয়ে এমন এক পরিণতিতে নিয়ে যান যেখানে ঐতিহ্যে অভ্যস্ত গণমানসের মনোজগতে খানিক ধন্দ জাগে কিন্তু মজিদ চরিত্রের ঘৃণ্যতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। একটা দেশ স্বাধীন হলো। নতুন দেশের প্রাপ্তিচেতনায় চারদিকে ধুন্দুমার দুন্দুভি চলতে লাগলো। দারিদ্রজর্জর লোকেদের চোখের সামনে ঝোলে স্বপ্ন- দিন আরও ভাল হবে। এমনকি শিক্ষিত জনমানসও ভেসে গেল আনন্দ-জোয়ারে। পূর্ববঙ্গের বহু কবির কবিতায় ঢেউ উঠলো ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’-এর। এককথায় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি এবং পূর্ববঙ্গের নবচেতনা-উদ্বুদ্ধ মানুষ সামিল হলো এক উচ্চ- উচ্চকিত কোরাসে। সেদিক থেকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এবং পূর্ববঙ্গের কথাসাহিত্যিকদের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। তাঁদের উপন্যাসে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ দূরে থাকুক, উঠে এলো জীর্ণ-সোঁদা-স্যাতলাপড়া জীবনের চিত্র। প্রচারণায় ভেসে যাওয়া হয় না তাঁদের। বলা যায়, তাঁরাই তখন পালন করেন প্রকৃত ভ্যানগার্ডের ভূমিকা। কোনোরকম রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারণায় না গিয়ে, কোনোরকম বিরোধ-বিপ্রতীপতার বিতর্ক না করে কেবল বয়ে যাওয়া সত্যিকারের জীবনটাকে তুলে ধরার মধ্যেই তাঁরা ব্যস্ত থাকলেন। একা ওয়ালীউল্লাহ্ই কিন্তু করলেন না সে-কাজ। এক নিঃশ্বাসে বেশ কয়েকজন কথাকারের নাম এ-প্রসঙ্গে উচ্চার্য যাঁরা সেদিন পাকিস্তানি প্রচারণার বিপরীতে সৃজনশীল বাঙালি জাতীয়তাবাদের নিশানা উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের শব্দের পৃথিবীতে। শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, শহীদুল্লা কায়সার, সরদার জয়েনউদ্দিন, শামসুদদীন আবুল কালাম প্রমুখ প্রধান ঔপন্যাসিকরাই ছিলেন সেদিন সামনের কাতারে। এঁদেরই কর্ণধার হ’ন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যাঁর লালসালু ঘটায় আনুষ্ঠানিক অভিষেক।
আবারও যদি মুহূর্তের জন্যে কুন্ডেরায় ফিরে যাই, উপন্যাস ইতিহাসেরই সমান্তরাল পথ, এবং একই সঙ্গে মনে রাখি বাখতিনকেও- উপন্যাস শৈলি, ভাষা (এবং স্বর), চরিত্র সবকিছুর একত্রসম্মিলন। ১৯৪৮ সাল, ধরা যাক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ’র ঔপন্যাসিক উন্মেষকাল, এবং তারই সমান্তরালে সদ্য জন্ম নেওয়া পরস্পর কয়েক হাজার মাইল ব্যবধানের ভিত্তিতে গড়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যেই চলমান এক অভিন্ন তৎপরতা। সাদামাঠা বিশেষ্যপদে যেটিকে বলা চলে সন্ত্রাস। ১৯৪৮ সাল থেকেই ক্রমান্বয়ে প্রকটিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসী চরিত্র। লালসালু উপন্যাসটিকে এক বিশেষ সমাপতনমূলক পরিস্থিতির আলোকে না-দেখে উপায় নেই। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ^বিদ্যালয় কার্জন হলে প্রদত্ত বক্তৃতায় উর্দুকে সর্বতোভাবে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে উর্দু’র পক্ষে এমন যুক্তি দেওয়া হয় যে উর্দু পবিত্র ভাষা যেহেতু উর্দু বর্ণগুলো দেখতে আরবি’র মতন। সেই বক্তৃতায় জিন্নাহ্ পূর্ববঙ্গবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এখনও রাষ্ট্রের ঐক্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে এবং ষড়যন্ত্রকারীরা মুসলমান ধর্মাবলম্বীই। জিন্নাহ্’র সেই ঘোষণা’র বিরুদ্ধে বাঙালি ছাত্ররা ফেটে পড়ে প্রতিবাদে যার ঐতিহাসিক পরিণাম ১৯৫২-র ভাষা-আন্দোলন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্’র লালসালু উপন্যাস বেরোয় ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে। মহব্বতনগর গ্রামের শিক্ষিত যুবক আক্কাসের স্কুল-প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভণ্ড পির মজিদ এবং জমিদার খালেক ব্যাপারি’র তৎপরতায় বাতিল হয়ে যায়। তার পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয় মক্তব। আরবি ভাষা যেহেতু পবিত্রতার প্রতীক, ইংরেজি এবং বাংলাকে হঠিয়ে দিয়ে কায়েম হয় সে-ভাষারই রাজত্ব। আর মৃদু প্রতিবাদকারী উদ্যোক্তা একা আক্কাস নয় তার পিতাসহ দু’জনকেই জনসমক্ষে এই বলে অপমান করা হয়, তাদের বাপ-ব্যাটা উভয়ের কেউই ধর্মীয় রীতি-অনুযায়ী পুরুষাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ-পর্ব সম্পন্ন করে নি। অতঃপর গ্রামে ইংরেজি শেখার স্কুল-প্রতিষ্ঠার বিষয়টির ঘটে অপপ্রিতি এবং এক দড়িতে ফাঁসির মত পিতা-পুত্র দু’জনেরই পুরুষাঙ্গের ত্বকচ্ছেদপর্ব সম্পন্ন হয়। এই ঘটনাটিকে স্পষ্ট সন্ত্রাসী তৎপরতা হিসেবেই দেখতে হয়। মজিদ যে কেবল আক্কাস এবং তার পিতার ব্যক্তিগত জীবনে বলপূর্বক অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদেরকে অপমানিত করেছে তা-ই নয়, গোটা গ্রামকে সে তার অনতিক্রম্য ক্ষমতার আগাম হুমকিও দিয়ে রাখে। পরে, সে-হুমকি’র পরিণতিও ঘটে ভিন্নতর প্রক্রিয়ায়। এখন, ১৯৪৮-এর জুলাই মাসে প্রকাশিত লালসালু উপন্যাসের পাঠকের নিকটে মজিদকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্’র মত কিংবা জিন্নাহ্কে মজিদের মত মনে হওয়াটাকে অস্বাভাবিক বলা যাবে না। যদি লালসালু ২৪ মার্চের পরে রচিত হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে সেটি বাস্তবের অসাধারণ প্রতিনির্মাণ, আর যদি লালসালু’র রচনাকাল হয় ২৪ মার্চের আগে তাহলে বলতে হবে ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ এক আশ্চর্য ভবিষ্যতদ্রষ্টা।#
চলবে…