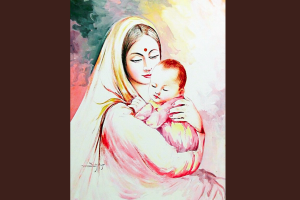বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে প্রান্তিক মানুষ
সনৎকুমার নস্কর
বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের জগতে বিজন ভট্টাচার্য এক অবিস্মরণীয় নাম। গত শতকের চল্লিশের দশকে যে গণনাট্য আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, বিজন ছিলেন তার অন্যতম নেতৃত্ব। বস্তুত তাঁর নাটকগুলি দিয়েই গণনাট্য সংঘ তার যাত্রা শুরু করেছিল। এই সংগঠনের সেরা প্রযোজনা ছিল পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা ‘নবান্ন’। খেয়াল রাখতে হবে, গণনাট্য আন্দোলন ছিল একটি বিশেষ সময়-সম্ভূত নাট্যিক ক্রিয়াকাণ্ড, যা এর আগে কিংবা পরে ঘটবার মতো পরিস্থিতির অভাব ছিল। এর আগে পেশাদারি নাট্যমঞ্চের সেই যুগটি চলছিল, যেখানে ব্যক্তি-বিশেষের নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনই ছিল মুখ্য। মধ্যবিত্তের কতকগুলো বাঁধা-ধরা আদর্শ ও সেন্টিমেন্টের বাইরে নাটকের আর যাওয়ার জায়গা ছিল না। সেই আবদ্ধতা থেকে বাংলা নাটককে টেনে বার করল গণনাট্য আন্দোলন। সে নাটককে ছড়িয়ে দিল আম-জনতার মাঝখানে। বাংলা নাটকের মঞ্চ জুড়ে এবার ভিড় করতে শুরু করল ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষি, কারখানার শ্রমিক, দালাল, গুণ্ডা, অন্ধ, খোঁড়া, ভিক্ষুক, মদ্যপ এবং এদেরই বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা সমাজের আর একটা শ্রেণি যারা শোষক ও অর্থলিপ্সু বলে পরিচিত। নাটকের পাত্রপাত্রীদের মধ্যে স্পষ্টত তুলে ধরা হতে লাগল শ্রেণিবৈষম্য— ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, শোষক-শোষিত, মহাজন-খাতক, জোতদার-কৃষক, মালিক-মজুর ইত্যাদি দ্বিকোটিক বৈপরীত্যমূলক সম্পর্ক। বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন এই নাট্যধারার অন্যতম অগ্রনায়ক। সুতরাং তাঁর নাটকে প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি ও অবস্থান কীভাবে রূপায়িত হয়েছে এটি একটি সঙ্গত নাট্যজিজ্ঞাসা হিসেবে দেখা দিতে পারে।
নাট্যকার ও তাঁর নাটক সম্পর্কে আলোচনার আগে প্রান্তিকতার (marginality) বিষয়টিকে একটু বুঝে নেওয়া দরকার। ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসির উদ্ভাবনা নিম্নবর্গীয় চেতনা তথা সাব-অলটার্ন থিয়োরির একটি সম্প্রসারিত রূপ এটি। গ্রামসি সাব-অলটার্নের বিপরীতে রেখেছিলেন এলিট বা উচ্চবর্গকে, যারা পরস্পর সম্পর্কান্বিত আধিপত্যের সূত্রে। এই আধিপত্যকে দু’ভাবে ভাগ করা যায়— ১. ভাবাদর্শগত ও ২. রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক । প্রথমটি চিহ্নিত হয়েছে ‘হেজিমনি’ অভিধায়, দ্বিতীয়টি কথিত হয়েছে ‘ডমিন্যান্স’ নামে। ১৯৩০-এর দশকে ‘Prison’s Note Book’-এ গ্রামসি যখন ‘সাব-অলটার্ন’ শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন তখন তার ব্যবহার ছিল বহুমুখী। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ধনতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক আধিপত্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি এই বিশেষ পরিভাষাটি প্রয়োগ করেছিলেন। উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্বে আধিপত্য কায়েম করতে বহুমাত্রিক কৌশল প্রযুক্ত হয় এবং পরিপ্রেক্ষিত বদলের সঙ্গে তাল রেখে বদল ঘটে প্রভুত্বকামী শ্রেণিরও। এই প্রভুত্বকামী ক্ষমতার নানামাত্রিক বিশ্লেষণ যে-সব তত্ত্বের মাধ্যমে করা শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম প্রান্তিকতার তত্ত্ব (Theory of Marginality)। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই যে ধরনের বইপত্র লেখা হয়েছে, তাতে প্রান্তিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে এইরকম কয়েকটি বাক্যবন্ধ মেলে: ‘Marginality is generally used to describe and analyse socio-cultural, political and economic spheres, where disadvantaged people struggle to gain access (societal and spatial) to resources, and full participation in social life. In other words, marginalised people might be socially, economically, politically and legally ignored, excluded or neglected, and are therefore vulnerable to livelihood change.’ (Ghana S. Gurung and Michael Kollmair, Marginality : Concepts and Their Limitations, p. 10)
আসলে নিম্নবর্গের মতো প্রান্তিকতার তত্ত্বও দাঁড়িয়ে আছে ক্ষমতা, আধিপত্য, বৈষম্য ও দ্বিকোটিক বৈপরীত্য (binary opposition)-এর ওপর। স্থানগত দূরত্বের কারণে যে প্রান্তিকতা, সেটি এখানে নগণ্য, প্রান্তিকতার ক্ষেত্রে বড়ো হয়ে উঠেছে মানুষের সামাজিক দিকটি। সামাজিক সম্পর্কের সমতলে যেখানে ক্ষমতাই মূল কথা, সেই ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে যারা দূরে থাকে তারাই প্রান্তিক বলে চিহ্নিত হন। সামাজিক প্রান্তিকতায় তিন ধরনের মাত্রা-বিভাজন দেখা যায়। এগুলি হল–- বর্ণগত, বৃত্তি তথা অর্থগত ও লিঙ্গগত। তবে এদের বিভক্তিকরণটা বায়ু-নিরুদ্ধ কক্ষের মতো নয়। একের মধ্যে অন্যের উপস্থিতিও ঘটে। কোনো একটির মধ্যে বাকি দুটির উপস্থিতি ঘটলে সেই শ্রেণিভুক্তরা চূড়ান্ত প্রান্তিক (extreme marginal) বলে বিবেচিত হতে পারে।
আরও পড়ুন: অস্তিত্বের জাদুঘরেই অনন্ত কবিতার প্রবাহ
প্রান্তিকতার তত্ত্ব একালের উদ্ভাবন হলেও সমাজে এর আবির্ভাব সেই সুপ্রাচীনকালে। কোনো কেন্দ্রের নিরিখে কিছু একটা প্রান্ত বলে বিবেচিত হয়। যখন মানদণ্ড বদলে যায়, তখন কেন্দ্রেরও বদল ঘটে। যাকে একসময় প্রান্তিক বলে মনে করা হচ্ছিল, সে তখন কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ তত্ত্বটি আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে অন্বিত। আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোণে ‘কেন্দ্র’ সম্পর্কে নির্মিত ধারণাটি হল এই— কেন্দ্র হল সবচেয়ে আলোকিত, উজ্জ্বল, সুবিধাপ্রাপ্ত একটি অবস্থান যা সবার মনোযোগ টানতে সমর্থ। যাবতীয় ক্ষমতার অবস্থান এই কেন্দ্রই। তবে কেন্দ্র তার শক্তিকে প্রকাশ করে রাইজোম্যাটিক পদ্ধতিতে। উদ্ভিদবিদ্যার পরিভাষায় রাইজোম এমন এক ধরনের উদ্ভিদ যার একটিমাত্র শিকড় থাকে না, থাকে অসংখ্য শিকড় এবং সেই শিকড়ের সাহায্যে মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে রস শোষিত হয়। কেন্দ্রও তেমনি তার নানান ক্ষমতার জাল বিস্তার করে শোষণকে বহুমুখী করে তোলে। প্রান্তরা থাকে কেন্দ্রের পরিধির মধ্যে। তাত্ত্বিকরা বলেন, আর্থ-সামাজিক প্রান্তিকতার সূচনা দাস সমাজব্যবস্থা থেকে। ক্রীতদাসের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনচর্যাকে চিরকালই অপহরণ করা হয়েছে। তার পরিবর্তে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষমতাবানের সংস্কৃতির জোয়াল। প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম প্রথার মধ্যে এদেশের প্রথম প্রান্তিকতার ধারণা লুকিয়ে ছিল। যদিও পৃথিবীর সবদেশে একই ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি, তবু মোটের ওপর সব জায়গাতেই প্রান্তিকের অবস্থান প্রায় অভিন্ন। ভারতীয় প্রেক্ষিতে প্রান্তিক মানুষের অভিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এইসব বাহ্যিক লক্ষণ :
(ক) প্রান্তিক বর্গের মানুষ সচরাচর নিম্নবর্ণ, ব্রাত্য, অন্ত্যজ, বৃত্তিহীন।
(খ) ক্ষমতা থেকে দূরে তার অবস্থান। প্রভাব বিস্তারে অক্ষম। তাই ক্ষমতা তাকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারে। এরা নানাভাবে শোষিত ও বঞ্চিত।
(গ) প্রান্তিক মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসহায়, বিপন্ন, নিরন্ন, দরিদ্র, সুবিধাহীন, অনালোকিত।
(ঘ) প্রান্তিকরা সাধারণত আত্মসচেতন নয়। মার্জিত, পরিশীলিত জীবনযাপন করতে পারে না। তাদের কণ্ঠস্বর অনুচ্চ।
এবার বিজন ভট্টাচার্যের নাটক প্রসঙ্গে আসা যাক। ১৯৪৩ থেকে ‘৭৭ পর্যন্ত বিজন পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক মিলিয়ে মোট ২৫টি নাটক লিখেছিলেন। তবে সেগুলির মধ্যে শক্তিশালী রচনা হিসেবে বিবেচিত হয় ‘আগুন’, ‘জবানবন্দী’, ‘নবান্ন’, ‘জীয়নকন্যা’, ‘মরাচাঁদ’, ‘গোত্রান্তর’ ও ‘দেবীগর্জন’। তাঁর দু’তিনটি এমন নাটক রয়েছে, যেগুলিকে মনে করা যেতে পারে পরবর্তীকালের সমৃদ্ধতর নাটকের খসড়া। যেমন ‘নবান্ন’-র প্রেক্ষিতে ‘জবানবন্দী’, ‘দেবীগর্জন’-এর প্রেক্ষিতে ‘কলঙ্ক’, কিংবা ১৯৬১-তে ‘মরাচাঁদ’-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার আগে ১৯৫২-র অপরিণত ‘মরাচাঁদ’। এগুলো প্রমাণ করে নাট্যকার নির্দিষ্ট কিছু ‘থিম’ ধরে তাঁর নাট্যসৃজনের পথে এগিয়েছিলেন। এজন্য কোথাও কোথাও তিনি মৃদু সমালোচিতও হয়েছেন। নাট্যগুণের তুলনায় নাকি তাঁর নাটকে প্রোপাগাণ্ডা বেশি। আসলে বিজন আত্মিকভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ছিলেন মার্কসবাদের সঙ্গে। তাঁর নাট্যকার হয়ে ওঠবার পেছনে এই রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে গোটা পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শিবির সক্রিয় হয়ে ওঠে। সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের পাশাপাশি কমিউনিস্টরাও এই অন্ধ আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে সংহত হতে থাকে। ভারতে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম পর্ব চলছে। আগস্ট আন্দোলনে দেশ উত্তাল। ১৯৪৩-এ ঘটল দক্ষিণবঙ্গের উপকূল অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী বন্যা। বাড়িঘর তো গেলই, গেল চাষবাস। ওদিকে বিশ্বযুদ্ধের আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা পৃথিবীতে। জার্মানির সঙ্গে জোট বেঁধেছে জাপানও। ১৯৪১-এ দেখা গেল রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানি আক্রমণ করছে সোভিয়েতকে। তার প্রতিক্রিয়ায় শুরু হল জনযুদ্ধ। ভারতের কমিউনিস্টরা এই যুদ্ধে শামিল হল। জাপানি বোমার আক্রমণে কলকাতায় তখন রাতের ব্ল্যাক আউট। শত্রুপক্ষকে ঠেকাতে ব্রিটিশ সরকার নিল ‘পোড়ামাটি নীতি’। মাঠের ফসল পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া হল। দেশে দেখা দিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। তার থেকে মন্বন্তর। গ্রাম থেকে শহরের দিকে ছুটে গেল মানুষ দুটি অন্নের আশায়। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হল তাদের। শহরগুলির দিকে ধেয়ে আসা কঙ্কালসার মানুষের মিছিল ক্রমে মৃতদেহের স্তূপে পরিণত হল। চূড়ান্ত হল প্রান্তিক মানুষদের পরিণাম। ১৩৫০-এর মন্বন্তরের ক্ষুধার্ত বাংলাকে পটভূমিতে রেখে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের লেখনী চালনা। তাঁর প্রাথমিক উত্থানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিশেষ কালের ইতিহাস, অর্থনীতি আর প্রান্তিক বর্গের সংস্কৃতি। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, নাটককার হিসেবে বিজনের আবির্ভাব ছিল একেবারেই আচমকা। অন্যান্য অনেকের মতো, তাঁর বাল্য কিংবা কৈশোর কোনো নাট্য-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বেড়ে-গড়ে ওঠেনি। সেই অর্থে তিনি আক্ষরিক তাৎপর্যেই শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর কোনো থিয়েটারি অভিজ্ঞতা না থাকলেও মাটি-মাখা জীবনের ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ছিল। জন্ম ১৯১৫ সালের ১৭ জুলাই, পূর্ববাংলার ফরিদপুরে। পিতা ক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য ছিলেন বৃত্তিতে শিক্ষক। গ্রামেই থাকতেন। সেই সুবাদে বিজনের প্রথম পনেরো বছর কাটে গ্রামেই। গ্রামজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। সেখানকার নিসর্গ প্রকৃতি, গ্রামীণ মানুষের সংকট, দারিদ্র্য, বৃত্তি, ভাষা, রীতিনীতি, জীবনযাপন প্রণালী, তাদের বিশ্বাস-সংস্কারকে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পান তিনি। বোধ হয় এই প্রাপ্তি তাঁর সারা জীবনের অমূল্য সঞ্চয় হয়ে ওঠে, যেটা একদিক থেকে নাট্যকার হিসেবে তাঁর অক্ষয় মূলধন বলে বিবেচিত হতে পারে। আমার ধারণা, এই অভিজ্ঞতার পুঁজিই তাঁর নাট্য-ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ। তাঁর বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন পটভূমি ব্যবহৃত হলেও আদতে তিনি অভিন্ন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে বাল্যের অর্জিত রিক্থকেই মূলধন হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই জীবন্ত অভিজ্ঞতার বলয়টি কতখানি ব্যাপ্ত ও বলিষ্ঠ ছিল তার কিছুটা হদিশ মিলবে ২০০৫ সালে মনফকিরা থেকে প্রকাশিত শিবাদিত্য দাশগুপ্তের সংকলন ও বিন্যাসে গাঁথা “বিশিষ্ট বিজন” গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ‘জনসাধারণের আমি’ শীর্ষক একটি দীর্ঘ কথোপকথনে। এটা যেন তাঁর আত্মজীবনী— যা মুখে মুখে বলা। এখানে তিনি অকপট। তাঁর জন্ম, স্কুল, কলেজ, বাল্যকাল, রাজনৈতিক আন্দোলনের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, গ্রামের নানা বৃত্তিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা, আউল-বাউল-ফকির, জেলে-মালো, কুমোর, ভূঁইচাষি, বেদে প্রভৃতি প্রান্তিকদের জীবনের খুঁটিনাটিকে খুব কাছ থেকে দেখা— এমন আকাঁড়া সব অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করে। বিজনের নিজের কথায় : ‘কলকাতায় আসার আগে আমি গ্রামে-গ্রামে থেকেছি। খুলনা, যশোর, বসিরহাট, সাতক্ষীরায়। সেইজন্য পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত dialect ও language-গুলো আমার খুব জানা ছিল। আমার ভীষণ ভালো লাগত ওদের সঙ্গে থাকতে এবং মিশতে এবং জানতে। Most of my days I spent with them in the villages, with the people. কাজেই ওদের reaction কী হয়, ওরা কেমন করে কথা বলে, অসুখে কী করে কষ্ট পায়, কীভাবে কষ্ট পায়, what are the sources of their trouble, সেগুলো জানা ছিল। … পূর্ব বাংলার যে-শিক্ষা ছিল সেটা পশ্চিম বাংলায় বসে খুব সহায়ক হয়েছিল, কারণ একই মানুষ, মানুষের তো আর কোনো frontier নেই। … ছোটবেলার যে-সমস্ত অভিজ্ঞতা আমি দেখেছিলাম, আমার মতো করে দেখেছে আর একজনকেও আমি পাইনি।’ এটা শুধু বিজনের অহংকার নয়, এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্যের জোর, প্রতিভার অনন্যতা। অন্যরা যেখানে বাল্য ও কৈশোরের নাট্যিক অভিজ্ঞতা নিয়ে, মঞ্চ ও নাট্য নির্মাণের চেনা আদল নিয়ে জীবনকে সেই সুপরিচিত খাঁচায় বন্দি করবার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, বিজনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল তার উলটো। তিনি এগিয়েছিলেন জীবন থেকে নাটকের দিকে। তাই সব কিছু তাঁর নাটকের মাপে শৈল্পিক হয়ে ওঠেনি। কেননা গোটা একটা মানুষকে তার অবয়ব, ব্যক্তিত্ব, অধৃষ্য উদ্ভাসনসহ ধরতে পারে এমন ফ্রেম কই, শক্তিমান শিল্পী কোথায়! নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ এই যে, তিনি যতো বড়ো প্রতিভা সঙ্গে করে এনেছিলেন, তার উপযুক্ত শিল্পী হয়ে উঠতে পারেননি। একালের অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের গলায় বেজেছে এমন অনুযোগের সুর : ‘(বিজন ভট্টাচার্য) দেবতার মতো প্রতিভাবান আর হয়তো শিশুর মতো অগোছালো ছিলেন। … যাঁর প্রতিভা আর শক্তির সম্যক আদল তিনি নিজে পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে।’ আমার মতে, এই অনুযোগের সারবত্তা থাকলেও তলিয়ে দেখা হয়নি তার কারণটি। দেখলে দেখা যেত, বিজন তাঁর গোটা জীবনের অভিজ্ঞতায় পাওয়া মানুষকে সামগ্রিক বিন্যাসে তুলে ধরতে গিয়ে শিল্পের শর্তকে লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শম্ভু মিত্রের মতো তিনি অতটা শিল্প-সচেতন ছিলেন না, জীবনকে আর্টিস্টিক করে দেখাবার মনোহারী ঢঙ তিনি কোনোদিনই প্রযত্নে আয়ত্ত করতে চাননি, বরং বাস্তব জীবনের সমান্তরাল করে নাটককে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে উপজীব্য হয়ে ওঠা মানুষগুলো নিজেদের অবয়ব নিজেরাই সরাসরি দেখতে পায়। এ প্রসঙ্গে ‘জবানবন্দী’ নাটকের ভূমিকার কথা মনে পড়বে । এ নাটক লেখার পূর্বপ্রেক্ষাপট হিসেবে তিনি প্রখ্যাত নাট্য-সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, ‘ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারের পাশ দিয়ে রোজ আপিস যাই। রোজই দেখি, গ্রামের বুভুক্ষু মানুষের সংসারযাত্রা। নারী পুরুষ শিশুর সংসার। এক একদিন রাস্তার ওপরেই শায়িত মৃতদেহ, নোংরা কাপড়ে ঢাকা। … আপিস থেকে ফিরবার পথে রোজই ভাবি, এই সবকিছু নিয়ে লিখতে হবে। কিন্তু কীভাবে লিখব? ভয় করে, গল্প লিখতে গেলে সে বড়ো সেন্টিমেন্টাল প্যানপেনে হয়ে যাবে। একদিন ফেরবার পথে কানে এল, পার্কের রেলিঙের ধারে বসে এক পুরুষ আর এক নারী তাদের ছেড়ে আসা গ্রামের গল্প করছে, নবান্নের গল্প, পুজোপার্বণের গল্প, ভাববার চেষ্টা করছে, তাদের অবর্তমানে গ্রামে তখন কী হচ্ছে। আমি আমার ফর্ম পেয়ে গেলাম। নাটকে ওরা নিজেরাই নিজেদের কথা বলবে।’ এই হল জীবন থেকে নাটকের দিকে চলবার সবচেয়ে জলজ্যান্ত উদাহরণ। বিজন তাঁর গোটা নাট্যকার-জীবনে এই পথের বদল করেননি। এতে তাঁর নাটকে ‘গণ’-ই হল মুখ্য, ‘নাট্য’ অপ্রধান। এবং এই কারণে শম্ভু মিত্র প্রায় অভিযোগের ঢঙেই বলেছিলেন, ‘গণনাট্য যতটা গণের, ততটা বোধহয় নাট্যের নয়।’ এ কি বিজনের দিকেও তাক করে বলা? যেহেতু বিজন তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনে কখনো গণনাট্যের আদর্শ থেকে একতিলও নড়েননি?
গণনাট্য আন্দোলন ছিল বাংলা নাট্য ও মঞ্চের জগতে সেই উল্লেখযোগ্য আন্দোলন যার সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের যোগ। এই আন্দোলন দানা বাঁধবার পেছনে নিঃসন্দেহে কমিউনিস্ট পার্টির একটা ভূমিকা ছিল। বিশ্বকে ছেড়ে যদি কেবল আমাদের দেশের কথাই ভাবি, তাহলে দেখা যাবে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব সফল হবার পাঁচ বছরের মধ্যে ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একটা দশক গড়াবার আগেই বামপন্থী আন্দোলন ধীরে ধীরে তার ভিতকে মজবুত করেছে। ১৯৩৫-এর জুলাইয়ে লণ্ডনে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা মিলে যে ‘Indian Progressive Writer’s Association’ গড়ে তুললেন ভারতেও তার শাখা প্রতিষ্ঠিত হল পরের বছর ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ’ নামে। এই ১৯৩৬-এই জন্ম নিল ‘সারা ভারত কৃষক সভা’। গণকণ্ঠস্বরের মঞ্চ হিসেবে দেখা দিল এই প্রান্তিক চাষিদের সংগঠন। ব্রিটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে জমিদারদের আশ্রয়দাতা হিসেবে ভূমিকা পালন করে এসেছে। মহারানি ভিক্টোরিয়ার কালেও তার অন্যথা হয়নি। ভুঁইচাষিরা সীমাহীন শোষণে জেরবার। ক্ষেতমজুরদের অন্য কিছু করার উপায়ও ছিল না। সুতরাং তারা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট সমস্ত দুর্গতিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলা নাটকের ধারা পর্যবেক্ষণ করলে উনিশ শতকের এক দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’ ছাড়া অন্য কোনো নাটকে কৃষকের সমস্যার কথা আর সেভাবে আসেনি। কল-কারখানার শ্রমিকরা তখন সাহিত্যের পাতায় অদৃশ্য। বাদবাকি যাদেরকে প্রান্তিক বলে গণ্য করা যায়, সেই নিম্নবিত্ত স্তরের অতি সাধারণ মানুষেরা তখন ‘জনতা’ নামের আড়ালে ব্যক্তি-পরিচয় হারিয়ে নাটকের চালচিত্র হিসেবে ব্যবহৃত। রবীন্দ্রনাথের নাটক কোনো ‘ইজম্’-এর ধার ধারেনি, তিনি থিম্ তথা ভাবমুখ্য করেই তাঁর নাটকগুলিকে গড়েছিলেন, যেখানে জনতারা এসেছে ঘটনাপ্রবাহের পটভূমি স্পষ্ট করতে। তিনিও ব্যক্তির তুলনায় গোষ্ঠী হিসেবেই দেখেছেন তাদের। এই রীতির খুব বেশি ব্যত্যয় হয়নি গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, মায় শচীন সেনগুপ্ত কিংবা বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটকে। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলন এই জনতা চরিত্রের উপস্থাপনেই নিয়ে এল চোখ-ধাঁধানো পরিবর্তন। যারা এতদিন চালচিত্র হয়েই ছিল, তারা এখন দেখা দিল মূলচিত্র হিসেবে। এদের সুখ, এদের দুঃখ, এদের জীবনযাপনের টুকিটাকি, এদের সমস্যা ও সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথসন্ধান যেন হয়ে দাঁড়াল নাট্যের প্রধান উপজীব্য।
প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো যে, ভারতীয় গণনাট্য-সংঘের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন হয় ১৯৪৩ সালের ২৫ মে বোম্বাই শহরে। উপলক্ষ্য ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন (২৩মে – ১জুন)। কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে বাংলা থেকে পঁচিশ জনের প্রতিনিধি দল বোম্বাইয়ে হাজির হয়েছিলেন। আর সেই উপলক্ষ্যেই নাট্যভারতী হলে (পরবর্তী সময়ে গ্রেস সিনেমা) একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছটি নাটক অভিনীত হয়েছিল, যাদের মধ্যে অন্যতম ছিল বিজন ভট্টাচার্যের ‘আগুন’, অন্যটি বিনয় ঘোষের ‘ল্যাবরেটরি’। সুতরাং আন্দোলনের দায়বদ্ধতা পালনের অঙ্গীকার বিজন তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে সার্থক করে তুলতে অগ্রসর হলেন। তাঁর হাত দিয়ে একে একে বেরোল জবানবন্দী, নবান্ন, জীয়নকন্যা, মরাচাঁদ, কলঙ্ক, জননেতা, অবরোধ, গোত্রান্তর, ছায়াপথ, মাস্টারমশাই, জতুগৃহ, দেবীগর্জন, কৃষ্ণপক্ষ, ধর্মগোলা, গর্ভবতী জননী, আজ বসন্ত, লাস ঘুইর্যা যাউক, চলো সাগরে, হাঁসখালির হাঁস। এই প্রতিটি নাটকই ছিল একজন ‘কমিটেড’ শিল্পীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্মারক। এইজন্যই বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ততটা শিল্পিত হতে পারেনি, যতটা দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারে একনিষ্ঠ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে প্রান্তিক মানুষের অবস্থান অগ্রবর্তী আলোচনার অন্বিষ্ট।
অনেকেই জানেন, বিজন নাটকের জগতে পা রাখার আগে কথাসাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করেন। সে সময়ের বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি ছোটোগল্প প্রকাশিত হয়। তরুণ বিজনের বয়স যখন ১৫–১৬, সেই সময় ফরিদপুর ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায়। তখন অন্যতম আশ্রয় হয়ে ওঠেন তাঁর মামা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। কলকাতাতে থাকতে থাকতে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মধারার প্রতি আকৃষ্ট হন, পরিচিত হন তৎকালীন প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে, যাদের মধ্যে ছিলেন মুজফ্ফর আহমেদ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, বিনয় ঘোষ, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ। এঁদের সংস্পর্ষে এসে সর্বহারা শ্রেণি সম্পর্কে তাঁর কিছু তাত্ত্বিক জ্ঞান হচ্ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তের মনোবৃত্তিকে তিনি পুরোপুরি বর্জন করতে পারছিলেন না। মনের চারপাশের সেই দেওয়াল ভেঙে দিল ১৯৪২-এর অস্থিরতাময় পরিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এদেশবাসীকে এনে দাঁড় করিয়ে দিল চূড়ান্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের জায়গায়। মন্বন্তর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ভদ্রবেশী মানুষের নীতিহীনতা, মনুষ্যত্বহীনতা, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারিদের নির্মোকহীন অর্থগৃধ্নুতা। মন্বন্তরের কালে কলকাতার পথে ঘাটে মৃত্যুর মিছিলে তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। এদের অমানুষিক জীবনযাপন দেখে তিনি যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে যারা কৃত্রিমভাবে খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ ডেকে এনেছে। এই মন্বন্তরজাত মানবিক দুর্দশার ব্যাপকতাই তাঁকে গল্পের ছোট্ট পরিসর থেকে টেনে আনল নাটকের আঙিনায়। তিনি মার্কসিজমের যে-তত্ত্বকে এতদিন মগজ দিয়ে বুঝছিলেন, এবার হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করার দরজা খুলে গেল। এইভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা নাটকের গণমুখী পালাবদলের প্রধান হোতা হিসেবে দেখা দিলেন বিজন ভট্টাচার্য। তাঁর এই নাট্য অনুভবে বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল একটি স্বপ্ন : বিপন্ন দুর্গত মানুষের সার্বিক ত্রাণ, সমস্ত ধরনের শোষণ থেকে পরিপূর্ণ মুক্তি। আমরা যদি বিজনের নাটকগুলি খুব খুঁটিয়ে লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব তাঁর এই লক্ষ্যের সন্ধানে যাত্রা কীভাবে নাটক থেকে নাটকে উত্তরিত হয়েছে। ইতিহাসের সময়-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি পালটেছেন কাহিনির পটভূমি, শোষণের রূপ, শোষিতের প্রতিক্রিয়া। তাঁর নাটকের প্রান্তিক মানুষকে চিনে নেবার এও এক অনবদ্য কৌশল।
বিজন ভট্টাচার্যের অধিকাংশ নাটকের পটভূমি গ্রাম বাংলা। এই পল্লীগ্রামের মানুষদেরকে তিনি তাঁর হাতের তালুর মতো খুঁটিয়ে চিনতেন। তাঁর প্রথম চার-পাঁচটি নাটকের ক্যানভাস গড়ে উঠেছে গ্রামের পটভূমিকায়। কাদের সেখানে দেখা পাই? মাঠে-খাটা কৃষক, জমিদারের অধীনস্থ ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষি, তাদের পরিবারের লোকজন— দেহশ্রমই যাদের সম্বল। এরা চিরকাল পরের কাছে গোলামি করে এসেছে। কন্ঠস্বর অনুচ্চ, শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়া, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় ভরপুর। বিজন মনে করতেন, যতই নগর সভ্যতা প্রসারিত হোক, তার ঝলমলে রূপ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, দেশ বেঁচে আছে গ্রামের ওপর, কেননা গ্রামেই রয়েছে সমস্ত উৎপাদক শ্রেণি। কৃষক তাদের মধ্যে অন্যতম। তাই কৃষককুলই তাঁর অধিকাংশ নাটকের মুখ্য পাত্রপাত্রী। এরা চিরকালই অবজ্ঞাত অপাংক্তেয় হয়ে এসেছে; নানাবিধ শোষণে ও শাসনে জেরবার করে তোলা হয়েছে এদের জীবন, তবু এদের হাসিমুখ কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। নাট্যকারের বিচিত্র জীবন অন্বেষণের তাগিদ তাঁর নাটকে নানা ধরনের চরিত্র সমাবেশ করতে প্রণোদিত করেছে। কৃষক ছাড়া এসেছে ছোটোখাটো দোকানদার, স্বল্প বেতনের স্কুলশিক্ষক, পাগল, ভিখারী, খোঁড়া, মদ্যপ, অন্ধ গায়ক, বেদে-সাপুড়ের দল, নিচুবৃত্তির মানুষজন। কখনো কখনো শহর হয়েছে তাঁর নাটকের পটভূমি। সেখানে অভিজাত ধনী এলাকার মানুষজন নয়, ফুটপাত কিংবা খোলার চালের ঘিঞ্জি বস্তিতে থাকা অভাব ও নানান সমস্যায় ক্লিষ্ট মানুষরাই হয়েছে তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রী। আসলে গ্রাম ও শহরের এইসব অন্নবস্ত্রহীন, বিপন্ন, মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া মানুষগুলোই ছিল বিজনের চোখে দেখা বাস্তবের ভারতবর্ষ। এদের উত্তরণের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। এদের সঙ্গেই ছিল তাঁর আত্মিক যোগ। যে মার্কসবাদের আদর্শকে লালন করতেন তিনি মনে মনে, তার যথার্থ প্রয়োগে জনগণের ভেতর নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই আছে একটি বলশালী ভারতবর্ষ— এমনটাই মনে করতেন তিনি। তাঁর চিত্রিত প্রান্তিক মানুষরা অত্যন্ত সাধারণ, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। কিন্তু তাদের মধ্যে আবেগ আছে, উদ্দীপনা আছে, আছে কোমল অনুভূতি। গ্রাম ছেড়ে আসা মানুষগুলোর মধ্যে হতাশা, অসহায়তা, গ্লানি আছে একথা অস্বীকার করা যায় না, এমনকি কেউ কেউ অস্তিত্বরক্ষার তাগিদে কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যময়, জীবনযাপনের আশায় পদস্খলনের পথে এগিয়েছে, তবু তাদের প্রাণশক্তির সতেজতা, মূল্যবোধের প্রতি নিষ্ঠা, প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই আমাদেরকে বিস্মিত না করে পারে না। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের প্রান্তিকরা আদৌ চালচিত্র নয়, তারাই কাহিনিভাগের মূল প্রতিমা। নাটক ধরে ধরে সেই প্রতিমার স্বরূপ প্রকাশ করাই এখন আমাদের লক্ষ্য।
‘আগুন’ বিজনের প্রথম নাটক। গণনাট্য সংঘ কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়েছিল ১৯৪৩-এর মে মাসে। মোট পাঁচটি দৃশ্য। এটি একটি একাঙ্ক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের অব্যবহিত পূর্বকালের প্রেক্ষাপটটি এ নাটকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। দেশে খাদ্যাভাব। ব্রিটিশ সরকারের তরফে সেই অভাব মোকাবিলার জন্য সামান্য একটু রেশনের ব্যবস্থা। প্রয়োজনের তুলনায় ভীষণই অপ্রতুল। তাই ভোর থেকেই অভাবগ্রস্ত হাভাতে মানুষগুলোর লম্বা লাইন রেশন দোকানের সামনে। তাদের সামলানোর জন্য রয়েছে সিভিক গার্ড। কাতারে কাতারে লোক আসছে সরকারি ডোল পেতে। তাই রাত ফর্সা হবার আগেই বস্তিতে বস্তিতে শোরগোল পড়ে যায়। কে আগে গিয়ে দাঁড়াতে পারে লাইনে। সেখানেও আগে-পিছে দাঁড়ানো নিয়ে মারপিট। সতীশ, জুড়োন, হরেকৃষ্ণ, নেত্য, নেত্যর মা, শ্রমিক, দোকানি, কেরানি একাধিক নামহীন পুরুষ— এদের সবাইকে উপস্থিত করে নাট্যকার প্রান্তিক মানুষদের একটা বৃত্ত রচনা করেছেন। স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্যের সরকারি বন্টনের মধ্যে নানা চক্র কাজ করে। গোপনে বিক্রি হয়ে যায় সরকারি সাহায্য। এই লাইনে দালাল ফড়েরাও আছে। সুতরাং রেশনিং নিয়ে নৈরাজ্যও চলছে। সিভিক গার্ড কর্তব্য দেখাতে গিয়ে নিষ্ঠুরতাও করছে। হকদার প্রাপককে লাইন থেকে বের করেও দিচ্ছে। এ নিয়ে বচসা, ঝঞ্ঝাট, গণ্ডগোল। লাইনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মধ্যে ব্যস্ততা। তারা সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। একে অন্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত। লাইনে দাঁড়িয়েই তাদের মধ্যে অন্তর্কলহ চলতেই থাকে। এরই মধ্যে সিভিক গার্ড একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে লাইন থেকে বের করে দিলে পরিস্থিতি চরমে ওঠে। সিভিক গার্ডকে একজন ঘুষি মারতে উদ্যত হয়। লাইন ভেঙে তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়— ‘মার শালা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে ফেল’। আর ঠিক সেই চরম উত্তেজনার মুহূর্তে এক যুবক চিৎকার করে ওঠে— ‘আগুন! আগুন!’ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে সবাই— ‘কোথায় আগুন?’ ‘কিসের আগুন?’ যুবকটি হাতজোড় করে জানায়— ‘আগুন! আগুন জ্বলছে আমাদের পেটে।’ বাইরের অগ্নিকাণ্ড যেমন বিধ্বংসী, তেমনি মানুষের জঠরানল ভয়ংকর রূপে প্রাণনাশী। অবশেষে চাল পায় অনেকে, আবার কেউ কেউ পায় না। নাটকটি শেষ হয় সমবেত জনতার এই বোধে : ‘সমস্যা সব্বার। যথেষ্ট তো হয়েছে। এখন বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে মিলেমিশে থাকতে হবে, ব্যাস্।’ এটাই প্রান্তিকদের উত্তরণ।
আরও পড়ুন: বাংলার নবজাগরণ ও মাইকেল মধুসূদন (শেষ পর্ব)
পরের নাটক ‘জবানবন্দী’। অভিনীত হয় ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে গণনাট্য সংঘের দ্বারা। নাট্যকার মোট চারটি দৃশ্যে মন্বন্তর-ক্লিষ্ট বাংলাকে উপস্থাপিত করেছেন। দুর্ভিক্ষ আর দূরে দাঁড়িয়ে নেই, একেবারে মানুষের ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আগের নাটকে ছিল ছিন্ন ছিন্ন মানুষের দল, পরস্পর নিঃসম্পর্কিত। এ নাটকে বিজন গ্রামের একটি পরিবারকে তাঁর কাহিনির ভিত্তি করেছেন। পরিবারের কর্তা পরাণ মণ্ডল। তিনি বৃদ্ধ চাষি। তাঁর দুই পুত্র বেন্দা আর পদা। পরাণের স্ত্রী তথা বেন্দার মাও রয়েছেন প্রেক্ষাপটে। আর আছে বেন্দার বৌ আর ছেলে মানিক। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিকে ব্যাপক করে তোলবার তাগিদে এসেছে পরাণের প্রতিবেশী রাইচরণ, রাইচরণের স্ত্রী হাসি আর রমজান। প্রথম দৃশ্য শুরু হয় এক অজপাড়াগাঁয়ে, যেখানে পরাণ মণ্ডলদের চোদ্দ পুরুষের বসবাস। বাড়ি বলতে বাঁশের খুঁটি লাগানো চালাঘর। খুবই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। দুজন স্ত্রীলোক অর্থাৎ বেন্দার মা ও বৌ নোংরা কাপড়ে আপাদমস্তক ঢেকে মড়ার মতো শুয়ে আছে। বেন্দার বৌয়ের কোল ঘেঁসে তার ছেলে মানিক। বৃদ্ধ পরাণ অসুস্থ। কাশির ব্যামো। তিনি দুর্গতিতে কেবল ঈশ্বরকে স্মরণ করেন। তাতেই রাগ বড়ো ছেলে বেন্দার। বেন্দা সার বুঝেছে এ আকালের দিনে ভগবানকে ডেকে দুর্গতি পার হওয়া যাবে না। মানিক শীর্ণ, রোগজর্জর। প্রবল খিদে তাকে কাঁদায়। পদা বলে, ‘মানুষির বাচ্চা তো। সময় মতো না পায় দুটো খাতি, না পায় এট্টা কিছু। এ তো আর জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা না। সইতি পারে কখনও এত ধকল ওই অটটুখানি ছেলে?’ পরাণ গোটা পরিবার নিয়ে পথে নামে, রওনা দেয় শহরের উদ্দেশে। তাদের সঙ্গে থাকে দু’একটা ছেঁড়া মাদুর, খানকয়েক সানকি, কয়েকটা মাটির পাত্র, একটা কাটারি, ছেঁড়া কাঁথা, দু’একটা তেলচিটে খড়ের বালিশ, দুটো কাস্তে। পরানের ‘সুখির সংসার’ ফেলে যেতে কষ্ট হয়, তবু পা ওঠাতে বাধ্য হন তিনি।
দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শুরু হয় পরাণদের শহরে ফুটপাতের জীবন। পার্কের রেলিং ঘেঁসে একটা আস্তানা বানিয়ে নিয়েছে বেন্দারা। রেলিং থেকে আচ্ছাদনের মতো ঝুলছে ছেঁড়া মাদুর আর চট। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রেলিং-এর ধারে সাজানো। শহরের প্রান্তিক মানুষের জীবনযাপন খুব স্পষ্টমাত্রায় ধরা পড়ে এই দৃশ্যপট রচনায়। এদের আশপাশ ঘেঁসে আরো অনেক ছিন্নমূল পরিবার। পরাণ সহজ হতে পারেন না শহরের অপরিচিত পরিবেশে। জন্মচাষির ভিক্ষে চাওয়ার অভ্যাস নেই। তাই বাধো-বাধো ঠেকে। অবশেষে এক ভদ্রলোককে দেখে বলেই ফেলেন নিজেদের দুর্গতির কথা, শহরের মানুষের প্রতি নির্ভরতার কথা : ‘তাই চলে আলাম শহরে। ভাবলাম, বলি বাবুরো থাকতি আর না খাতি পেয়ে মরবো না সেখেনে, দুটো ভাতের ব্যবস্থা একরকম করে হয়েই যাবে।’ একথার প্রত্যুত্তরে যেকথা বললেন ভদ্রলোক পরানের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, ‘তা হলে সব বুঝে শুনেই এয়েছো!’ এই শুরু। শহরের বাবুদের আরো হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রকট হয়ে উঠতে থাকবে এরপর থেকে। শহরে এসে যে ‘খুব শিক্ষে হচ্ছে’ সেকথা বুঝতে পারবেন বেন্দার মাও। তিনিও ধীরে ধীরে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে স্বার্থপর হয়ে উঠবেন। লঙ্গরখানা থেকে পাওয়া এক হাঁড়ি খিচুড়ি একাই গোগ্রাসে খেয়ে ফেলবেন। স্বামীর খিদেকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনবেন না। এই খিচুড়ি খেয়েই অসুস্থ মানিক আরো অসুস্থ হয়ে পড়বে, শেষ অব্দি মৃত্যু হবে তার। গোটা পরিবার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বে এরপর।
আরও পড়ুন: গ্রাম সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (শেষ পর্ব)
সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষগুলোর কী পরিণাম ঘটেছিল, দুর্ভিক্ষের কবলগ্রস্ত হয়ে নাট্যকার তার বাস্তব-অনুসারী বিবরণ রেখেছেন এখানে। পুত্রশোক ভুলে যায় বেন্দার বউ। একদিন তাকে দেখা যায় নতুন শাড়ি পরতে। রাতের অন্ধকারে সে ক্রমে স্বেচ্ছায় নিরুদ্দেশ হতে থাকে। শহরের অসভ্য জানোয়ারেরা শিকার ধরতে বেরোয় বেন্দার বউদের মতো মেয়েদের। তেমন এক ভদ্রবেশী যুবককে ধরে ফেলে পদা। রাতের পাহারাদাররা তাকে নিয়ে যায়। বেন্দা এখন সারসত্যটা বোঝে— ‘ওই সেই পরমেশ্বর আর এই এক ভদ্দরনোক, সর্বনাশ করে ছাড়লে একেবারে আমাদের।’ সে স্ত্রীকে কটুভাষায় গাল দেয়, আর পিচ কেটে বলে, ‘চাষির ঘরের কলঙ্ক’। বোঝা যায় এরা দরিদ্র হলেও ইজ্জৎ বিকিয়ে দিতে নারাজ, ন্যূনতম মূল্যবোধ এদের আছে। সবশেষ দৃশ্যে বৃদ্ধ পরাণ ভয়ংকর অসুস্থ হয়ে পড়েন। কঙ্কালসার তাঁর শরীর, কোটরগত চক্ষু। যে আশা নিয়ে এসেছিলেন শহরের মানুষের কাছে, তা নিরাশায় পরিণত হয়েছে। পরাণের মতো জন্মচাষির জীবনের মূল্যায়ন করতে চেয়েছে তার ছেলেরা :
“পদা।। (গম্ভীরভাবে) ষাট বছর ধরে বাপ আমার সোনা ফলিয়ে এয়েছে মাথালের মাটিতি। শহর বাজারে আজ যেসব চালডালির খয়রাতি হচ্ছে, ইরির মধ্যে পরাণ মণ্ডলেরও হয়তো কিছুডা দান আছে। কিন্তু কেউ আজ সে কথাডা স্বীকার কল্লে না। পরাণ মণ্ডল বরবাদ। না খেতি পেয়ে আজ তারে রাস্তায় পড়ি মরতি হচ্ছে।
বেন্দা।। (গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে) চারিদিকি এত সম্পদ, এত ধনদৌলত অতচ এই পিরথিমিতি পরাণ মণ্ডলের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার সাব্যস্ত হল না।”
তাই পরাণ মণ্ডল আলো ঝলমলে কলকাতার ফুটপাতে বুভুক্ষায় অনাহারে মরে গেল। তবে চলে যাবার আগে সেই কৃষক বৃদ্ধের চোখে ভেসে উঠল মাঠভরা পাকা ফসলের স্বপ্নদৃশ্য–- ‘মাঠে মাঠে কত কত ধান, কত ধান হয়েছে। কত– ধান হয়েছে।’ সেই স্বপ্নকে শয্যাশায়ী মৃতপ্রাণ পরাণকে বিছানা থেকে যেন ঠেলে তুলে দেয়। তিনি বেন্দা, পদা, রাইচরণ, রমজান সবাইকে ডেকে সোৎসাহে বলতে থাকেন— ‘তোরা সব ঘরে ফিরে যা বেন্দা। ঘরে ফিরে যা। আমার আমার সেই মরচে পড়া নাঙ্গল কখানা আবার শক্ত করে, শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতি। … সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে। ফিরে যা। ফিরে যা।’ বৃদ্ধ পরাণের এই অন্তিম নির্দেশ শেষ পর্যন্ত পালিত হয়েছিল কিনা, নাটকে তার হদিস নেই; তবে মন্বন্তরের কালে প্রান্তিক মানুষের কী দুর্গতি হয়েছিল তা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারা যায়। এই নাটকেরই যেন পরিবর্ধিত রূপ গড়ে তোলা হয়েছে ‘নবান্ন’-এ। সেখানে গ্রামছাড়া মানুষগুলো আবার ফিরেছিল গ্রামে, নতুন ফসলের মুখ দেখে তাদের দুঃখ দূর হয়েছিল। ‘আগুন’-এ পেয়েছিলাম একসঙ্গে বাঁচবার কথা, ‘জবানবন্দী’-তে মিলল শহরবাসের মরীচিকা ত্যাগ করে কৃষক পরিবারের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের কথা। পরাজয়ের অন্ধকার নয়, আশার আলো দেখিয়েই নাটকের সমাপ্তি। উদ্ভ্রান্ত প্রান্তিকের জীবনকে নাট্যকার বিজন যেন একটা দিশা দেখাতে চেয়েছেন এ নাটকে।
আরও পড়ুন: কোন পথে আমাদের সাহিত্য এবং সাহিত্যিক
মাঝখানে মাত্র আটটা মাস। তারপরেই বিজন ভট্টাচার্য আবির্ভূত হলেন তাঁর কালজয়ী নাটক ‘নবান্ন’ নিয়ে। এর প্রথম অভিনয় হয়েছিল ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪-এ শ্রীরঙ্গমে। গণনাট্য তার উত্তুঙ্গ সীমা স্পর্শ করেছিল এই নাটকে। একে ঘিরে যত উচ্ছ্বাস, প্রশংসা আর চর্চা হয়েছে গণনাট্যের পর্বে আর কোনো নাটক নিয়ে তা হয়নি। কারণ একটাই। ‘নবান্ন’ কেবল প্রান্তিক সমাজের দুর্গতির নাটক ছিল না, ছিল একইসঙ্গে সেই বিপন্নতা থেকে মুক্তির নাটকও। এর আগে বিজন ‘জবানবন্দী’তে যেখানে এসে থেমেছিলেন, এ নাটকে সেই সমাপ্তির রেখাকে টেনে নিয়ে গেলেন আরো কিছুটা ইতিবাচকতার দিকে। প্রান্তিক মানুষেরা নিজেরাই একজোট হয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে— এই সমাধান-সূত্র দেওয়ায় গণনাট্যের কর্মীরা, মার্কসিস্টরা একে সাদরে বরণ করে নিয়েছিল। ‘জবানবন্দী’র মতো এ নাটকেরও পটভূমি পঞ্চাশের মন্বন্তর। অন্নাভাবে হাহাকার-দীর্ণ ক্ষুধার্ত বাংলাকে যেন এক চিলতে মঞ্চের ওপর টেনে এনেছিলেন নাট্যকার। এখানেও আখ্যান কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটি গ্রামীণ চাষি পরিবারকে ঘিরে। দক্ষিণবঙ্গের বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী জেলা মেদিনীপুর। তারই অন্তর্গত অখ্যাত এক আমিনপুর নাটকটির সূচক পটভূমি। পরে নাটকের কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে কলকাতা মহানগরের আনাচে-কানাচে। সবশেষে আবার এসেছে আমিনপুর। আগের দুটি নাটক ছিল একাঙ্ক। সুতরাং পরিসর ছোটো। ‘নবান্ন’ তা নয়। অনেক চরিত্র ও প্রচুর ঘটনার সমাবেশে এ নাটক আয়তনে যথেষ্ট বিস্তৃত, যাকে ধরতে নাট্যকারকে চারটি অঙ্কে পনেরোটি দৃশ্যের আয়োজন করতে হয়েছে। এ নাটকের সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের কিঞ্চিৎ সংযোগ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। নাটকটির ভূমিকায় বিজন লিখেছেন : “১৯৪২ সনের আগস্ট মাসে দেশব্যাপী যখন প্রত্যক্ষ গণঅভ্যুত্থান আরম্ভ হল, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার শেষ প্রাণান্তিক চেষ্টায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে ভারতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ‘নবান্ন’ নাটকের রচনাকাল এই রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্বে।” গান্ধীজির ডাকে গোটা দেশ তখন উত্তাল। মেদিনীপুরের বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে ও শ্লোগানে আলোড়িত-মুখরিত করে তুললেন তাঁর জেলা। ভারতের তেরঙ্গা পতাকা হাতে অকুতোভয়ে এগোলেন বাহিনীর সামনে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর বুলেট তাঁর শরীরকে ঝাঁজরা করে দিল। হাতে ধরা পতাকা তখন উড্ডীয়মান। ‘নবান্ন’-এ সেই গৌরবময় ইতিহাসের যেন নাট্যিক পুনর্নির্মাণ ঘটেছে প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননীর শাসক-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনায় ও প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে সাহসিকতার সঙ্গে প্রাণ বিসর্জনে। প্রধানের দুই পুত্র ভূপতি ও শ্রীপতি আত্মবলি দিয়েছে এই আন্দোলনে শামিল হয়ে। পুত্রদের এই নির্মম মৃত্যু প্রধানকে ভীত করে না, বরং করে তোলে আরো বেশি পরিমাণে উদ্দীপ্ত। তিনি পুত্রহন্তাদের সমুচিত জবাব দিতে চান। কিন্তু অক্ষম বৃদ্ধ অসহায়ভাবে বারবার খালি আক্ষেপ করেন— ‘আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে। আজ যদি আমার শ্রীপতি ভূপতি…।’ আর বারেবারেই ভাইপো কুঞ্জকে ডেকে বলেন, ‘ও কুঞ্জ, কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে! কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব! প্রাণ দেব, প্রাণ দেব!’
চলবে…