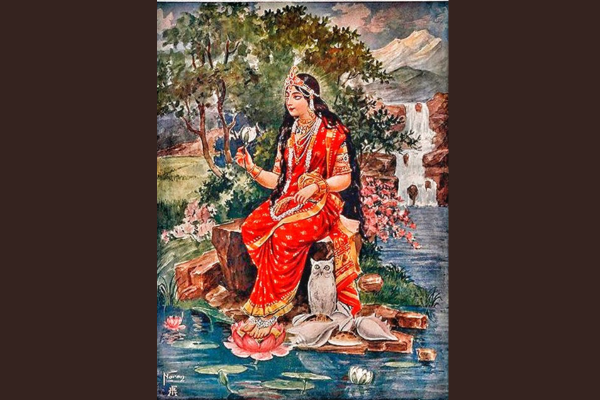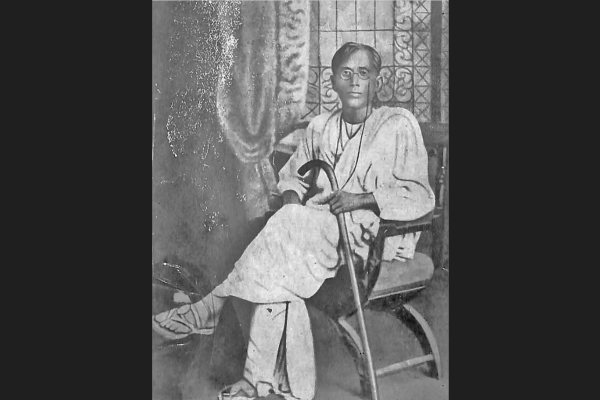প্রাচীন ভারতে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার
এযুগের মত বই সেযুগেও ছিল, তবে প্রাচীন ভারতের বইগুলি এখনকার মত ছিল না; তখন বইকে বলা হত পুঁথি। আর এই পুঁথি তৈরি ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, ইতিহাসে এবিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু মহর্ষি বাৎস্যায়ন রচিত কামসূত্র গ্রন্থের লোকবৃত্ত প্রসঙ্গ থেকে একথা অবশ্যই জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে প্রতি সন্ধ্যায় পুস্তক-বাচনের প্রথা…